আমার যে দিন ভেসে গেছে

জায়গাটার নাম সাহেববাড়ি। বাসিন্দারা পুরোপুরি এদেশীয়, তবে জাতে খ্রিস্টান। পরবর্তীতে অবশ্য কিছু হাড়হাভাতে হিন্দু রিফিউজিও এসে জুটেছে, স্থানীয়রা বলে রিপুচি।
বাস রাস্তার ধারে, আদিগন্ত সবুজ ধানজমির মাঝে প্রভু যিশুর গীর্জা। চারপাশে ছবির মতো সুন্দর খনিকটা অনাবাদী জমি, কেয়ারি করা নানারকম বাহারি ফুলের গাছ আর মখমলের মতো সুন্দর পরিচ্ছন্ন সবুজ ঘাসে-ঢাকা চত্ত্বর।
পথ চলতি রিপুচিরা অবাক চোখে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ‘বড়োই সৈন্দর্য’!
গির্জার সামনে সবুজ ঘাসের গালিচায় পা রেখে শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মা মেরির মূর্তিতে মায়ামাখা ঘরোয়া মা-মাসির আদল, নির্জন দুপুরে সেই মূর্তির চোখে চোখ পড়লে মনে হতো, এই বুঝি তিনি ডেকে কথা কইবেন। ছোটবেলায় আমাদের মনের অবচেতনে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো তাঁকেও আমরা বড়ো মান্য করতাম। পরীক্ষার আগে কিংবা রেজাল্ট বেরবার দিনে তাঁকে নমস্কার না করে স্কুলের পথ মাড়াতাম না।
গৌরচন্দ্রিকাটা বুঝি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আসলে যার কথা বলার জন্যে এই প্রৌঢ় বয়েসেও এতটা ভনিতা করতে হল, তার নাম রেবেকা, রেবেকা ফার্নান্ডেজ। ওর মা বাঙালি হলেও বাবা নাকি খাঁটি সাহেব ছিলেন। তবে কস্মিনকালেও তাঁকে কেউ দেখেনি।
অস্ট্রেলীয় গমের মতো গায়ের রঙ, তিলফুলের মতো তীক্ষ্ণ নাক, কালো গভীর চোখ, একঢাল কোঁকড়ানো কালো চুল, মুখের ডৌলটি যেন অবিকল লক্ষ্মী ঠাকরুণের মতো, সব মিলিয়ে খ্রিস্টান পাড়ার কালোকোলো অসুন্দর দেশি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে ছিল একেবারেই বেমানান।
রেবেকা যখন ক্লাস এইট-নাইনে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত, তখনই তার অসংখ্য অনুরাগী। অনেকে তার আসা-যাওয়ার পথের ধারে নানা আছিলায় দাঁড়িয়ে থাকত। তবে সে সব সময় এমন গাম্ভীর্যের বর্মে নিজেকে আড়াল করে রাখত যে কেউই তার খুব কাছাকাছি যাওয়ার সাহস পেত না।
তবে এলাকায় দুঃসাহসী ছেলেরও তো অভাব ছিল না। তাদের প্রেমপত্র মোড়া ঢিলের আঘাতে ওদের বাড়ির কাচের শার্সিগুলো মাঝে মাঝেই বদলাতে হতো। প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে কেউ চড়-থাপ্পড় খেয়েছে, এমন ঘটনাও প্রায়ই শোনা যেত।
তবে কালা প্রশান্তর কেসটা একেবারে আলাদা। ঘটনাটা আমাদের ছাত্রাবস্থায় প্রায় কিংবদন্তির মতো হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল কিঞ্চিৎ কানে খাটো, কথা বলার সময় ‘ত’-কে ‘ট’ উচ্চারণ করত। তবে ওর বাবা ভক্ত ছাগুলের ছিল দেদার পয়সা, প্রশান্ত তার একমাত্র পুত্র। ক্লাস সেভেন এবং এইট মিলিয়ে বার চারেক গোত্তা খাওয়ার পর সে যখন ক্লাস নাইনে উঠল, তখনই তার মোটা গোঁফ, তাগড়াই শরীর।
রেবেকার স্কুলে যাওয়ার সময় সে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরে হাসপাতাল মোড়ে্ দাঁড়িয়ে থাকত।
একদিন সাহস করে সে বোধ হয় রেবেকাকে ইংরেজি-সংক্রান্ত কিছু বোঝাচ্ছিল। খেয়াল করেনি, আমাদের স্কুলের ইংরেজির মাস্টারমশাই বীরেনবাবুও ঠিক ঐ সময়ে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে স্কুলে আসছেন।
তার কথায় রেবেকার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানা না গেলেও প্রশান্তর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বীরেনবাবু কথাটা শুনে ফেলেছিলেন।
স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকদিন প্রেয়ার শেষ হওয়ার পর পাঁচ মিনিট ঐদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অরাজনৈতিক খবর পড়া হত। সাধারণত ভালো ছাত্ররাই সংবাদ পাঠকের দায়িত্ব পেত।
সেদিন প্রেয়ার শেষ হওয়ার পর বীরেনবাবু ‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আজ প্রশান্ত খবর পড়বে, ইংরেজিতে।
প্রস্তাব শুনে তো সকলে থ। ইংরেজিতে যে বরাবর শূন্যের কাছাকাছি নম্বর পেয়ে এসেছে, কোনও শব্দই ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারে না, সে পড়বে ইংরেজি খবর!
কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি ছিল। স্যার একটু থেমে ফের বললেন, আজ ক্লাস ফাইভ থেকে এইটের সব ইংরেজি ক্লাসগুলো প্রশান্তই নেবে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, সে আজ এক বালিকাকে ইংরেজি শেখাতে চেয়ে প্রস্তাব দিচ্ছিল।
স্যারের ঘোষণা শেষ হতে না হতেই প্রশান্ত সেই যে স্কুলের গেট টপকে পালাল, তারপর ওকে স্কুলের ত্রিসীমানায় কখনও দেখা যায়নি।
তবে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ার বাতিক যে ওর যায়নি, তা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সময় হাসপাতাল মোড়ে গেলেই বোঝা যেত।
আমি বরাবরই মুখচোরা। পড়াশুনোয় হয়তো অন্যদের চাইতে কিছুটা ভালো ছিলাম। তবে সে অনেকটা উলুবনে খাটাশ রাজার মাপে। নিজের ভালোত্ব সম্পর্কে সেই তরুণ বয়েসে আমার একটা মনগড়া অহংকার ছিল। ফলে রেবেকার প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও আমি কখনও রাস্তায় দাঁড়ানো ছেলেছোকরার দলে ভিড়তে পারিনি। তবে তাকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে প্রবল ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যেত।
খ্রিস্টান পাড়ায় বন্ধুবান্ধব নেহাত কম ছিল না। প্রতি বছর বড়দিনে তারা নেমন্তন্ন করে ঘরে তৈরি কেক আর কমলা লেবু খাওয়াত। সঙ্গে পকেট সাইজের বাংলা ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’ কিংবা ‘মথি-লিখিত সুসমচার’ ছিল বড়দিনের বাঁধা উপহার। তবে ওসবে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। স্রেফ রেবেকাকে কাছ থেকে এক নজর দেখা যাবে, হয়তো মুখোমুখি হলে একটু হাসবে, এই আশায় সারাবছর বড়দিনের নেমতন্নের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতাম।
ঘটনাটা কাকতালীয়ই বলতে হবে, স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হওয়ার ঠিক আগে বড়ো অদ্ভুতভাবে এই রেবেকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে গেল।
হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর টিউশানি শুরু করেছিলাম। মাসখানেক যেতে না যেতেই ছাত্র সংখ্যা পিল পিল করে বাড়তে লাগল।
একদিন সকালে বাড়িতে ক্লাস সেভেন-এইটের একপাল অপোগণ্ডকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করছি, এমন সময় স্বয়ং রেবেকা ওর ছোট ভাইকে নিয়ে হাজির। ক্লাস সেভেনের ডেভিডকে অঙ্ক আর ইংরেজি পড়াতে হবে। খ্যাতি যে সর্বদা বিড়ম্বনার কারণ না হয়ে মাঝে মাঝে সৌভাগ্যের দ্যোতকও হতে পারে, এই প্রথম টের পেলাম।
ধানক্ষেতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মা মেরির প্রতি আমার ভক্তি আরও বেড়ে গেল। রেবেকাকে সেদিন কী বলেছিলাম, কিংবা আদৌ কিছু বলেছিলাম কিনা, আজ আর মনে পড়ে না। শুধু চোখ বন্ধ করলে সেদিনের উত্তেজনাটুকু আজও টের পাই।
তখন মনে হত, ডেভিড নয়, যেন রেবেকাই আমার কাছে রোজ পড়তে আসে। নিজেকে প্রাণপণে শাসনের চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নিজের অজানতে রেবেকার প্রসঙ্গ তুলে লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম।
ক্রমে আমার খাওয়া-ঘুম চলে যাওয়ার উপক্রম হল। বন্ধুরা রেবেকার সম্পর্কে রসিকতা করলে আগের মতো তাতে যোগ দিতে পারি না। ওর নতুন কোনও অনুরাগীর খবর কানে এলে কেমন যেন দিশেহারা লাগে। অথচ সাহস করে যে রেবেকার সঙ্গে একবার কথা বলব, তাও পেরে উঠি না।
এর মধ্যে আরও বার দু’য়েক রেবেকার সঙ্গে দেখা হল। ওর ভাই কেমন পড়াশোনা করছে, অঙ্ক ঠিকমত বুঝতে পারছে কিনা, এইসব মামুলি প্রশ্ন। আমি কোনওবারই গুছিয়ে উত্তর দিতে পারিনি। কী যে বলতে চেয়েছিলাম আর কী যে বলে ফেলেছিলাম জানি না, শুধু রেবেকার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে রহস্যময় হাসি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।
মনে মনে আমি যেন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, এমন অবস্থা বেশিদিন চললে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।
ঠিক এই সময়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার রেজাল্ট বেরল। দেখা গেল একদম লেজের দিকে র্যাঙ্ক, কোনও রকমে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ঠাঁই হল।
আমাদের গেঁয়ো স্কুলে এটা একটা অভিনব ঘটনা। পরিচিত সকলেই উচ্ছ্বসিত। শুধু আমি যেন খুব একটা খুশি হতে পারলাম না। রেবেকাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, এটা ভাবতেই বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল।
তবু হায়, চলে যেতে হয়! বাপ-পেতামোর অর্জিত পুণ্য এবং সঞ্চিত অর্থের তলানিটুকু সম্বল করে উত্তরবঙ্গ যাত্রার তোড়জোড় চলতে লাগল।
যাওয়ার আগে রেবেকাকে একবার অন্তত আমার মনোভাবটুকু জানাবার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল, কথাটা শুনে রেবেকার মুখে যদি সামান্য বিষাদের ছায়াও পড়ে, তাতেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে।
কিন্তু বলবটা কী? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করব, তারও উপায় নেই! আমার আগেই হয়তো তারা ছিপ ফেলে বসে আছে!
মনকে প্রবোধ দিলাম, এতবার চোখাচোখি হল, কথাও তো হয়েছে কয়েকবার, ও কি আর আমার মনের কথাটা বুঝতে পারেনি?
উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগের দিন বিকেলে মা মেরিকে স্মরণ করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েই পড়লাম। তাঁর কৃপাই বলতে হবে, ওদের বাড়ির সামনে পৌঁছতে একেবারে মুখোমুখি দেখা।
রেবেকা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আরে তুমি? কোনও কাজে এসেছ? ভাই কি টিউশ্যানির টাকা দেয়নি?
আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, না, না, ওসব কিছু নয়। আসলে তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। শুনেছ বোধ হয়, মেডিকেলে চান্স পেয়েছি।
রেবেকা খুব নির্লিপ্তভাবে বলল, ডেভিড বলছিল।
আমার ভেতরে ফুলতে থাকা বেলুনটা নিমেষে চুপসে গেল। তবু মরিয়ার মতো বললাম, কালই উত্তরবঙ্গে চলে যাচ্ছি।
সে একইরকম নির্লিপ্তভাবে বলল, বেশ তো।
আমি খেই হারিয়ে নিতান্ত আনাড়ির মতো বললাম, বুঝতে পারছ না, আমি আসলে—
—আমাকে ভালোবাসো, তাই তো? রাবিশ!
নিমেষে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা প্রবল ঘৃণায় কালো হয়ে উঠল।
তীব্র শ্লেষের সঙ্গে কেটে কেটে বলল, তোমাকে এতদিন ভালো ছেলে বলে জানতাম, রেসপেক্টও করতাম। শেষ পর্যন্ত তুমিও ওদের মতো হয়ে গেলে? ছি!
আরও অনেক কথাই হয়তো সে বলেছিল। কিন্তু তীব্র লজ্জা আর ভয়ঙ্কর অপমানে বিধ্বস্ত আমার চেতনা এমনই অবশ হয়ে এসেছিল যে বাকি কথা কানে ঢোকেনি।
ভাঙা মন নিয়েই উত্তরবঙ্গে যেতে হল। কিন্তু বুঝিনি, আরও বড়সড় বিড়ম্বনা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দু’চার দিন ক্লাস করার বুঝলাম, আমার সহপাঠীরা আমার চাইতে জানে বেশি, বোঝে তাড়াতাড়ি এবং চোস্ত শহুরে প্রকাশ কৌশলে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে সহপাঠিনীদের মনোযোগ আকর্ষণে অনেক বেশি দক্ষ। এতগুলো ভালো ছাত্রছাত্রীর মাঝে আমি যেন নিতান্তই এক অর্বাচীন গেঁয়ো ভূত! আমার এতদিনকার সযত্নে লালিত শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারটুকু ভেঙে চুরমার হতে সময় লাগল না।
বরাবরের মুখচোরা আমি কারও সঙ্গেই সহজ হতে পারি না। ক্লাসের পড়া মাথায় ঢোকে না বলে প্রায়ই শিক্ষকদের বাঁকা মন্তব্য শুনতে হয়। অন্যদের হাসাহাসিতে কান লাল হয়ে ওঠে। পড়ন্ত বিকেলে হস্টেলের ছাদে গিয়ে একা চুপচাপ বসে থাকি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মাঝে মাঝে অস্তগামী সূর্যচ্ছটায় স্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি। সেই অপার্থিব সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের ঘৃণায় কুঁচকে যাওয়া রেবেকার মুখটা মনে পড়লে নিজেকে আরও হীন মনে হয়।
চিকিৎসা শাস্ত্রে সেলফ হিলিং বলে একটা কথা আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ মানুষ অনেক সময় আপনা থেকেই সেরে ওঠে। আমার ক্ষেত্রেও আস্তে আস্তে তেমনটাই ঘটতে লাগল। ক্রমবর্ধমান পড়ার চাপ এবং অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা থেকে বাঁচতে আমি নিজের অজান্তে বইকেই আঁকড়ে ধরলাম। ক্রমে ক্রমে নতুনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। এবং তার চাইতেও বড় কথা, একটা কিছু করে দেখাবার জেদ যেন পেয়ে বসল আমাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রাম্য রেবেকার প্রতি আমার কৈশোরের অনুরাগ এবং তার সেদিনের ছিছিক্কারের গ্লানি ফিকে হয়ে আসতে লাগল।
যথাসময়ে এমবিবিএস শেষ হল। একটুর জন্যে গোল্ড মেডেলখানা হাতছাড়া হলেও রেজাল্ট যথেষ্ট ভাল। পোস্ট গ্রাজুয়েশান করবার জন্যে দু’বছরের কম্পালসারি কমিউনিটি সার্ভিসে যোগ দিতে হল। পোস্টিং হল পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির কাছে এক গ্রামীণ হাসপাতালে।
কর্মস্থলে গিয়ে দেখলাম, সে এক নেই-রাজ্যের দেশ। সরকারি হাসপাতাল, অথচ না আছে স্টাফ, না আছে ওষুধপত্র। এমনকী আপৎকালীন চিকিৎসার জন্যে ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুও নেই।
তবে সুবিধে একটাই, আশপাশের গ্রামগুলিতে হতদরিদ্র আদিবাসীদের বাস। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ফেল হলে তবেই তাঁরা সরকারি হাসপাতালে আসেন বটে, তবে দু’একটা মেয়াদ উত্তীর্ণ বড়ি পেলে কিংবা ডাক্তারবাবু গায়ে হাত দিয়ে রোগ পরীক্ষা করলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যান। আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে ওদের ধারণা কম, চাহিদা আরো কম। কী পাচ্ছেন আর কী কী পাওয়া উচিত ছিল, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ কিংবা কৌতূহল নেই ওদের।
দিন দুয়েক বাদে বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিলার মতো একটা জায়গায় একটা পাকা বাড়ি নজরে এল। একখণ্ড রুক্ষ টাঁড় জমির ওপরে বেশ পরিপাটি চেহারা সেটির। কাছে গিয়ে বুঝলাম, ওটা একটা চার্চ। সঙ্গে একটা মিশনারি স্কুল, এক চিলতে বাগান, সব মিলিয়ে বেশ ছবির মতো সাজানো।
এতদিন বাদে ফের আমার কৈশোরের ছেলেমানুষির দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল।
আমি জয়েন করার পর অল্পদিনের মধ্যেই হাসপাতালে আউটডোরে রোগীর চাপ বাড়তে লাগল। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকেও রোগী আসতে শুরু করল। একজন পাশ করা ডাক্তার শহর থেকে যাতায়াত না করে গ্রামে থাকছেন এবং রাতবিরেতে দরকার পড়লেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, এমন আজব কাণ্ড ওঁরা হয়তো অতীতে কখনও দেখেননি। অল্পদিনের মধ্যেই সহজ সরল মানুষগুলোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। আস্তে আস্তে আমি যেন ওদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠলাম।
কেউ কেউ সুস্থ হয়ে ওঠার পর ভগবানকে নৈবেদ্য দেওয়ার মতো ভক্তিভরে মাচার প্রথম কাকড়ি কিংবা মুরগির প্রথম ডিম নিয়ে এসে নেওয়ার জন্যে সাধাসাধি করেন।
নিতে না চাইলে অনুনয় করে বলেন, ক্যানে নাই নিবি বাবু?
পয়সা দিতে গেলেও বিপত্তি বাঁধে। অভিমান করে বলে, তু মোদের ঘরের লোক না আছিস বটেক?
এমন ভালবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য ক’জনেরই বা থাকে!
একদিন সকালে বইপত্র নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় পিটার সরেন কোয়ার্টারে এসে হাজির। এখানে আসবার পর পরই আলাপ হয়েছিল। লেখাপড়া জানা মানুষ, শিক্ষকতার সঙ্গে নানারকম সমাজসেবামূলক কাজও করেন।
জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার সরেনবাবু, বাড়ির কারও শরীর খারাপ হয়েছে?
উনি কুন্ঠিতভাবে বললেন, আমি নিজের জন্যে আসিনি ডাক্তারবাবু। আমাদের চার্চটা তো আপনি দেখেছেন। ওখানকার একজন সিস্টার কয়েকদিন হল, কোত্থেকে একজন পেশেন্টকে নিয়ে এসেছেন, তাঁকেই দেখাতে চান। আমি নিজে দেখেছি, রোগীর যা অবস্থা, তাতে এতটা পথ আনা দুষ্কর। আপনি যদি একটু কষ্ট করে—
অগত্যা চললাম ওঁর সঙ্গে। ওঁর পিছু পিছু চার্চ সংলগ্ন একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটা মাদুরের ওপর একজন রুগ্ন মানুষ শুয়ে আছেন। কঙ্কালসার শরীর। সারা গায়ে চাকা চাকা ঘা।
তাঁর মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে একজন মহিলা ঝিনুকে করে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করছেন। বিশেষ কায়দায় পরা নীলপাড় সাদা শাড়ি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না, উনিই সেই সিস্টার।
কাছে গিয়ে সিস্টার এবং পেশেন্টকে দেখে চমকে উঠলাম। রেবেকার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আমাদের সেই কালা প্রশান্ত!
নিজের অজান্তেই মুখে থেকে বেরিয়ে এল, রেবেকা, তুমি?
কথাটা যেন সন্ন্যাসিনীর কানে ঢুকল না। আমার দিকে সে ফিরেও চাইল না। গভীর মমতায় রোগীর গায়ে-মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রোগের বিবরণ দিতে লাগল।
হঠাৎ শৈশবে দেখা ধানক্ষেতের মাঝখানে শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মা মেরির মূর্তিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে হল, তিনিই যেন পরম মমতায় শিশু যিশুর মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন।

Sadharon anubhutir asadharon prokash.
Mita Kar
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৮:৪৫

ছোট ছোট সুন্দর বাঁক পেরিয়ে জন্ম নেওয়া এক মিষ্টি প্রেমের গল্প... ভালো লাগল
শুভ্রজ্যোতি রায়
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৮:৪৭

Khub Bhalo Laglo, Apurbo!
Himadri Khan
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৮:১৫

Excellent
Tamoghna sengupta
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:১৫

Darun hoyeche sir
Bikash
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৪৭

আসলে এটা প্রত্যেকের জীবনে কৈশোরের প্রথম ব্যর্থ ভালোবাসার প্রকাশ, যেটা একান্তই ব্যাক্তিগত। খুব ভালো লাগলো,হৃদয় স্পর্শ করল।
রজত দত্ত
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:১৫

Mind blowing..
Abhranil
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৩৬

আমাদের চেনাজানা পরিবেশ থেকে ভিন্ন পটভূমিকায় লেখাটি নির্মিত হওয়ার কারণে প্রথমেই পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। কালা প্রশান্ত এবং রেবেকা গল্পের উপসংহারে উপস্থিত হয়ে গল্পটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। তবে পুরুলিয়ার উপভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে 'নিবি' এর পরিবর্তে 'লিবি' আর 'না আছিস বটেক' এর বদলে 'লয় বটে' লিখলে আরও ভাল হত।
সোমপ্রকাশ ভট্টাচার্য
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:২৬

Love and sacrifice go hand in hand. What a heart touching story of unspoken love. Diction and depiction are excellent.Feel like reading more.
Swarup Bhattacharjee
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৩৮

খুব ভালো লাগল।
পুলক বসু
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৫২

বিয়োগান্তক সংযোগ,রূপক হলেও ভালো লাগলো।বাঘমুন্ডি পাহাড়ের পাদদেশে ঝুপ করে সন্ধ্যা নামার মতো গল্পটা শেষ হয়ে গেলেও রেশ থেকে রায়।
দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৫৭

সহজ, সাবলীল গদ্য। গল্পের শেষে একটা পরিপূর্ণ অবয়ব নজরে আসে।
অসীম ভট্টাচার্য।
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:৩৪

গল্পটি হৃদয়ে গভীর ভাবে দাগ কেটে গেল! কিছুক্ষণের জন্যে হলেও যেন ফিরে গেলাম ৪০/৪৫ বছর আগেকার সেই ছাত্রজীবনে! সত্যিই খুব ভালো লাগলো ! অশেষ ধন্যবাদ????????!
দেবাংশু শেখর ঢালী। হ্নদয়পুর, উত্তর চব্বিশ পরনগনা।
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৯:০৯

গল্পে র প্রথম ভাগ স্বপ্নএ দেখা যে ভাষায় লেখা যায় , ভাবতে অবাক হই। লেখক অতি ভালো ভালো।এর মতামত দিতে শিহরিত হই।
রাধাকৃষ্ণ মন্ডল।
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১০:৫৮

Seen the appraisal by Mita Kar. I agree with her.
Debiprasad Jana
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১০:৪৬

অসাধারন
অরুন কাটারুকা
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১০:১৩

Khub valo laglo sir
Poulomi shoor
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১০:২৯

Lekhar bunot ta darun
Manojit Raha
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১০:৪২

এ যেন তোর,আমার সকলেরই মন ছুঁয়ে, নিজের জীবনের বাস্তবায়ন। কি অসাধারণ লেখনী তোর। লিখে যা,লিখে যা ,এরকমই মন ছুঁয়ে যাওয়া লেখা লিখে যা। ভগবান তোকে আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছেন। খুবই ভাল লাগল বলে কয়েকবার পড়লাম।
Kamalendu Dalal
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১১:১৪

খুব ভাল
উত্তম কাঞ্জিলাল
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১১:০৪

Kub sundor
Ayan
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১২:১৯

খুব মন ছুঁয়ে গেলো স্যার।আরো এইরকম গল্পের অপেক্ষায় রইলাম।
রাজু পাল
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১২:১৮

অসাধারণ লাগল, সুন্দর ও প্রাঞ্জল, মন ছুঁয়ে গেল ????
সিদ্ধার্থ মহান্তি
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১৩:২১

Gorporta Pathok er moto ses ongse bhebechilam jak ontoto rugi hisabe Rebeka er sathe Dakter babur Milon ghotte choleche kintu lekhoker tak lagano aakankhkher songi k Matrirupe protistha deoa ta kolpanatit Osadharon.
Bidhan Chandra Gharami
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১৩:০৬

Asadharan laglo.Eiram lekha aro chai.
Swapan kumar Banerjee
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১৩:০১

জীবনের বাঁকে বাঁকে ফুটে ওঠে এমন দুষ্প্রাপ্য কিছু ফুল, যা গল্প হয়ে যায় কলমের ছোঁয়ায়। খুব ভালো লাগলো।
রীণা ত্রিবেদী
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ১৫:৪৯

দারুণ গদ্য। ভাল লাগল
মৈনাক ভট্টাচার্য
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ২০:৪৩

শাশ্বত মানব প্রেমের পরিচিত প্যানপ্যানে গন্ডী টপকে এ এক ঈশ্বরীক প্রেমের আকুতি। সুন্দর বা অসাধারন ইত্যাদি বললে লেখকের চিন্তন-প্রকাশ কে খাটো করা হয়।????????
সৌমেন ভ্ট্টাচার্য্য
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ২১:৩১

Free Flowing awesome story.....????
rxtannu
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ২৩:০৭

শেষের চমকটা,অসাধারণ।চেনা চরিত্ররাও যেন কোথাও কোথাও ভীষণভাবে অচেনা হয়ে ওঠে।খুব ভালো লাগল।
madhuparna Bhattacharya
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ০০:৫৩

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া। বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া। রেবেকার মধ্যে শেষে মা মেরি কে খুঁজে পেয়ে হয়তো এরকমই অনুভূতি হয়েছিল ডাক্তারের।
পাভেল দত্ত
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ০৩:২০

Sesh hoia o hoilo na sesh!
Pratul Kr. Bose
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ০৭:২৭

অদ্ভুত মায়াবী ভঙ্গীতে বলা শুরু করে একটা অসাধারণ মোচড় দিয়ে শেষ।
Abhisek Dutta
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ০৯:৫৮

অসম্ভব সুন্দর লাগল চেনা জায়গার নাম চেনা মানুষ গুলোকে নিয়ে লেখা এত মন জয় করা গল্প যে আমার ছোট্ট ভাই লিখেছে ভেবে আনন্দিত ও গর্বিত। লিখে যা।ভগবান তোকে এত প্রতিভা দিয়েছেন দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা এক ই মায়ের সন্তান। খুব ভাল লাগল খোকো
Anjali maity kar
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ০৯:৪৬

অরুণ কর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় একটি টান টান গল্প উপহার দিয়েছেন। প্রেমের অনুভূতি মানব দরদে রূপান্তরিত এক অসামান্য আলেখ্য তিনি বিবৃত করেছেন। গল্পটির ভাষা অসাধারণ। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।
সুশীল সাহা
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ১১:৫১

খুব ভালো লাগলো...
Arindam Ghosh
নভেম্বর ০২, ২০২৩ ১২:১৭

গল্পটিতে মানুষের প্রেমের দুটি রূপ খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হযেছে ৷ আসাধারন লাগল ৷
রঞ্জন চ্যাটার্জী
নভেম্বর ০৩, ২০২৩ ২২:২৬

khub bhalo laaglo...
Tathagata Sikdar
নভেম্বর ০৪, ২০২৩ ০২:০৪

'শেষ হয়েও হইল শেষ' - এর এই অতৃপ্তি এতটাই হৃদয় ছুঁয়ে গেল যে তার রেশ মুছে যাবে না কিছু সময় পর্যন্ত। সেই দিক থেকে এটি ছোট গল্পেরও ছোট গল্প; স্বার্থক ছোট গল্প ।
সেখ আবুল আনসার
নভেম্বর ০৪, ২০২৩ ১৩:২০

মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প। শেষের বাঁক খাওয়া চমকটা অসাধারণ। লেখকের লেখার গুনে তা এক অপরূপ মাধুর্যতায় রূপ পেয়েছে।
অশোক পাল।
নভেম্বর ১৫, ২০২৩ ২৩:৫৯

মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প। শেষের বাঁক খাওয়া চমকটা অসাধারণ। লেখকের লেখার গুনে তা এক অপরূপ মাধুর্যতায় রূপ পেয়েছে।
অশোক পাল।
নভেম্বর ১৫, ২০২৩ ২৩:০২

মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প। শেষের বাঁক খাওয়া চমকটা অসাধারণ। লেখকের লেখার গুনে তা এক অপরূপ মাধুর্যতায় রূপ পেয়েছে।
অশোক পাল।
নভেম্বর ১৫, ২০২৩ ২৩:০৩

ব্যাতিক্রমী গল্প। এতো ছোটো পরিধীতে ও মন স্পর্শ করতে সময় নেয় না।
দেবাশিস ভট্টাচার্য
নভেম্বর ২১, ২০২৩ ০০:১১

স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি তে গল্প এগিয়ে চলে তরতরিয়ে l climax যে থাকবে বোঝা যাচ্ছিলো কিন্তু প্রশান্ত কে শেষে ফিরিয়ে আনা একেবারেই অভিনব চমক এবং۔۔ লেখকের মুন্সিয়ানা l খুব ভালো লাগলো l
লিপিকা বসু
নভেম্বর ২৩, ২০২৩ ১০:০৫




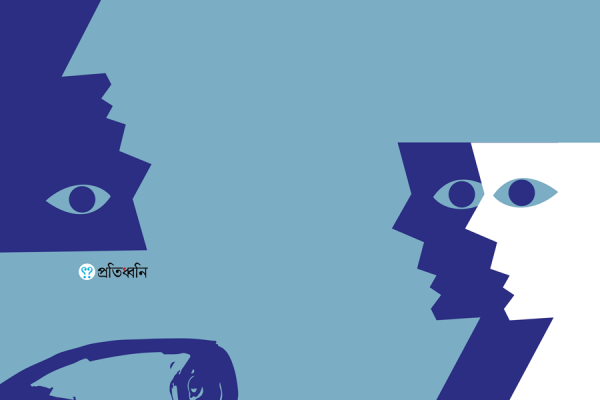


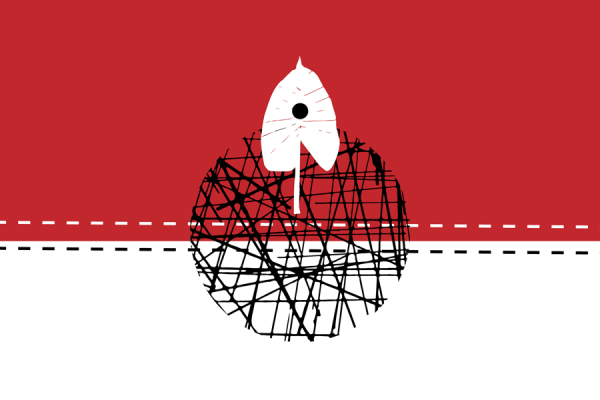

Excellent _Truly Touched The Heart'
Sajal Kanti Jana
নভেম্বর ০১, ২০২৩ ০৭:২৫