ফুলমনি ও করুণাদের পৃথিবী: নারীমুক্তির প্রশ্ন ও আধুনিক শিক্ষা

হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্সকে আমরা চিনি মূলত ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ নামক উপন্যাসের লেখিকা হিসেবে। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন অনেকে। সাহিত্যকর্ম হিসেবে উপন্যাসটি তেমন আদৃত হয়নি, কারণ একটি সার্থক উপন্যাসের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তা এই উপন্যাসে যথাযথ মাত্রায় ছিলো না। ফলে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্সের নাম সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর জীবন ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম নিয়েও আজকাল কেউ মাথা ঘামান না। ম্যালেন্স লেখিকা হিসেবে তেমন ভালো ছিলেন না হয়তো, কিন্তু তিনি কি বিস্মরণযোগ্য? অনেকেই জানেন যে, লেখিকা ম্যালেন্সের মূল পরিচয় ছিলো তিনি একজন ধর্মপ্রচারক, এবং তার যাবতীয় সাহিত্যকর্মেরও মূল উদ্দেশ্য ছিলো ধর্মপ্রচার। আমৃত্যু তিনি কাজ করেছেন জেনানা মিশনে, যার লক্ষ্য ছিলো সেই আমলের অন্তঃপুরবাসী ভারতীয় নারীদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সম্ভব হলে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। জেনানা মিশনের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড নিয়ে সেকালে ও একালে যতো বিতর্কই থাকুক, এবং যদিও জেনানা মিশন শেষ পর্যন্ত খুব একটা সফলও হয়নি, তবু উনিশ শতকের ভারতের নারীশিক্ষার ইতিহাস লিখতে গেলে জেনানা মিশনের নামোল্লেখ আবশ্যক। ম্যালেন্স ছিলেন সেই মিশনেরই বিখ্যাততম কর্মীদের একজন এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘The Apostle of Zenana’ উপাধিও লাভ করেছিলেন তিনি। ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন প্রধানত স্ত্রীশিক্ষার জন্য। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির প্রচ্ছদে শিরোনামের নিচে খুব স্পষ্ট করে লেখা ছিলো, “স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত”। সুতরাং এ উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য বিচার করার সময় এই কথাটি মনে রাখা জরুরী যে, একটি ‘সার্থক উপন্যাস’ লেখার লক্ষ্য মাথায় রেখে ম্যালেন্স ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ লিখতে বসেননি। এমনকি এই উপন্যাস ছাড়াও তার অন্য যে সমস্ত রচনার কথা জানা যায়, সেগুলোও মূলত উপন্যাসের আদলে লেখা নীতিশিক্ষামূলক আখ্যান ছাড়া কিছু নয়। এরকমই একটি রচনা হলো ‘বিশ্বাস বিজয়’, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নারীমুক্তি নিয়েও ম্যালেন্স উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে ম্যালেন্সের দু’টি উপন্যাসের যথোচিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাধ্যমে তাঁর নারীভাবনার একটি বিশ্বাসযোগ্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।
‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ দিয়েই শুরু করা যাক। উপন্যাসধর্মী এই আখ্যানটি উত্তম পুরুষে লেখা। কাহিনীর কথক একজন ইংরেজ মহিলা, যার স্বামী হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট। কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে ফুলমনি ও করুণা নামক দু’জন ধর্মান্তরিত দরিদ্র বাঙালি খ্রিস্টান মহিলা ও তাদের পরিবারকে ঘিরে। এর মধ্যে ফুলমনি হচ্ছে অতীব সচ্চরিত্র ও ধার্মিক; খ্রিস্টীয় সদগুণের আধার বলা যায় তাকে। সে সচরাচর কোনো পাপ করে না, সবসময় যিশুখ্রিস্টকে স্মরণ করে, এবং আপন দারিদ্র্য নিয়ে তার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। অন্য দিকে, করুণা খ্রিস্টান হলেও খ্রিস্টীয় সদগুণের তেমন কোনো সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তার চরিত্রে। তার সংসারে শান্তি নেই, তামাক খেয়ে সে তার সব দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। দারিদ্র্য ও মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে প্রায়ই কথায় ও কাজে খ্রিস্টের বিরুদ্ধাচরণ করে। এক জায়গায় তাকে এ কথাও বলতে শোনা যায় যে, ‘মেম সাহেব, আমরা দুঃখি লোক, পেটে খাইতে পাই না, তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম কি প্রকারে করিব?’ তবে পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর করুণার বোধোদয় হয়, এবং সে ফুলমনির মতোই সৎ খ্রিস্টান হওয়ার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে। সব মিলিয়ে, এ উপন্যাসে ফুলমনি হচ্ছে ম্যালেন্সের ‘আদর্শ খ্রিস্টান নারী', যদিও চরিত্র হিসেবে সে খুবই যান্ত্রিক এবং প্রায় অবাস্তব বললেই চলে। অন্যদিকে করুণার পাপের জন্য আমাদের যত করুণাই হোক, সে খুবই জীবন্ত একটি চরিত্র। তার ভুলগুলোই তাকে আমাদের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে; তাকে দেখলে অবধারিতভাবেই গ্রাম-বাংলার দরিদ্র, নির্যাতিত গৃহিণীদের কথা মনে পড়ে যায় আমাদের।
এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো এর তেমন কোনো প্লট নেই, কাহিনীর ওঠা-পড়া নেই, এমনকি চরিত্রগুলোও অনেকটাই কৃত্রিম মনে হয়। যখন দেখি যে, মা মায়ের মতো কথা বলছে না, কিংবা শিশুর কথা শুনে তাকে আদৌ শিশু মনে না হয়ে বরং বাইবেল-বিশেষজ্ঞ মনে হচ্ছে, তখন বারবার আমাদের মনে হতে থাকে যে, লেখিকা তার বলার কথাটাই হুটহাট করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন, একবারও ভাবছেন না এর ফলে চরিত্রগুলোর স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা। তাই এ উপন্যাসের যে তেমন কোনো শৈল্পিক আবেদন থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু লেখিকা ম্যালেন্স যেহেতু স্ত্রীশিক্ষার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন, সেহেতু এই উপন্যাসের শিল্পগুণের প্রশ্নটাকে মুলতবি রেখে বরং এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর উপর সম্যক আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা উপন্যাসটিকে নীতিশিক্ষামূলক আখ্যান হিসেবে বিবেচনা করবো।
‘বিশ্বাস বিজয়’ উপন্যাসটি আকারে ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর প্রায় দ্বিগুণ। ম্যালেন্স উপন্যাসটি লিখেছিলেন ইংরেজিতে, যার শিরোনাম ছিলো ‘Faith and Victory: A Story of the Progress of Christianity in Bengal’। বাংলায় উপন্যাসটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয় ম্যালেন্সের মৃত্যুর বেশ পরে, ১৮৬৭ সালে। নারী যদিও এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, তবে উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইউরোপীয় নারী ও ভারতীয় নারী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। এছাড়াও উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে বারবার নারীর প্রসঙ্গ আসতে দেখি আমরা। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু ম্যালেন্সের নারী-ভাবনা, সেহেতু নারী ব্যতিরেকে এ উপন্যাসের অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা আপাতত অগ্রাহ্য করবো।
উপন্যাস হিসেবে ‘বিশ্বাস বিজয়’ আরো বেশি পরিপক্ব এবং এর কাহিনীও যথেষ্ট সুঠাম। উপন্যাসের নায়ক প্রসন্ন কলকাতা-নিবাসী, সম্পদশালী ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তার স্ত্রী কামিনী অত্যন্ত ধার্মিক। কামিনী শিক্ষিত, তবে তার জ্ঞান মূলত হিন্দুশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ। পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রসন্ন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে প্রসন্ন অনেক নির্যাতনের শিকার হয়৷ এমনকি তার স্ত্রী কামিনীও তাকে ঘৃণা করা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাস করা শুরু করে। এ পর্যায়ে প্রসন্ন ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের ‘উন্নত সভ্যতা ও জীবনাচরণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে এবং হিন্দু সমাজের হীনতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার ধারণা আরো পাকাপোক্ত হয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিবারের সাথে প্রসন্ন পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করে এবং এক পর্যায়ে খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে তার স্ত্রী কামিনীসহ পরিবারের প্রত্যেকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ম্যালেন্সের যে দু’টি উপন্যাসের ভিত্তিতে এই আলোচনা, দু’টিই রচিত হয়েছে উনিশ শতকের হিন্দু সমাজের প্রেক্ষাপটে। ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর চরিত্রগুলো উঠে এসেছে কয়েকটি ধর্মান্তরিত, গ্রামীণ, নিম্নবিত্ত হিন্দু পরিবার থেকে, যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু সমাজের প্রথা ও সংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। একটিমাত্র মুসলমান চরিত্র আছে, মেমসাহেবের আয়া, যাকে ম্যালেন্স ‘মিথ্যা পয়গম্বরে’র অনুসারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই মুসলমান আয়াও উপন্যাসের শেষে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অন্যদিকে, ‘বিশ্বাস বিজয়’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছিলো কলকাতার উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো এসেছে কলকাতার এক রক্ষণশীল, ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। উনিশ শতকের ইংরেজ-প্রভাবিত আধুনিকতার অভিঘাতে এই চরিত্রগুলো দ্বিধাগ্রস্ত। ইংরেজদের কাছ থেকে কতোটুকু নিতে হবে, কতোটুকু ছাড়তে হবে, এ ব্যাপারে তারা মীমাংসায় আসতে পারছে না। উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বটিকে মূলত হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের সংঘর্ষ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু আজ আমরা জানি, আন্তঃধর্মীয় এই দ্বন্দ্ব আদতে দু’টি সভ্যতার মধ্যকার বৃহত্তর এক দ্বন্দ্বেরই অংশমাত্র।
বলাই বাহুল্য, বর্ণ, বিত্ত ও অবস্থানে ভিন্নতা থাকলেও মোটের উপর উনিশ শতকের হিন্দু সমাজে নারীদের অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। পুরুষ-শাসিত সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেই নারীরা ছিলো বিভিন্ন প্রথা ও সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। ম্যালেন্স যেহেতু ধর্মপ্রচারক ছিলেন, সেহেতু ধর্মপ্রচারের স্বার্থেই তিনি হিন্দু সমাজের এই সংস্কারগুলোকে আক্রমণ করেছেন। ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর নবম অধ্যায় থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ দিতে পারি,
‘অতঃপর সুন্দরী আরো কহিল, মেম সাহেব, এ দেশীয় লোকেরা কন্যাদিগকে বাটীর বাহিরে যাইতে দেয় না। তাহারা বলে, মেয়্যারা সর্ব্বদা পরদার ভিতরে তালা চাবি দিয়া থাকিবে; কিন্তু মনের যে তালা চাবি, তাহার মত ভাল তালা চাবি কোন স্থানে পাওয়া যায় যাইবে না।’
‘কিন্তু যদ্যপি বাঙ্গালি মেয়্যারা ঘোমটাদি দিয়া অন্তঃপুরে থাকে, তথাপি যত লজ্জা ইংরাজ বিবিদের মধ্যে পাওয়া যায়, তত অন্তঃপুরের মেয়্যাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষদের সাক্ষাতে অনায়াসে গর্ভ হওয়া ইত্যাদি বিষয় বলিতে পারে। কিন্তু ইংরাজদের মধ্যে যদি স্বামী ছাড়া পুরুষের নিকটে স্ত্রীলোক এমত বাক্য মুখে লয়, তবে সকলে তাহাকে বড়ো অসভ্য বলিয়া তুচ্ছ করে।’
‘শ্বশুর ও ভাসুরদের প্রতি যে অত্যন্ত লজ্জা করা, ইহাও বাঙ্গালি স্ত্রীদের একটি বড় মন্দ রীতি আছে; কেননা কোন স্ত্রী পুরুষকে বিবাহ করিলে স্বামির পিতা তাহার পিতা হয়, এবং স্বামীর ভ্রাতা তাহার ভ্রাতা হয়।... স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক কপট লজ্জা আছে কেননা তাহারা স্বামির ঘরে এক প্রকার ও পিতা মাতার ঘরে অন্য প্রকার ব্যবহার করে।... এদেশীয় স্ত্রীদের অন্তঃপুরে যে প্রকার অপবিত্র কৌতুকাদি হয়, ও যে প্রকার গালাগালি করে, সেই সকল ইংরাজ বিবিরা কখনো মুখেতেও আনেন না।’
একটা বিষয় এখানে খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা ম্যালেন্স যে কেবল খ্রিস্টধর্মই প্রচার করছেন, বিষয়টা মোটেও তা নয়। এক নতুন শিষ্টাচার, নতুন ধরনের সংবেদনশীলতা এবং নতুন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনাচরণের দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। তৎকালীন হিন্দু সমাজ-কাঠামোর মধ্যে সেই শিষ্টাচারের চর্চা অসম্ভব ছিলো, তাই ম্যালেন্স সেই সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন। শাদা চোখে দেখলে এই আক্রমণকে নিরপরাধ ও ন্যায্য মনে হতে পারে, কিন্তু মনোযোগী পাঠক মাত্রেরই ম্যালেন্সের ভাষায় এক ধরনের অভিভাবকসুলভ মনোভাব, কিংবা উন্নততর সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের এক অনিবার্য বোধ চোখে পড়ার কথা। ‘ভ্রমান্ধকারে পতিত’ হিন্দু সমাজকে ম্যালেন্স দেখেছেন পরিত্রাতার অবস্থান থেকে, করুণার চোখে। ‘আমরা সভ্য, এরা অসভ্য। আমরা যদি এদেরকে রক্ষা না করি, তো এরা উচ্ছন্নে যাবে'- ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে এই ধরনের একটা মনোভাব লেখিকা ম্যালেন্স স্পষ্টভাবেই নিজের ভেতরে লালন করতেন। এমনকি কোনো কোনো মন্তব্যে ভারতীয়দের প্রতি তার সরাসরি ঘৃণাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, এক জায়গায় মেমসাহেবকে আমরা বলতে শুনি, ‘অনেক ভক্ত খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা হিন্দু ও মুসলমানদের ন্যায় মন্দ আচার ব্যবহার করিয়া খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক দেয়।’ এই অভিভাবকসুলভ করুণা, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঔপনিবেশিক মাত্রই নিজেকে উপনিবেশিতের অভিভাবক ও পরিত্রাতা মনে করে। উপনিবেশিত নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারবে না, উপনিবেশিতের সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে হীন, এবং ঔপনিবেশিকের মূল্যবোধ আয়ত্ত করেই তাকে আলোকপ্রাপ্ত হতে হবে ও এগিয়ে যেতে হবে—এটা হচ্ছে উপনিবেশবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূলনীতি। এই মূলনীতির বিপদ হচ্ছে, এখানে দু’টো সভ্যতার মধ্যে পারষ্পরিক বিনিময় হয় না, বরং একটা সভ্যতা তার ভালোমন্দসহ আরেকটা সভ্যতার ভালোমন্দের উপর চেপে বসে এবং বিজিত সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই বিজয়ী সভ্যতার মূল্যবোধকেই এক সময় আপন ও শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য হয়। স্পষ্টতই, ভারতীয় হিন্দু সমাজের নিকট ম্যালেন্স হচ্ছেন বিজয়ী ঔপনিবেশিক শক্তির মূল্যবোধের প্রতিনিধি। সুতরাং হিন্দু সমাজের ভালো মন্দ সবকিছুকেই হেয় জ্ঞান করা এবং নিজ সভ্যতাকে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ববোধে ভোগার প্রবণতা তার মধ্যে থাকবেই। এইখানে তিনি নেহাত কোনো ধর্মপ্রচারক মাত্র নন, তিনি একটি সভ্যতার প্রচারকও বটেন। মানুষ ম্যালেন্সের সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধকে স্বাগত জানালেও লেখিকা ম্যালেন্সের অভিভাবকসুলভ শ্রেষ্ঠত্ববোধকে সঙ্গত কারণেই ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা উচিত হবে না আমাদের।
‘বিশ্বাস বিজয়’ উপন্যাসের পরিসর অনেক বড়ো। ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর মতো এখানেও পুরো উপন্যাস জুড়ে অজস্র জায়গায় ম্যলোন্সের অভিভাবকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। যে অধ্যায়টি বিশেষভাবে নারীকে নিয়েই লেখা হয়েছে, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়েও আমরা হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান ও দুর্দশা নিয়ে তিক্ত সমালোচনা দেখতে পাই। সেখানে অন্তঃপুর প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের দুর্দশা, বর্ণপ্রথা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে আক্রমণ করছে ম্যালেন্সের কয়েকটি চরিত্র। যেমন,
‘খ্রীষ্টানেরা যে স্ত্রীগণের স্বভাব উন্নত করিয়া, আপনাদের সমাজের ভিত্তিমূল অনেক উন্নত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহারা ইতিপূর্ব্বেই স্ব স্ব ভার্য্যাকে সাধ্যমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং যাহাতে স্বামীর হিত হইতে পারে, তাদৃশ সকল গৃহকার্য্যেই ঐ শিক্ষার সুফল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। স্ত্রীরা স্বজাতির স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জভাব ও অন্তঃপুরবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং প্রত্যেক দেশের রমণীগণ যে রূপ করিয়া থাকেন, সেই রূপে স্বদেশের রীতিক্রমে স্বামীর নিমিত্ত আপনারাই সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন বটে। স্বামীরাও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাদৃশ ব্যবহার হিন্দুগৃহের সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে আর মূর্খ ভাবিতেন না, সুতরাং তাহাদিগকে তুচ্ছ করিতেন না। পূর্ব্বে তাহারা কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন না; এখন অনেকেই ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন। এখন স্বামীরা স্ত্রীদিগকে প্রায় আত্মসদৃশ বিবেচনা করিতেন।’
“আচার্য্যপত্নী বলিলেন, ‘আমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তথাকার স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয় স্ত্রীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন। এদেশ উষ্ণপ্রধান হওয়াতে, আমাদিগকে কারারুদ্ধের ন্যায় থাকিতে হয়। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালিদের সহিত থাকিতে থাকিতে আমাদেরও তাহাদের ন্যায় অযথোচিত ও অন্তঃপুরবাস অভ্যাস পাইয়াছে। ইংলণ্ডে ‘আমরা পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, ও সুখে বাস করি।”
‘যুবতী স্ত্রীরা পিতা ও ভ্রাতার সহিত ইংলণ্ডের সকল রাস্তাতেই নিরাপদে বেড়াইতে পারেন।’
‘ইংরাজ স্ত্রীরা একদিনে যত কাজ করেন, আমাদের স্ত্রীলোকেরা এক সপ্তাহেও তাহা করিতে পারেন না।’
‘আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বুদ্ধিও আছে, কিন্তু উদ্যান-কুসুমে ও বনপুষ্পে যাদৃশ প্রভেদ, ইংরাজ ও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেও তাদৃশ প্রভেদ দেখিতেছি।’
আরো একটা জিনিস এখানে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ম্যালেন্স যখন সমস্যার আলাপ করেন, তখন সমাধানটাও প্রায় সাথে সাথেই দিয়ে দেন। ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ ও ‘বিশ্বাস বিজয়' উভয় উপন্যাসেই ম্যালেন্সের আদর্শ নারীর প্রতিরূপ হচ্ছেন একজন ইংরেজ, তথা ইউরোপীয় খ্রিস্টান নারী। বাঙালি হিন্দু নারীদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি নিহিত খ্রিস্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতার আন্তরিক অনুসরণে ও অনুকরণে—এটাই ম্যালেন্সের মূল প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনা তখনই সফল হবে, যখন বাঙালি নারীরা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক শিক্ষা, তথা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। তা, সে আমলে কিছু নারী তো আধুনিক শিক্ষা গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু এরপর? ‘অন্তঃপুরের বিবি’-রা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজি শিখলেই কি নারীমুক্তি ঘটে যায়? প্রশ্নটা আরো সহজভাবে করা যায়: ম্যালেন্স প্রস্তাবিত এই নতুন নারী আসলে কতোটা মুক্ত?
বাস্তবতা হচ্ছে, যে ইউরোপীয় নারীকে ম্যালেন্স আদর্শ নারী হিসেবে হাজির করছেন, সে-ও আসলে ব্যক্তি হিসেবে খুবই পরাধীন এবং তার গণ্ডিও খুবই সীমাবদ্ধ। সেই নারী হয়তো অন্তঃপুরে বন্দী নয়, কিংবা হয়তো সে নিরক্ষর নয়। কিন্তু নারী হিসেবে সে পুরুষতন্ত্র-নির্ধারিত প্রতিটি ভূমিকাই পালন করতে বাধ্য, এমনকি তার জন্য যদি নিপীড়নের শিকার হতে হয়, তবুও। এই কারণেই করুণা যখন মেমসাহেবের কাছে তার স্বামীর নির্যাতনের কথা তুলে ধরে, তখন মেমসাহেব করুণাকে বোঝান যে, তার দুঃখের আসল কারণ হলো তার পাপ। দারিদ্র্য মোচনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তার নিজের পাপমোচন। স্বামীকে সংশোধনের চেয়ে বেশি দরকারি হলো করুণার আত্মসংশোধন। ম্যালেন্সের আদর্শ নারী লেখাপড়া শেখে বাইবেল পড়ার জন্য এবং শিক্ষিত ও সুসভ্য স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য। সুশিক্ষা তার এই কারণেই দরকার যে, সুশিক্ষা পেলে সে আরো ভালোভাবে তার সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে, গৃহিণী হিসেবেও সে আরো সফল ও কর্মক্ষম হতে পারবে। ‘বিশ্বাস বিজয়’-এর আচার্য্যপত্নী কিংবা ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর মেমসাহেব কিংবা ফুলমনির জ্যোষ্ঠ কন্যা সুন্দরী-কে এই ধরনের আদর্শ নারী হিসেবে বিবেচবা করতে পারি। এই নারীরা শিক্ষিত এবং বাইবেল পড়তে সক্ষম। কিন্তু ‘আদর্শ গৃহিণী’ হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে তারা মুক্ত নয়। পুরুষতন্ত্রের বেঁধে সীমার বাইরে তারা এক পা-ও এগোয় না। স্ত্রীজাতির উদ্দেশ্যে ম্যালেন্সের দেওয়া কিছু উপদেশ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে:
‘সে তোমার বিবাহিত স্বামী, অতএব তাহা হইতে তুমি কো প্রকারেই পৃথক হইতে পারিবা না।’
‘ভাল গৃহিণী হওয়া খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের অবশ্য কর্ত্তব্য।’
‘তোমার স্বামী যদি তোমাকে দুই একটি কঠিন বাক্য কহে, তবে কোন প্রকারে তাহা সহ্য করিতে হইবে; কেননা বিবাহিত স্বামী হতে তোমাকে কেহ পৃথক করিয়া দিতে পারিবে না।’
‘হে নারী সকল, তোমরা যেমন প্রভুর বশীভূতা তেমনি নিজ নিজ স্বামিরও বশতাপন্না হও। ইফিষীয়| ৫| ২২|’
বলাই বাহুল্য, ম্যালেন্সের এই আদর্শ নারীদের পক্ষে আর যাই হোক, পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন ও সুখী হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ম্যালেন্স সেটা আদতে চানও না। আজ আমরা যাকে নারীমুক্তি বলছি, উনিশ শতকের মিশনারি হিসেবে ম্যালেন্স সেই ধরনের নারীমুক্তিতে বিশ্বাসই করতেন না। তাহলে ম্যালেন্সের নারীভাবনা নিয়ে আমরা এতো বাক্য ব্যয় কেনো করলাম? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আলোচনার শুরুর দিকে একবার দিয়েছি। এখন আবারও দেবো, তবে অন্যভাবে। আমরা দেখাতে চাইবো যে, ম্যালেন্সের যে নারীভাবনা, এবং যে ধাঁচের নারীমুক্তিতে ম্যালেন্স বিশ্বাস করতেন, সেটা আদতে ম্যালেন্সের ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন কোনো তৎপরতা মাত্র নয়। বরং ইংরেজ-শাসিত তৎকালীন কলকাতার শিক্ষিত মহলে নারীশিক্ষা ও প্রগতির যে ধারণা আধিপত্য লাভ করেছিলো, ম্যালেন্সের নারীভাবনা তার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়।
উনিশ শতকের নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার ইতিহাস যদি আমরা ঘেঁটে দেখি, তো অনেক পরষ্পর-বিরোধী প্রবণতা আমাদের চোখে পড়বে। এক দিকে আমরা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো ইউরোপানুগত সমাজ-সংস্কারকদের দেখতে পাবো, যারা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ কিংবা বিধবা বিবাহের প্রচলনের মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চাইছেন। অন্য দিকে দেখতে পাবো বাঙালি হিন্দু সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য মিশনারিদের ব্যাপক তৎপরতা। আবার এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে একাধিক রক্ষণশীল ধারা, যেগুলো বিভিন্ন কারণে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ম্যালেন্সের উপন্যাসেও আমরা নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত আপত্তিগুলোর উল্লেখ দেখতে পাই। স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত নয়, এই আপত্তি তো ছিলোই, রক্ষণশীলরা এমনকি এই আপত্তিও উত্থাপন করেছিলেন যে, লেখাপড়া করলে মেয়েরা বিধবা হয়ে যাবে। ‘বিশ্বাস বিজয়’ উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে কামিনী ও নিস্তারিণীর কথোপকথনে আমরা এই বিষয়টি উঠে আসতে দেখি। সেখানে নিস্তারিণী বলছে, ‘বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা আমাদিগকে বলেন যে, আমরা পড়িতে শিখিলে, বিধবা হইব।‘ কামিনী এ কথার প্রতিবাদ করার পর নিস্তারিণী আবারও বলছে, ‘আমরা বিধবা না হইতে পারি, কিন্তু যদি খ্রীষ্টান্ হইয়া পড়ি, তবে কী হবে?’ আবার ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’-এর প্রথম অধ্যায়ে আমরা করুণাকে বলতে শুনি,
‘কিন্তু ফুলমনি, আমি তোমাকে যথার্থ বলি, লোকেরা আর স্কুলের মেয়াদের (মেয়েদের) সহিত আপন পুত্রদিগকে বিবাহ দিবে না। স্কুলের মেয়াদের দ্বারা বারবার এইরূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে।’
দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এইসব আপত্তি ডিঙিয়ে যারা সেকালে নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলতেন, তারাও আসলে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে খুব একটা উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। সীমন্তী সেন তাঁর একটা প্রবন্ধে যেমন লিখছেন,
“বস্তুত বাংলাদেশে (সারা ভারতেই) ‘নারীমুক্তি’ প্রকল্পের উপায় এবং লক্ষ্য দুটোই ছিল ‘শিক্ষা’। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মেয়ের জন্য একটি জীবনজীবিকাই নির্ধারিত ছিল—তা হল গৃহিণীর।”
অর্থাৎ, শিক্ষা গ্রহণের পর সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের নারীদের মধ্যে তেমন একটা দেখা যেতো না। হাতে গোনা কয়েক জন হয়তো এর ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তাদের সাফল্য সমাজের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাছাড়া তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোক সমাজও নারীমুক্তির প্রশ্নে হয় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো, নয়তো এর বিরুদ্ধে ছিলো। এর কারণ একাধিক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে সীমন্তী সেন দেখিয়েছেন, ইংরেজ-শাসিত ভারতে আধুনিকতা আত্মীকরণের ক্ষেত্রে তৎকালীন হিন্দু সমাজ ঘর (inner domain) ও বাহির (outer domain) নামক দু’টো ক্যাটেগরি তৈরী করে নিয়েছিলো। বাহিরের জগতের সব ক্ষেত্রেই শিক্ষিত হিন্দুরা ইউরোপীয় আধুনিকতাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঘরের ভেতরে তারা চেষ্টা করেছে আধুনিকতার বিপরীতে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে। এখানে ক্ষেত্র বিশেষে আধুনিকতাকে গ্রহণ করা হয়েছে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে আধুনিকতাকে প্রতিরোধও করা হয়েছে। নারী যেহেতু ঘরেরই অংশ ছিলো, সেহেতু নারীমুক্তির প্রশ্নে এমনকি আধুনিকতাপন্থী হিন্দুরাও প্রায়ই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছেন। নারীমুক্তির জন্য সবচেয়ে খেটেছেন যাঁরা (রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রমুখ), তাঁরাও দেখা গেছে দাম্পত্য জীবনে অসুখী, নিজ নিজ স্ত্রীকে আধুনিকতায় দীক্ষিত করতে পারেননি কেউই। বলা বাহুল্য, আজ আমরা নারীমুক্তিকে যেভাবে উপলব্ধি করি, উনিশ শতকের কোনো ‘প্রগতিশীল’ হিন্দু ভদ্রলোক তা কল্পনাও করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। গোটা উনিশ শতক জুড়েই ভদ্রলোকেরা নারীশিক্ষাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন, এবং এ-ও বলা যায় যে, নারীশিক্ষা যাতে নারীশিক্ষার অধিক কিছু না হয়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ নারীশিক্ষা যাতে কোনো ক্রমেই নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে না যায়, সে ব্যাপারে তারা সতর্ক থেকেছেন। তাই উনিশ শতকের শিক্ষিত নারীদেরও সিংহভাগই ব্যক্তি হিসেবে যথেষ্ট পরাধীন থেকে গেছেন। আধুনিক শিক্ষা এমনকি শিক্ষিত নারীদের নারী-ভাবনাকেও খুব একটা প্রসারিত করতে পারেনি। কেউ কেউ ব্যতিক্রম থাকলেও অধিকাংশই ছিলেন নিয়ম-শাসিত ও নিয়মেরই পক্ষে।
উদাহরণস্বরূপ হিসেবে আমরা কৈলাসবাসিনী দেবীর কথা বলতে পারি। উনিশ শতকে কৈলাসবাসিনী দেবী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন দু’জন মহিলা। তাঁদের মধ্যে একজন স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর লেখা ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ নামক বইয়ের জন্য। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে কৈলাসবাসিনী তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, বৈধব্যদশা, ইত্যাদি প্রথা ও সংস্কার কিভাবে হিন্দু নারীদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে, বাল্যবিবাহকে তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা আসলেই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু নারীশিক্ষার ব্যাপারে তিনি যা লিখেছেন, তা পড়ার পর অবাক হতে হয়। কৈলাসবাসিনী মেনেই নিয়েছেন যে, পরাধীনতাই নারীর পক্ষে স্বাভাবিক:
‘হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহদাশয়গণ কি যুক্তিই করিয়া থাকেন; বিদ্যার কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে তদ্বারা নারীগণকে বাহির করিবে; আর নারীগণ যে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? একাল পর্য্যন্ত ত কোন দেশীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তবে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কি প্রকারে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে। জগদীশ্বর স্ত্রী জাতিকে যে প্রকার স্বভাব ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নারীগণের অধীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত।’
ম্যালেন্স তবু অন্তঃপুর থেকে নারীকে বের করে আনার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু কৈলাসবাসিনী অন্তঃপুরকেই নারীর জন্য শ্রেয় মনে করেছেন। তিনি নিজে অন্তঃপুরে থেকেই তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। অন্তঃপুর ছিলো তার কাছে বিদ্যামন্দিরের মতো, এবং শিক্ষিত নারী স্বাধীনতা লাভ করে এই মন্দির ছেড়ে বাইরে বের হোক, কৈলাসবাসিনী এটা চাননি। তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু সেই নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য নারীকে যথাযথভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে শেখানো। কেউ ‘এ, বি পড়ে বিবি সেজে সিন্দূর চুপড়ির অপমান করুক’, কিংবা ‘ইউরোপীয় বর-বর্ণিনীগণের তুল্য ভাব ধারণ করিয়া সকল পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করণে প্রবৃত্ত হোক’, কৈলাসবাসিনী সেটা চান না। বরং অন্তঃপুরে থেকে পতিব্রতা নারী স্বামীর সেবা করবে ও আগের চেয়ে ভালোভাবে সংসারের কাজকর্ম করবে- নারীশিক্ষার কাছ থেকে এটুকুই তাঁর চাওয়া। ম্যালেন্স তার দু’টো উপন্যাসেই খুব তিক্ত ভাষায় যে অন্তঃপুরের সমালোচনা করেছেন, শিক্ষিত নারী হয়েও সেই অন্তঃপুরকেই আদর্শ জ্ঞান করছেন সেই আমলের সুশিক্ষিত নারী কৈলাসবাসিনী দেবী।
আরেক কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫)-র কথা আমরা জানতে পারি, যার স্বামী ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক ও লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁর রচিত দিনলিপি ‘জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী’তে ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর সঙ্গে নৌকায় করে তাঁর নদীপথে ঘুরে বেড়ানোর গল্প শুনি। ভদ্র ও বিদ্বান স্বামীর গরবে গরবিনী এই নারী লেখাপড়া শিখেছিলেন স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী হওয়ার জন্য। সেটা হয়তো তিনি হতে পেরেছিলেন, কিন্তু এর বাইরে তিনি ছিলেন নেহাতই প্রথাগত হিন্দু নারী, যার অন্তঃকরণে আদতে তেমন কোনো পরিবর্তন এসেছিলো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। যথেচ্ছ বানানে লেখা তার ডায়েরীতে আমরা পড়ি:
‘আমরা স্ত্রীলোক আমাদের অন্তকরণ খুদুর (ক্ষুদ্র), মন অল্প, কাজে কাজে অল্পতে তুষ্টু হই।’
এই কৈলাসবাসিনীও হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনেক সংস্কার ছাড়তে পারেননি। হয়তো সাহস করে উঠতে পারেননি। এক জায়গায় তিনি লিখছেন,
‘আমি হিন্দুয়ানি মানিনে, কিন্তু বরাবর খুব হিন্দুয়ানি করি। তার কারণ আমি জদি একটু আলগা দিই তাহলে আমার স্বামি আর হিন্দুয়ানি রাকিবেন না। হিন্দুরা হলেন আমার পরম আত্মীয়। তাদের কোন মতে ছাড়িতে পারিবো না, ইহা ভেবে আমি খুব হিন্দুয়ানি করি। আমার বড় ভয় পাছে আমার হাতে কেউ না খান। তাহলে কি ঘৃণার কথা, তার কর্তে মরণ ভাল।’
মনে রাখা জরুরী যে, দরিদ্র নারী হিসেবে ফুলমনি ও করুণাদের যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী থেকে ভদ্রলোক পরিবারের গৃহবধূ কৈলাসবাসিনীদের পৃথিবীর দূরত্ব অনেক বেশি ছিলো। বরঞ্চ ‘বিশ্বাস বিজয়’-এর কামিনীর সাথেই কৈলাসবাসিনীদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ম্যালেন্স যে সময়ে তার উপন্যাসগুলো লিখছিলেন, তখন ভদ্রলোক পরিবারের নারীরাও লেখাপড়া করে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করার চিন্তা করতে পারতেন না। ভদ্র ও বিদ্বান স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী, তথা helpmet of man হতে পারার মধ্যেই নারীশিক্ষার সার্থকতা নিহিত ছিলো। বলাই বাহুল্য, এই সার্থকতা অর্জনের জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ আবশ্যক ছিলো না। বরং যে নতুন সামাজিক শিষ্টাচার এবং নতুন সংবেদনশীলতার দীক্ষা ম্যালেন্স তার উপন্যাসে দিয়েছেন, সেই শিষ্টাচারটুকু আয়ত্ত করতে পারলেই উনিশ শতকের ‘নতুন নারী’ হওয়া সম্ভব ছিলো। এই ‘নতুন নারী'-রা লেখাপড়া শেখেন, অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু দিনশেষে তারা তাদের গৃহিণীদশাই মেনে নেন। অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে আর অগ্রসর হন না। তাই ম্যালেন্সের নারী-ভাবনাকে নিছক খ্রিস্টধর্ম প্রচার বলে উড়িয়ে দিতে পারি না আমরা, কেননা সেটা তার সময়ের বৃহত্তর সামাজিক প্রবণতারই একটা অংশ। উনিশ শতকের নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে ম্যালেন্সের রচনাবলী আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে।
পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, উনিশ শতকের সেই বাস্তবতা পেরিয়ে নারীরা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেলেও নারীমুক্তির যে আদর্শ আমরা শিরোধার্য করেছি, তা আজও বেশ প্রকটভাবেই ইউরোপানুগত। সেখানে আমাদের দেশীয় নারীদের সংগ্রাম, যুগপৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার গল্পগুলো খুব বেশি জায়গা পায়নি। বরং আমাদের খেটে-খাওয়া ফুলমনি ও করুণাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সংস্কারের জালে আবদ্ধ মধ্যবিত্ত নারীতে পরিণত করতে চেয়েছি। তবে নারীমুক্তির এই আদর্শ যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পেরেছে, এ কথা বলা যায় না। এর কারণ এই অঞ্চলে নারীমুক্তির বয়ানগুলো তৈরী হয়েছে মূলত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের হাত ধরে, যারা অন্যান্য বিষয়ের মতো এখানেও ইউরোপ ও ইউরোপীয় নারীকেই আদর্শ জ্ঞান করেছে। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশ নারীমুক্তির আধিপত্যশীল বয়ানে সায় দিলেও সমাজের নিম্নবিত্ত কিংবা সাধারণ শ্রমজীবী নারীদের উপর সেই আদর্শ তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটাই নিয়ম। স্থানীয় নারীদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে নারীমুক্তির বয়ানে তুলে আনতে না পারলে নারীশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও দিনশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তি আদৌ ঘটবে না। হয়তো পোশাকে-আশাকে উপরি উপরি কিছু পরিবর্তন আসবে, নারীশিক্ষার হার হয়তো বাড়বে, কিন্তু বাস্তবিক নারীমুক্তির ব্যাপারটা দেখা যাবে সেই অধরাই রয়ে যাচ্ছে। তাই মেমসাহেব-কেন্দ্রিক নারীবাদের গণ্ডি পেরিয়ে নারীমুক্তির ধারণাকে আরো প্রসারিত করা এই সময়ে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।
তথ্যসূত্র:
১. কৈলাসবাসিনী দেবী, রচনা সংগ্রহ, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১১)
২. কৈলাসবাসিনী দেবী, জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী, (কলকাতা: এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৮)
২. গোলাম মুরশিদ, আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনী, ২০১৬)
৩. হ্যানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স, ফুলমনি ও করুণার বিবরণ, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৩)
৪. মিসিস মলিন্স, বিশ্বাস বিজয়: বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ, (কলিকাতা: ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৬৭)
৫. সীমন্তী সেন, উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষা: প্রগতিবাদ ও তার পরিসীমা, নারীবিশ্ব (কলকাতা: গাঙচিল, ২০০২)





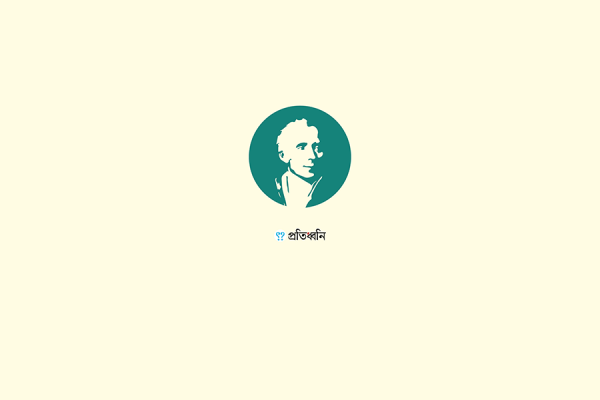

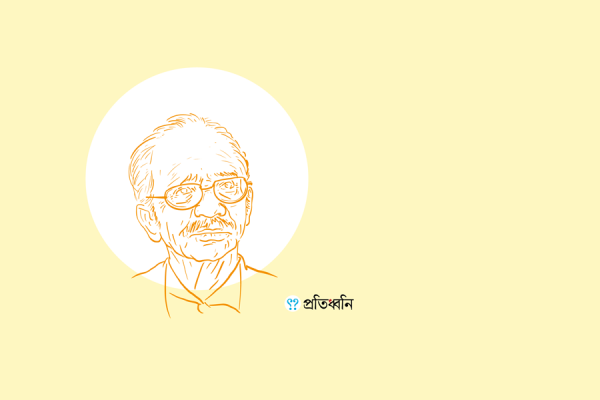

আপনার মন্তব্য প্রদান করুন