নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ বিচার
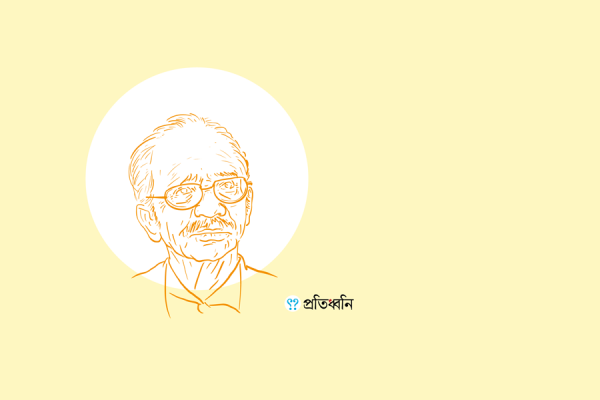
শ্রীনীরদ সি চৌধুরী ১৯৬৬ সালে ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ বইয়ে স্থান পায়। নানান কারণে ওই প্রবন্ধের রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। দেশভাগ ও ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ৭৫ বছর, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরোনোর এই সময়ে ওই প্রবন্ধের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও অভিমত ফিরে দেখা যেমন জরুরি, তেমনি সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়াটাও যুক্তিযুক্ত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববঙ্গের সমস্যা বিচারে তিনি প্রকৃতার্থে কতটা নির্মোহতার পরিচয় দিয়েছেন? ইতিহাসের সত্য অন্বেষণে এবং ইতিহাস নির্মাণে রেখেছেন কী ভূমিকা, সেসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কেননা, ভারত উপমহাদেশের তিন দেশ ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এখন পার করছে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ এবং তার অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির নানান জয়ন্তী।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গেই, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে, ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর। জন্মভূমিতে ছিলেন শৈশব-কৈশোরের ১৩ বছর। এরপর থিতু হন কলকাতায়। ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’প্রবন্ধ যখন লিখছেন, তখনো ছাড়েননি কলকাতাবাস। এরও চার বছর পর পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে, পূর্ববঙ্গে যখন শুরু হয়েছে নির্বাচনী ডামাডোল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির আহবান সংবলিত প্রস্তাব, ইঙ্গিত, মিছিল ও আন্দোলন। ১৯৭০ সালে হন বিলেত প্রবাসী, একই সঙ্গে স্থায়ী ঠিকানাও গাড়েন।
নীরদবাবুর ইংরেজ প্রীতি-পক্ষপাত ও দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। শতায়ু কীর্তিমান বাঙালিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৯৯ সালের ১ আগস্ট মারা যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন লেখালেখিতে। পূর্ববঙ্গে জন্ম নেওয়া নীরদ বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বৃহত্তর পাঠক সমাজকে বুঁদ করে রেখেছিলেন আমৃত্যু। শুধু ঢাকা, কলকাতা কিংবা ইংল্যান্ড নয়, লেখার পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এসব ভূগোলের বাইরেও। কারণ, তিনি ছিলেন বিরলপ্রজ মনীষার প্রতিকৃতি। উনার লেখা মানেই প্রজ্ঞার সঙ্গে বিতর্কের জমাট বুনন। বিতর্ক কখনোই পিছু ছাড়েনি, কিন্তু আমলে নেননি কখনোই। অপ্রিয় হওয়ার সাহস ছিল সহজাত। ফটোকপি মেমোরি বলতে যা বোঝায়, ছিলেন তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। সমাজ-রাজনীতির যেকোনো বিষয়কে বিশ্লষণ করেছেন প্রজ্ঞার ঔদার্যে। এসব বিশ্লেষণ ও অভিমত কার পক্ষে গেল আর কার বিপক্ষে গেল, কে কীভাবে নেবেন, সেসবে ছিল না বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আর বিতর্ক একারণে সমান্তরালভাবে বহমান ছিল।
নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখার বড়গুণ হলো তাতে বহুকৌণিক দৃষ্টি রাখার সুযোগ থাকে অবারিত। পূর্ববঙ্গের সমস্যা প্রবন্ধে কি আমরা সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে খুঁজে পাই, নাকি এই নীরদ সম্পূর্ণ আলাদা, চেনা চৌহদ্দির বাইরের কেউ। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ত্ব-ভূগোল ও জাতীয়তার আলোচনায় উনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে কতটা নির্মোহ সত্য জারি রয়েছে, সেসব বিচারে ও পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে এই লেখা।
‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধের বয়স প্রায় ৬০ বছর। পাঁচ পর্বে এটি কলকাতার শতবর্ষী দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় যথাক্রমে ১১ভাদ্র ১৩৭৩, ২৮ আগস্ট ১৯৬৬; ১৩ ভাদ্র ১৩৭৩, ৩০ আগস্ট ১৯৬৬; ১৫ ভাদ্র ১৩৭৩, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬; ১৮ ভাদ্র ১৩৭৩, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬; এবং ২০ ভাদ্র ১৩৭৩, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ প্রকাশিত হয়।
বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কেন বিংশ শতাব্দীর ওই বছরের ওই সময়ে এরকম একটি প্রবন্ধ লিখিত হলো বিষয়টা বিবেচনায় নেওয়া দরকার। ১৯৬৬ সাল পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর। কেননা, ওই বছরই শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এক্ষণে স্মরণ করা জরুরি, কী ছিল ছয়দফার দাবিসমূহে:
এক. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে।
দুই. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে।
তিন. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে, তার ব্যবস্থা সংবলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।
চার. দুই অঞ্চলের বৈদেশিকা মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।
পাঁচ. দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।
ছয়. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।
ছয় দফার উল্লিখিত দাবি বাঙালির কাছে মুক্তির সনদ হিসেবে স্বীকৃতি পায় স্বল্পসময়ের মধ্যেই। নীরদচন্দ্র এই প্রবন্ধ লিখেছেন ওই প্রেক্ষাপটেই। যদিও পুরো প্রবন্ধের কোথাও এ সম্পর্কিত কোনো প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। শুধু একটা জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘এখনও ভারতবর্ষ হইতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের ভীতির কারণ আছে। এই ধারণার বশেই ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে নিজেদেরকে অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় দেখিয়া উহারা এত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সঙ্কটে সামরিক ব্যবস্থা উপযুক্ত করা হয় নাই বলিয়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা অভিযোগ করিয়াছিল। যদিও এই আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না বলিয়াই আমার বিশ্বাস, তবু তাহাদের মনে যে ভয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেজন্যই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্যে স্বতন্ত্র সামরিক ব্যবস্থারও দাবি করিতেছে।’এই প্রবন্ধের সবিশেষ সৌন্দর্য ও গুরুত্বের জায়গা হলো, যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রবন্ধটা নির্মাণ করা হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত রেখেও তাৎপর্যবাহী একটা প্রবন্ধ সৃজনের ক্ষমতা।
‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেসময় এটি পাঁচ পর্বে প্রকাশিত হয়। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল, প্রবন্ধটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত হলেও এটাকে ঠিক অংশ বা অধ্যায় বললে বিষয়টা স্পষ্ট হয় না। পাঁচটি খণ্ড কি বলা যায়? যা দৃশ্যত খণ্ড মনে হলেও প্রকৃতার্থে অখণ্ড সত্তাই নির্মিত হয়েছে প্রবন্ধের সকল শর্তকে মান্যতা দিয়ে। এগুলো হলো—
এক. প্রকৃতির বিধান; দুই. জাতিত্ব, জীবনযাত্রা, ইতিহাস; তিন. ‘দুই বাংলার ঐক্যসাধন আজ বাঙালির হাতে নাই-’ ক. প্রবল বিদ্রোহ, খ. দুইটি গুরুতর প্রশ্ন, গ. হিন্দু-মুসলমান বিরোধ; চার. দুই বাংলার তুলনা; পাঁচ. পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলন হবে কি, ক. প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও উহার সম্ভাবনা।
প্রবন্ধটি একক পরিসরে ছোট নয় মোটেই। কিন্তু উপজীব্য বিষয় গুণে এ আধার দীর্ঘকায়ও নয়। কেননা এর বিষয়বস্তু, যেখানে একটা জনপদের শিকড়ের নদ-নদী, আবহাওয়া-জলবায়ু, ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতির সমস্ত কিছুই হাজের নাজেল হয়েছে সবিস্তারে-বিশদ যুক্তিতর্ক জারি রেখে।
প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রকৃতির বিধানের কথা। অর্থাৎ যা অনিবার্য, নিয়তিবিশেষ। কেননা এখানে কারোরই কোনো প্রকার ইতরবিশেষ করার ক্ষমতা নেই। এখানে নীরদ মূলত যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, সেটি হলো পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গ অবস্থানগত কারণেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দিল্লির সঙ্গে তার কোথায় মিল আর কোথায় অমিল, সেটা এখানে নিরূপণ করার চেষ্টা রয়েছে। পুরো প্রবন্ধে দিল্লি, উত্তর-ভারতকে উত্তরাপথ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং উত্তরাপথের সঙ্গে সম্পর্কটা যুক্তিযুক্ত কারণে কতটা ছিল, সেই প্রাচীনকাল থেকে তারও একটা সুলুকসন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধের বিষয় পূর্ববঙ্গ হলেও ঘুরেফিরে চকিতে হাজির হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা। লেখক অবশ্য স্পষ্ট করেই পশ্চিমবঙ্গ বলতে কলকাতাকেই বুঝিয়েছেন। উত্তরাপথের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কলকাতা আর পূর্ববঙ্গের বিষয়টাও এক নয় বলে অভিমত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, অবিভক্ত বঙ্গ, অবিভক্ত বাংলা বললে যে একত্র বাংলাকে বোঝানো হয়, সেটা প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশশাসিত বাংলার সময়কালেও পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সকল সময় ছিল। নীরদচন্দ্র সেই স্বাতন্ত্র্যর পেছনে প্রকৃতির বিধানকেও খুঁজে ফিরেছেন। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হইতেই বাংলার রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রভাবের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিৎ। আমি যাহাকে ‘প্রাকৃতিক বাংলা’ বলিয়াছি উহা ভূগোলের বাংলা, রাজনীতির নয়।’ পূর্ববঙ্গের গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়, বঙ্গোপসাগরের অবস্থান, তার পুবের ও পশ্চিমের বাস্তবতা এবং উত্তর ও দক্ষিণের প্রকৃতি প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলিকেও তিনি আলোচনায় হাজির করেছেন এবং সেসবের কারণে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদের মানস গড়নের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছেন।
এ খণ্ডের আলোচনার একেবারে শেষাশেষি এসে তিনি যে বয়ান হাজির করেছেন, তার সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। তিনি বলেছেন, “বাংলার সমাজ ও সভ্যতা হিন্দু সভ্যতারই একটা স্থানীয় রূপ, সুতরাং আদিবাস ও আদি জীবনের সহিত যোগ রাখিতে হইলে তাহাকে আর্যাবর্তেও যাইতে হইত—বিশেষ করে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের। ইহা ছাড়া মুসলমানী আমলে যাইত বৈষয়িক উন্নতির আশায়। কিন্তু দিল্লীতে ‘রাজাই করিতে গিয়া’ অনেককে খিলাপও করিতে হইত ‘দুধে-ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কে বা দিল…’ ইত্যাদি।”
নীরদচন্দ্র যে বলেছেন, ‘বাংলার সমাজ ও সভ্যতা হিন্দু সভ্যতারই একটা স্থানীয় রূপ’, সেটা সর্বাংশে সত্য নয় এবং বিষয়টা এতটা সরলরৈখিকও নয়। ইতিহাসের সত্যও উনার এই দাবিকে সমর্থন করে না। বাংলার সমাজ ও সভ্যতা কোনো একক সভ্যতার স্থানীয় রূপ নয়। বরং একাধিক সভ্যতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বাংলা তার নিজস্ব সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখানেই বঙ্গের অন্যান্য জনপদ থেকে পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ এক জনপদ। এ প্রসঙ্গের অবতারণা অন্য একটা খণ্ডেও রয়েছে। সেখানে এই নিয়ে আমরা আরও কিছু যুক্তি হাজির করার চেষ্টা করব।
প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম ‘জাতিত্ব, জীবনযাত্রা, ইতিহাস’। নীরদচন্দ্র এখানে পূর্ববঙ্গের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ধরার চেষ্টা করেছেন, যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে তার জীবনযাত্রা ও ইতিহাসের সম্যক পরিচয়। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে ভারতের বাইরে থেকে যে অভিগমন ঘটেছে, সেখানে অনেকখানি পৃথক বাস্তবতা রয়েছে পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে। উত্তরাপথ দিয়ে অভিগমন যেমন ঘটেছে, পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে পূর্ব থেকেও অভিবাসীরা এসেছে। ফলে, এই জনপদ ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের মতো নয়। চেহারাতেও সেই ছাপ প্রবলভাবে রয়ে গেছে। এমনকি পূর্ববঙ্গের মানুষের ঘর গেরস্থালিও উত্তরাপথ থেকে আলাদা। তিনি লিখেছেন, ‘যদি কেহ পশ্চিম এশিয়ার পুরাতত্ত্ব পড়িয়া থাকেন, তিনি স্বীকার করবেন এই সব জিনিস সেই অঞ্চলের নূতন প্রস্তরযুগ বা প্রথম তাম্রযুগের দান। এগুলোর উৎপত্তি কৃষির উৎপত্তির সঙ্গে হইয়াছিল। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া বা পারস্যে যে-সব প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ঠিক হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের গ্রামের মতো। পূর্ববঙ্গের গ্রামের গড়নে ও চেহারায় অন্যরকম বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে ধরা দেয়। উহাতে বাড়ি ও বাস্তভিটা ছাড়া ছাড়া, প্রতিটি বাড়ি দরমার বেড়া বা টাট্টি দিয়ে ঘেরা। কিশোরগঞ্জ শহরে ও পৈতৃক গ্রাম বনগ্রামে আমাদের বাড়িও ঠিক এই ধরনের ছিল। এই সব বাড়ির চারিদিকে বাঁশের ঝাড় থাকিত। দূর হইতে গ্রামগুলিকে জঙ্গল বলিয়াই মনে হইত, গ্রাম বর্ধিষ্ণু ও ভদ্রগৃহস্থবহুল না হইলে গাছপালার ভিতর দিয়া চাল বা ছাত দেখাই যাইত না। এই সব বাড়ি ও গ্রাম আসিয়াছিল বিষুবরেখায় নিকটবর্তী বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে।’
নীরদবাবু বিশদ যুক্তি হাজির করেছেন তার এই সিদ্ধান্ত ও পর্যবেক্ষণের পক্ষে। ঘরবাড়ি, সমাজের গড়নের মতো তার দেহের গড়নেও রয়েছে পার্থক্য। তিনি মনে করেন, ‘এই পার্থক্য বাংলার ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। উহার ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না’। এখানে এসে নীরদবাবু ইতিহাসের এমন এক সত্যকে আবিষ্কার করেছেন, যা পূর্ববঙ্গবাসী যে কোনো বাঙালির জন্যই শ্লাঘার। গভীর এষণার আলোকে এই অন্বেষণ বাঙালিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার লক্ষ্যে অতীতের আলোয় ভবিষ্যতকে নির্মাণের দিশা জোগায়। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের নানাদিকে স্পষ্ট ও উগ্র স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করিবে না, ইহা মনে করাই অসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে সত্যকার বাঙালিত্ব প্রকট হইবার বহু আগেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়াছিল। যেদিন মাৎস্যন্যায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বাংলার লোক গোপালকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আরম্ভ। তখনও বাংলা ভাষা জন্মায় নাই, বাংলার বিশিষ্ট সংস্কৃতিও বিকশিত হয় নাই। তবু উত্তরাপথের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে নাই।’
এক্ষণে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। যে প্রসঙ্গ হাজির করেছেন নীরদবাবুও। ভারতের একদা নাম ছিল আর্যাবর্ত। অর্থাৎ আর্যদের আবাস বা বাসস্থান। কিন্তু পূর্ববঙ্গ কখনোই পুরোপুরি আর্যদের আবাসস্থান হয়ে ওঠে নাই। তিনি মনে করেন, ‘উত্তরাপথের সমাজ ছিল মোটের উপর বিশুদ্ধ আর্য। কিন্তু বাংলার সমাজ তিন স্তরের—বিশুদ্ধ আর্য, বর্ণশঙ্কর ও বিশুদ্ধ অনার্য।’ আর্যাবর্ত এক সময় হয়ে ওঠে হিন্দুস্থান, সেটা তো মুসলমানদের কারণে। যে জনপদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বসবাস, সেটা তো পূর্ববঙ্গই। আরবে যখন ইসালামের আবির্ভাব ও বিকাশ হচ্ছে ঠিক তখনই ভারতবর্ষে ইসলামেরও যাত্রা ঘটে। যে জনপদে ইসলাম আরবের মতোই একইসঙ্গে বিকশিত হতে থাকে সেটা পূর্ববঙ্গ। এবং তা সম্ভব হয়েছে কেবল পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই। নীরদবাবু অবশ্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে না বললেও আরব বণিকদের সূত্রে ইসলামের যাত্রা শুরুর ইতিহাসকে মান্যতা দিয়েছেন। আমরা মনে করি, পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যতার পেছনে এসব বিষয় আরও বেশি করে তালাশ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকূট রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই এখানে একাধিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে বলে সাধন কমল চৌধুরী বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন বইয়ে উল্লেখ করেছেন। লালমনিরহাটে হিজরী ৬৯ সাল মোতাবেক খ্রিস্টীয় ৬৪৮ সালের মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলায় রাষ্ট্রের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, এরকম গড়পড়তা একটা কথা এখানে প্রতিষ্ঠিত। ব্রজদুলাল চট্রোপাধ্যায় এ-সম্পর্কিত গবেষণায় স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘বাংলায় সংহত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল।’
নীরদচন্দ্রও এই প্রবন্ধে মুসলমান শাসনের প্রসঙ্গ টেনে আগ্রহোদ্দীপক এক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এবং তার মধ্যেও পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যিক সত্তার দীর্ঘ এক ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসের একটা মোটা হিসাব লওয়া যাক। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে স্বাধীন মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ৭৪১ বৎসর। ইহার মধ্যে বাঙালি স্বাধীন বা কার্যত স্বতন্ত্র ছিল ৪২৬ বৎসর, আর ৩১৫ বৎসর ছিল উত্তর ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীন, তা সে দিল্লীতেই হউক বা আগ্রাতেই হউক। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে অপ্রতিহত ও অনিবর্তিত না হইলে কেহই বাংলাদেশকে উত্তরাপথের সহিত যুক্ত রাখিতে পারে নাই। এই অত্যন্ত স্থূল ব্যাপারটা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান।’
নীরদবাবুর উপর্যুক্ত অনুসন্ধান আমাদেরকে যেমন গৌরবান্বিত করে, তেমনি কিছু কিছু অনুসন্ধান প্রশ্নের মুখোমুখিও দাঁড় করায়। এবং মনে হয় কখনো কখনো তিনি ইতিহাসের সত্য উপস্থাপনে ঔদার্যের পরিচয় দেননি। যেমন নীরদবাবু লেখেন, ‘রাজধানী দিল্লী চলিয়া গেলেও বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জীবনের খুব ইতরবিশেষ হয় নাই এই কারণে যে, বাংলাদেশকে একজন গভর্নরের অধীন করিয়া অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহাকে প্রায় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই দেওয়া হইয়াছিল।’ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হলেও ইংরেজ শাসনের পুরোটা সময়ে তা রাজধানী কলকাতা থাকুক আর দিল্লিতেই স্থানান্তরিত হোক বাঙালির ওপর ইংরেজ শাসকেরা যে অত্যাচার করেছেন, কোনো কিছুতেই সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হওয়ার নয়। নীল চাষের নামে পূর্ববঙ্গবাসীর ওপর ব্রিটিশদের যে অত্যাচার তার ছিটেফোঁটাও ভারতের অন্যত্র হয় নাই। ইংরেজদের অত্যাচারে সাক্ষ্য মেলে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকাতেও। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে নীরদবাবু প্রকারান্তরে তাঁর ইংরেজপ্রীতির সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ কিংবা সংশয় নেই।
পূর্ববঙ্গে ইসলামের প্রচার প্রসঙ্গে নীরদবাবু উল্লেখ করেছেন, ‘বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার বিজেতা আফগান, পাঠান বা তুর্কেরা করে নাই, করিয়াছিল সমুদ্রপথে আসিয়া আরব প্রচারকেরা। এই আরব প্রচারকেরা যাহা প্রচার করিত সেটা ইসলামের আরব দিক—অর্থাৎ ধর্ম ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের রীতি ও নিয়ম। মুসলমান সভ্যতার পার্থিব দিকের প্রতি তাহাদের তেমন মনোযোগ ছিল না, কারণ যে-যুগে ভারতবর্ষ মুসলমানের অধীন হয় সেই সময়ে ইসলামের সংস্কৃতি—অর্থাৎ সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য ইত্যাদি লইয়া যে সংস্কৃতি তাহা তুর্ক ও পারসিক মুসলমানের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। তাই আরব প্রচারকের হাতে মুসলমান হওয়ার ফলে বাঙালি মুসলমানের লৌকিক দিক হইতে বাঙালি থাকিবার স্বাধীনতা মোটামুটি অব্যাহত রহিল।’ নীরদবাবুর বয়ানের এই সত্য পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এখনো জারি রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেককিছু বদলে গেলেও বীজ রয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের সমাজের গভীরে।
‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধের তিন নম্বর খণ্ডের বিষয়, ‘দুই বাংলার ঐক্যসাধন আজ বাঙালির হাতে নেই’, এর আবার রয়েছে তিনটি অংশ—প্রবল বিদ্রোহ, দুটি গুরুতর প্রশ্ন ও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ।
প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ১৯৬৬ সালে লিখিত। তখন ভারত বিভক্তি ও দেশভাগের বয়স দুই দশকও হয়নি। ফলে, প্রকাশ্যে না হলেও একধরনের গুঞ্জরণ নিভৃতে কিংবা কিছু মানুষের মধ্যে ছিল যে, পাল্টে যেতে পারে ৪৭ এর প্রেক্ষাপট। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাস্তবতায় সেটা অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। কেননা, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালির টানাপোড়েন নানান ঘটনায় উচ্চকিত হয়ে স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। এবং বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ততদিনে ছয় দফা দাবির পক্ষেও সরব হয়ে উঠেছেন। ছয় দফা দাবি জানানো হয় ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। ‘পূবর্বঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে একই বছরের আগস্টের শেষে ও সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে। ইতোমধ্যে এই প্রবন্ধের বয়স ৬০ ছুঁইছুঁই। এইসময়ে অনেক প্রশ্নের ফয়সালা হয়েছে বিশেষ করে প্রবন্ধটির তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়। এর বাইরে এখানে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হলে বুঝতে সুবিধা হবে, নীরদবাবুর পূর্ববঙ্গের সমস্যা বিচারের পদ্ধতি ও এষণার সিদ্ধান্তসমূহ, যা আলোকপাত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘বিংশ শতাব্দীতে তিনবার বাংলার রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ফলে আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি চারিটি বাংলা দেখিয়াছি, হয়তো কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আরও দেখিতে পারি।’ একটা প্রবন্ধের শক্তি কোথায় নিহিত এবং প্রবন্ধ কীভাবে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও তার আত্ম অন্বেষায় কামিয়াবি করে তুলতে পারে নীরদবাবু আলোচ্য প্রবন্ধে তার প্রমাণ রেখেছেন। বাস্তবিকই এই প্রবন্ধ প্রকাশের মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় আরও একটি বাংলা দেখার সুযোগ তিনি পান। পূর্ববঙ্গ এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়।
চতুর্থ খণ্ডের বিষয় দুইবাংলার তুলনা। দুই বাংলা অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা, যার সেই সময়ের সাংবিধানিক নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব বাংলা হয়ে এখন বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম এক রাষ্ট্র। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্য। নীরদবাবু যখন এই প্রবন্ধ লেখেন, তখন দুই বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান একটা প্রদেশ বা রাজ্য হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের অনেক রাজ্যের মধ্যে একটি। তুলনাটা হয়েছিল সেই বিবেচনায়। ফলে, এই খণ্ডের আলোচনা বর্তমানের সময়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, সেসব আলোচনার অনেককিছুই এখন বাস্তবে পরিগণিত হয়েছে এবং কতিপয় বিষয় হাজির হয়েছে মীমাংসিত এক সত্যরূপে।
কিছু কিছু বিষয় অবশ্য অতীতের আলোয় বর্তমানকে নির্মাণের প্রশ্নে পাঠ করা যেতেই পারে। নীরদবাবু যেমনটা বলেছেন, “পশ্চিম পাকিস্তান ইসলামী পশ্চিম এশিয়ার পূর্বতন অংশ মাত্র। সুতরাং, পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান, আরব অথবা পারসিকের চেয়ে কম বিদেশী নয়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের সহিত উত্তরাপথের পার্থক্য বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমান নয়, ক্রম প্রকাশমান। অর্থাৎ পূর্বে অল্প পার্থক্য, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে গিয়া অতি স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্থক্যটা এইভাবে ক্রমিক হওয়াতে অনুভূত হইবামাত্র ধাক্কার মতো লাগে না। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের ‘শক্-অ্যাব্সবার’ বা বাফার নাই। এই দুইয়ের বৈষম্য মোটেই ক্রমবর্ধমান নয়, প্রথমেই একেবারে গুরুতর ধাক্কা, অর্থাৎ মোটরের বা ট্রেনের ‘কলিশ্যনে’র মতো লাগে। উহা একেবারে প্রথম হইতেই সংঘর্ষ হইয়া দাঁড়ায়।”
পূর্ববঙ্গের সমস্যা প্রবন্ধের খণ্ড পাঁচে-র বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিল হবে কি এবং প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও উহার সম্ভাবনা। এটিও চার নম্বর খণ্ডের মতো একেবারে ওই সময়ের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে উত্থাপিত প্রশ্নবিশেষ। সময় নিরপেক্ষ কোনো বিষয় না হওয়ায় তার ফয়সালাও কাছাকাছি সময়েই হয়ে গেছে। তবে কয়েকটি প্রসঙ্গ রয়েছে যেগুলোর খোলতাই করা হলে নীরদবাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, ‘পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এতটুকু আছে যে, উহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব।’ আমরা মনে করি, স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের মূল শক্তি নিহিত ছিল তার সমাজের মধ্যে। সামাজিক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সম্মিলনেই পূর্ববঙ্গের স্বাধীন হওয়া সম্ভব—বাস্তবে হয়েছেও তাই।
নীরদবাবু এই প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমানের স্থান যতই অসন্তোষজনক হউক না কেন, উহা ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের স্থানের অপেক্ষা খারাপ হইবার কথা নয়। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমানের নিজস্ব জীবন অন্য রকম করিবার কোনও আগ্রহ ইংরেজের ছিল না। তেমনই পূর্ববঙ্গের মুসলমানত্ব, মুসলমানী জীবনযাত্রা ও মুসলমান-প্রাধান্যের ক্ষতি করিবার কোনও ইচ্ছা পাকিস্তানের থাকিতে পারে না, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানও মুসলমানের দেশ, ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত।’
নীরদবাবুর এই ধারণা মোটেও সত্য নয়। তিনি দূর অবলোকনে এই সত্য আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে ধর্মের সত্যকেই বড় করে দেখেছেন। কিন্তু বাস্তবতা তেমনটা ছিল না মোটেই। পাকিস্তানের নিগড়ে পূর্ববঙ্গের দুই যুগ কেটেছে শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তান সমস্ত রকমের অন্যায় অবিচার অনিয়ম ও দুর্নীতি কায়েম করেছে ধর্মের নামে—ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যার ভয়ংকর রূপ উন্মোচিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে। নীরদবাবুর যেহেতু এতদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই ধর্মবোধ ও ইসলাম সম্পর্কে মোটাদাগের ধারণা থেকে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায়-অত্যাচারের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের অনিয়ম-অবিচারের প্রতিতুলনা টেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।
নীরদবাবু ‘প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও উহার সম্ভাবনা’ অংশে উল্লেখ করেছেন, “প্রকৃতপক্ষ পূর্ববঙ্গের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা আছে। সেটি এই—পাকিস্তানের আধিপত্য মানিয়া ও উহার রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া যতটুকু স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা। ইহাকে একপ্রকার ‘ডমিনিয়ন স্টেটাস’ বলা চলে।” নীরদবাবুর কাছে তখনই বোধ করি বাঙালির জেগে ওঠার খবর পৌঁছে নাই। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার দাবি যে প্রকারান্তরে স্বাধীনতার ঘোষণাই সেটা পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা থেকে দূরে থাকার কারণে উনার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। অথচ ততদিনে পূর্ববঙ্গ জেগে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় তখন নবজাগরণের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। মনে রাখতে হবে সকলের অজান্তেই ১৯২১ সাল থেকে ঢাকায় নবজাগরণ সংঘটিত হতে থাকে। তিনটি ঢেউয়ে এই নবজাগরণের সর্বৈব প্রকাশ ঘটে। প্রথম ঢেউয়ের বিস্তার কাল হলো ১৯২১ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিস্তার কাল ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত। তৃতীয়ও সর্বশেষ ঢেউয়ের বিস্তার কাল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।
প্রথম নবজাগরণের ঢেউয়ের কেন্দ্রে ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষ। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ—বর্তমানের ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এ. এফ. এম আবদুল হক, ঢাকা কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখ। নেপথ্যে সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা কলেজের বাংলার অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর। পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হন কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আ ফ ম আবদুর রশীদ প্রমুখ। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বার্ষিক সম্মেলন ১৯২৭ সালের ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ। সম্মেলনের কার্যসূচিতে প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ছাড়াও আরও যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: কাজী নজরুল ইসলাম, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মোহাম্মদ কাসেম, সুশীলকুমার দে, সৈয়দ এমদাদ আলী, অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, খান বাহাদুর আবদুল রহমান খান, বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ।
মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। শিখার মুখবাণী ছিল, ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখান আড়ষ্ট, মুক্তি সেখান অসম্ভব।’ মুসলিম সাহিত্য সমাজের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে দশবছর ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।
মুসলিম সাহিত্য সমাজের ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি লক্ষ করলে এরা সেইসময়ে কতটা প্রভাববিস্তারী ভূমিকা পালন করেছেন, তা প্রকৃতার্থে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।
সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পাঁচ দফা প্রস্তাব হাজির করে মুসলিম সাহিত্য সমাজ। যা উপস্থাপন করা হয় সংগঠনের ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে। এগুলো হলো—
এক. এই সভা বাংলার মুসলমান নর-নারীকে বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিকে কোরানের সহিত পরিচিত হইবার অনুরোধ জানাইতেছে।
দুই. এই সভা বাংলার পল্লীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবার জন্য দেশের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে।
তিন. এই সভা বাংলার বিভিন্ন মক্তব ও বিভিন্ন মাদ্রাসায় যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে।
চার. এই সভা বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দকে পর্দা প্রথা দূরীকরণার্থে আদর্শ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
পাঁচ. এই সভা সাহিত্য সমাজের কর্মীবৃন্দকে মুসলিম ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক আরবী ও ফার্সি গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিবার জন্য একটি অনুবাদ কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
মুসলিম সাহিত্য সমাজের আলোয় গড়ে ওঠা ঢাকার এই নবজাগরণ একার্থে পুরো বাংলাদেশের অর্থাৎ সেদিনের পূর্ববঙ্গেরই নবজাগরণ। তখন ঢাকাকে ঘিরেই পূর্ববঙ্গের বিকাশ আন্দোলন সংগ্রাম এমনকি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকার এই নবজাগরণের এখন পর্যন্ত বৌদ্ধিক স্বীকৃতি নেই। অথচ এই নবজাগরণের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো একটা স্বাধীন দেশের জন্ম।
আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়, উনিশ শতকের প্রারম্ভে ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রহ্মসভা। এই দুটি ঘটনা উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণে মাইলফলক ঘটনার সূচনা করে। ঠিক তার একশ বছর পরে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এই দুটি ঘটনাও ঢাকার নবজাগরণকে বাস্তব সত্যরূপে হাজির করে।
নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো সদর্থক অর্থেই বিরলপ্রজ একজন পণ্ডিতও এই নবজাগরণে সম্পর্কে বুঝে উঠতে পারেন নাই। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের ন্যায্য হিস্যার আন্দোলন-লড়াই-সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ‘একদিকে উচ্ছ্বাস ও আবেগ, আর একদিকে স্থির বুদ্ধি। সুতরাং এ-দুই এর মধ্যে দ্বন্দ্বে সহজে কাহারও জিত হইবার নয়। আমার বিশ্বাস, পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পর বিরোধ করিয়া কোনও বিশেষ হারজিত দেখাইতে পারিবে না, সুতরাং পূর্ববঙ্গের সমস্যার সমাধান এই দুটির কার্যকলাপের দ্বারা হইবে না।’ নীরদবাবু কেন এবং কী মনে করে ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধের এরূপ উপসংহার টেনেছেন, তা আমাদের কাছে প্রহেলিকা বিশেষ। তবে একটা বিষয় হতেই পারে, তেরো বছর বয়সে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার পর তিনি এই জনপদের পরিবর্তন সম্পর্কে সেভাবে সম্ভবত ওয়াকিবহাল ছিলেন না। একারণে ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধে তিনি ঐতিহাসিক জায়গা থেকে যেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন, তা শুধু তারিফযোগ্য নয়, বাঙালি বিশেষ করে বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষার ক্ষেত্রে মাইলফলক বিশেষ। ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ব, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নীরদবাবুর বোঝাপড়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিস্ময়কর, অভিনব ও বিশেষভাবে তাৎপর্যবাহী। কিন্তু তিনি যখন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অভিমত দিয়েছেন তার সবটাই প্রশ্নাতীত নয়। উল্টো কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব হাজির করেছেন, সেসবে বিস্তর দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। এর পেছেন মুখ্য যে কারণ রয়েছে সেটি হলো, পূর্ববঙ্গের পরিবর্তনকে সম্যক উপলব্ধি করতে না পারা। নীরদবাবু যে পূর্ববঙ্গকে পেছনে ফেলে কলকাতাবাসী এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডবাসী হয়েছেন, সেই পূর্ববঙ্গ ততদিনে আমূল পাল্টে গেছে। এবং এই পরিবর্তন এতটাই নাটকীয় ও গতিশীল ছিল যে, সে একটি স্বাধীন দেশ হয়ে ওঠার সক্ষমতাও অর্জন করেছে, প্রবন্ধ প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যেই সে স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়েছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, পূর্ববঙ্গ পঞ্চাশ বছরব্যাপী একটা নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। এই নবজাগরণ পূর্ববঙ্গবাসীকে এমনভাবে সংঘটিত করেছে যে যুদ্ধের মাঠে সে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান একটা রাষ্ট্রকে পরাজিত করার সামর্থ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত সামরিক শক্তির সঙ্গে সামাজিক শক্তির লড়াই। সেই লড়াই বাংলাদেশ বাস্তবিকই বিশ্বমাঝে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যদিও তার পাশে ভারত সকল প্রকার সহায়তা দিয়ে শক্তভাবে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মূলত পূর্ববঙ্গের সামাজিক শক্তিরই বিজয়। যে শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন। যে শক্তির প্রকাশ দেখা গেছে, ১৯৫২-এর একুশে, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে [শেষের দুটি ঘটনা অবশ্য এই প্রবন্ধ লেখার পরে সংঘটিত হয়েছে]।
যে প্রেক্ষাপটে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধটি লেখেন, তার পরিপ্রেক্ষিত জানাটা জরুরি। মূল কারণ ছিল পাক-ভারত যুদ্ধ। যা সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে। তাসখন্দ চুক্তির মধ্যে দিয়ে ওই যুদ্ধের অবসান ঘটে। স্পষ্ট হয় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার অসহায় ও শোচনীয় অবস্থা। যার নেপথ্যে ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্য। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন এসবের বিরুদ্ধে। ঠিক এই সময়ই তাসখন্দ চুক্তি পরবর্তী পাকিস্তানের রাজনীতির গতিধারা নির্ণয়ের জন্য দেশটির বিরোধীদলীয় নেতারা ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। শেখ মুজিব দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছান। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে পরদিন সাবজেক্ট কমিটির সভায় ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন এবং সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরদিন পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় ছয় দফা দাবি নিয়ে খবর প্রকাশিত হয় এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার অভিযোগ ওঠানো হয়।
১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিতপাক-ভারত যুদ্ধের নেপথ্যের কারণ ছিল তিনটি। এগুলো হলো—
এক. কুচের রান অঞ্চলে এপ্রিল মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষামূলক যুদ্ধ।
দুই. আগস্টে ছদ্মবেশে পাকিস্তানিদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের ঘটনা।
তিন. সেপ্টেম্বরে দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমণ।
এই যুদ্ধ কেবল এক বছরের মধ্যে দৃশ্যমান হলেও দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস, বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব ১৯৪৮ সালে থেকেই চলমান ছিল। যার প্রকাশ ঘটে ১৯৬৫-তে এসে।
পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধে স্বাক্ষরিত তাসখন্দ চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের বৈরিতাকে কিছুটা লঘু করতে সমর্থ হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কাছে পাক-ভারত যুদ্ধ উন্মোচন করে দেয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান।
পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানে ১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতিসংঘের সরাসরি হস্তক্ষেপে যুদ্ধ থেকে সরে আসে দুই দেশ। চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেন আলেক্সি কোসিগিন। এর শর্তগুলো হলো—
এক. ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যাবে।
দুই. কেউই অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।
তিন. যুদ্ধবন্দীদের সুশৃঙ্খলভাবে স্থানান্তর করা হবে।
চার. দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি সাধনে কাজ করবে।
পাঁচ. দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হবে।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী সোয়াশত বর্ষ পূর্ণ হলো এ বছর, জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর। বাঙালি মনীষায় তিনি শ্রদ্ধা জাগানিয়া এক প্রতিভা। তাঁর পূর্ববঙ্গের সমস্যা বিচার নানানকারণেই বাংলাদেশের জন্য ফিরে দেখা জরুরি। বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষায় এই প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। উনার বয়ান-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ও সেই সময়ের ঘটনাসমূহের গতি-প্রকৃতি বুঝতে এই প্রবন্ধ স্বচ্ছ এক আয়নারূপে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। ১৯৬৫ এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৬-র ছয়দফা দাবির ঘটনাসমূহ কীভাবে স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তর করল। পূর্ববঙ্গের মানুষেরাই-বা কীভাবে এসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল, তার বৌদ্ধিক বাস্তবতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ নীরদবাবুর ‘পূর্ববঙ্গের সমস্যা’ প্রবন্ধ। যা একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর চারিত্র্য কাঠামোয় প্রাধান্য পেয়েছে সময় নিরপেক্ষ এক সত্য। যা পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের জন্যই বিশেষ শ্লাঘার। এই প্রবন্ধের তরফে যেখানে প্রশ্ন হাজির হয়, সেখানে আমরা যেন এই জনপদের অন্য এক সত্তা ও স্বতন্ত্র রূপকে আবিষ্কার করি। যা ইতিহাসকে যেমন নতুন তাৎপর্য দেয়, তেমনি সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে চেনায় এবং ঢাকার নবজাগরণকে উন্মোচন করে। নীরদবাবুর ইতিহাস নির্মাণ ও গতি সঞ্চরণের শক্তি এখানেই, যা দিশা দেয় বাংলাদেশকে তার সত্তার অন্বেষায়। যেমনটা বলেছেন তিনি, হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রার মূলগত প্রভেদ আছে। সে-প্রভেদ এত বড় ও এত প্রাচীন যে, দুই পক্ষের মিলন বা সমন্বয়ের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রকৃতি ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে, ‘পৃথক করেছি যারে আমার বলে, তোমরা ফিরাবে তারে কিসের ছলে?’
তার মানে স্বাধীন বাংলাদেশ তার প্রকৃতির চাওয়া। বাংলার জল হাওয়া কারও অধীনতা মানে না, মানুষও মানবে না, এটাই স্বাভাবিক-সংগত এবং প্রকৃতিরও সত্য। যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। আমাদের স্বাধীনতার অনিবার্য বাস্তবতা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনেরও পাঁচ বছর আগে এরকম সুলুকসন্ধানী কথা নীরদচন্দ্র চৌধুরী ছাড়া আর কেউ উচ্চারণ করেছেন কি? নিশ্চয় না।








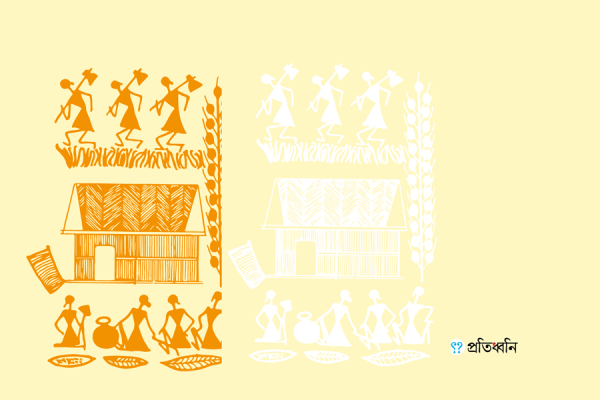
আপনার মন্তব্য প্রদান করুন