হুমায়ূন আহমেদ কি উপযোগিতা হারাবেন?
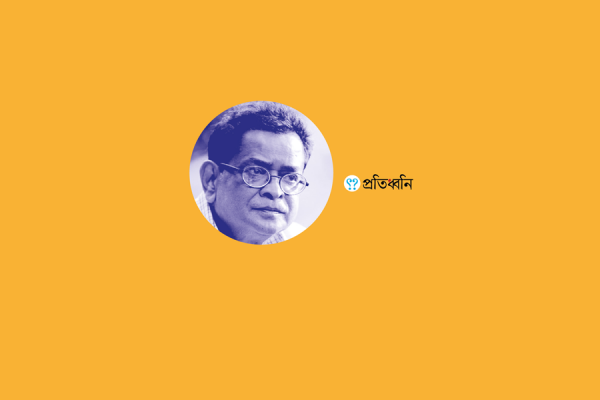
তখন স্কুল পালানো বয়স। মাঝে মাঝে বড় বোনের বইয়ের তাক থেকে নিয়ে নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘কিরীটী সিরিজ’ পড়ছি। গোয়েন্দা কাহিনী ভালবেসে ফেলবার কারণে সেবা প্রকাশনীর দ্বারস্ত হতে হচ্ছে বেশ কিছুদিন; এর মধ্যে আবার জাফর ইকবাল, রাহাত খান, চার্লস ডিকেন্স পড়া শুরু করেছি। বই পড়ার প্রতি ঝোঁক দেখে বড় দুই বোনের সাজেশন অনুযায়ী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, এমনকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই নিয়ে বিপুল তর্কে জড়িয়ে, মাঝে মাঝে চুরি করে করে তাঁদেরই সাজেশনের বইগুলোর কিছু পাতা উল্টেপাল্টে দেখছি। এর মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামের সুমতি পড়েও ফেলছি। বিষম দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে লুকিয়ে কেঁদে কাউকে জানাতে পারিনি—এডভেঞ্চার প্রিয়, বাড়ন্ত পুরুষ ইগো পাছে আঘাত পায়! কিন্তু এত প্রাঞ্জল, মায়াময়, সহজ গদ্য—আমার পাঠাভ্যাসের বাইরের গদ্য আর এমন কিছু তখনো পড়া না থাকায় বইটা ভীষণভাবে দাগ কাটে। বিশেষ করে সেই সব ব্যক্তিগত দুঃখ গাঁথা, যা আমার কিশোর মনকে নাড়া দিয়ে নিজের বলে ভাবিয়েছিল। যদিও তার আগে অন্য অনেক মুসলিম সন্তানের মতো, আমারও মায়ের মুখে মীর মশাররফ হোসেনের বিয়োগাত্মক কারবালার কাহিনী নির্ভর ‘বিষাদ সিন্ধু’ শোনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সচেতনভাবে তখনো জানতে বা বুঝতে পারিনি যে সে সবই ছিল সাহিত্যের অন্তর্গত। জানলে হয়তো বই পাঠের অভ্যাস বা সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক তৈরি হতো কিনা সন্দেহ—তবে গল্পের প্রতি প্রবল ঝোঁক তৈরি হয়েছিল বেশ আগের থেকে।
তখন খেলতে পারলে বেঁচে যাই, ডাকটিকেট জমাই, গ্রীষ্মের শেষভাগে আকাশ পরিষ্কার হয়ে সাদা মেঘের ভেলা ভাসলেই সূতায় মাঞ্জা দেই আর প্রায়শই বিবিধ টিকার ভয়ের উসিলায় স্কুল পালাই। শহরের চৌহদ্দি তখনো বাসা আর স্কুলের নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর থাকায় কোর্ট বিল্ডিঙের চত্বরে বানর খেলা, সাপ খেলা, ম্যাজিক অসাধারণ লাগতো। কামরূপ কামাক্ষ্যার গল্প আর তার মায়ার কথা শুনতে শুনতে ম্যাজিশিয়ানের হাত-সাফাই, তাসের খেলা, ব্লেড বা ছুরি খেয়ে ফেলা, টুপির ভেতর থেকে বের করে আনা অদ্ভুত সব জিনিসের মায়ায়—মোহজালে আটকা পড়ে যাই যতক্ষণ না সে যাদু শেষে তাঁর মলমের বাক্স বের করে। মলম কিনতে না পারার অক্ষমতায় আমাদের পালিয়ে আসতে হলেও ফের আমরা সুযোগ পেলেই সেই সব যাদুটোনার খেলায়, বশীকরণ মন্ত্রে মুগ্ধ হতে শিখতে কোর্ট চত্বর বা রেল ইস্টিশনে খুঁজে খুঁজে সেই সব খেলোয়াড় বা যাদুকরকে বের করে ফেলতাম যারা তাঁদের খেলা, বাচন আর যাদুর বিস্তারে আমাকে, আমার মতো অনেককেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।
ঐ সময়, গত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথম ভাগে কেমন করে ঠিক মনে করতে না পারলেও এত সব ইন্ডিয়ান লেখকের মাঝে বোনদের ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা পাতলা বই চোখ টেনে নিয়েছিল। লেখকের নামটা অপরিচিত, কিন্তু বইয়ের প্রচ্ছদটা ছিল তখন পর্যন্ত আমার দেখা অন্য দশটা বই থেকে বেশ ব্যতিক্রম এবং আকর্ষণীয়। তো পড়তে শুরু করতেই গল্পের ভেতর ঢুকে গেলাম, যেন আমিও সেই গল্পের একজন পাত্র, আমাদের সংসারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাই যেন এই বইয়ের পরতে পরতে বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত দুপুর বুঁদ হয়ে সন্ধ্যায় বুকের ভেতর হাহাকার জাগানো শূন্যতা নিয়ে সবকিছুকে তুচ্ছ বলে মনে হতে শুরু হয়েছিল। পরে লেখকের ভাষ্যেই জানতে পারি, এই বয়সে নাকি এমনই হয়, এটা আবেগাক্রান্তের বয়স; যে আবেগে যুক্তি-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। আমার কেন, আমাদের সময়ের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের দেখেছি হুমায়ূন আহমেদের লেখার কি অসম্ভব ভক্ত একেকজন। তাঁদের থেকে ব্যতিক্রম হবার কোন প্রয়োজনীয়তা, তাগিদ ছাড়াই আমি, আমরা অনেকেই গোগ্রাসে তাঁর লেখা পড়ে যেতে থাকলাম বললে ভুল বলা হবে, গিলতে থাকলাম। আমাদের ভেতর মায়া জেগে উঠল, আমরা তাঁর অন্ধ অনুসারীর মতো অপ্রাপ্ত বয়সী কিশোরীদের ভালোবাসতে শুরু করলাম, আমরা দুঃখকে নিজের করে চিনলাম প্রতিবেশীর বাড়িতে উঁকি দিয়ে, আমরা সুডো লজিককে যুক্তিবিদ্যা ভেবে রপ্ত করলাম ইলজিক্যাল জেনেও, মশার কামড়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হতে হতে জ্যোৎস্নার ম্রিয়মাণ আলোয় ঘর ছাড়া হলাম আর জ্যোৎস্নার সেই দু’কুল ছাপানো আলোকে মায়া মনে করে, ভেবে নিয়েছিলাম এই মায়াময়তার জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোন পৃথিবীতে!
আমাদের গোগ্রাসে গিলবার মতো তখন খুব বেশি আনন্দ উপকরণ ছিল না। মফস্বল শহরের কিশোর, তরুণ, যুবার যেমন থাকে আরকি; যারা একটু আধটু বই পড়তাম তারা হয় সেবা প্রকাশনীর কিশোর ক্লাসিক, কিশোর থ্রিলার, রহস্য পত্রিকা, শিশু পত্রিকা, যারা তরুণ-যুবা তারা ওয়েস্টার্ন, মাসুদ রানা, ইমদাদুল হক মিলন, তসলিমা নাসরিন, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি থেকে নিজের মতো রসদ কুড়িয়ে নিতাম। যদিও হুমায়ূন আহমেদের কারণে ভারতীয় বাংলা লেখকদের বই বেশ চাপের ভেতর পড়তে শুরু করেছিল সেই সময়ে। আমাদের দেশের বিনোদনের একমাত্র, প্রধানতম মাধ্যম তখন টিভি। সেই বিটিভিতে তখন হুমায়ূন আহমেদের ‘এইসব দিনরাত্রি’ দেখানো শুরু হয়েছে মাত্র। বাসার সবাই মিলে তো বটেই পাড়া-প্রতিবেশী মিলেমিশে রীতিমতো আয়োজন করে সেই নাটক দেখতে বসাটা সব বয়সীর জন্য এক অতীব জরুরী, এমনকি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঈদের দিনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তাঁর নাটক—যেন তাঁর নাটক ছাড়া ঈদ অপূর্ণ থেকে যাবে। আর আমাদের মা-বোনেরা তো আগের থেকেই তাঁর মায়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় বুঁদ হয়েছিলেন। এবার পত্রিকায়, টিভিতে তাঁর নাটক দেখে, সাক্ষাৎকার, গল্প পড়ে বাবার বয়সীদেরও সাজেশন হয়ে উঠলো, পড়তে হয় হুমায়ূন পড়। শরৎচন্দ্রের পর একমাত্র তিনিই পাঠযোগ্য বলে বিবেচিত হতে লাগলেন—এমনই ছিল সেই পিআর প্রেশার। দলে দলে বাড়তে লাগলো তাঁর অন্ধ-ভক্তকুল। যার জন্য এমনকি বন্ধু বন্ধুতে মারামারি হতেও আমরা সাক্ষী হয়েছি, একজন হয়তো সারাজীবন আরেকজনের মুখ দর্শন করেনি এমনও ঘটনা ঘটেছে। তিনি গল্পের মায়াজালে আটকে ফেলে যেন হয়ে উঠলেন আমাদের সময়ের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা আর আমরা তাঁর মোহাচ্ছন্ন ইঁদুর!
তাঁর ঈর্ষনীয় সহজ গদ্যে, এমন ভাবে, একই ভঙ্গিতে, একই দুঃখগাঁথা বা হিউমারের অবতারণা আমাদের এমন বুঁদ করে রেখেছিল যে আমরা ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টকে তার সাথে মিলিয়ে সেল্ফলেস হয়ে উঠছিলাম। আমাদের ভোঁতা যুক্তিবোধ কোনভাবে বুঝে উঠতে পারছিল না এই নতুন নভেলার সাথে আগের পড়া নভেলার পাত্রপাত্রীর নামের ভিন্নতা আর ঘটনা প্রবাহের ভিন্নতা ছাড়া মৌলিক পার্থক্যটা কি? কেন আমি ভোক্তা হবো একই ধরনের আরেকটি কাহিনীর? সময় তখনো আমাদের কাছে মূল্যহীন—যদিও আমি এখনো শিওর না, এখনো তার মূল্য বুঝতে শিখেছি কিনা। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের বাংলাভাষার সেই লেখক যার জন্য এখনো তরুণরা বিশেষ দিনে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমু হয় আর মেয়েরা শাড়ি পরে রূপা। তিনিই আমাদের দেশের প্রথম লেখক যার কারণে প্রতিটা মধ্যবিত্তের বাড়িতে একাডেমিক বইয়ের বাইরে তিনটা বই থাকলে তার একটা বই অবধারিতভাবে হুমায়ূন আহমেদের হবেই। তিনি বই পড়াটাকেও একটা লাইফ স্টাইল করে তুলেছিলেন। তবে সেটার ভেতর একধরনের মুমিনীয় ব্যাপার ছিল, এক লেখকের বই পড়ার মতো ক্যাভটিভিটি ছিল। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কাছে তিনি শুধু মাত্র একজন লেখক না, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন যার বিশাল কর্মকাণ্ড নিয়ে, যার উপন্যাস ধরনের বইয়ের ভাণ্ডার নিয়ে বলতে গেলে এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব হয়ে উঠবে বলে সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি। এখানে আমি শুধু তাঁর লিখিত গল্প নিয়ে কথা বলবো, সেখানেও যে সব গল্পের স্থান দিতে পারবো, তা মনে করি না। আমি তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ গল্প এবং গল্পের প্রবণতা, লক্ষণ ও আমাদের প্রাপ্তির ভেতর আলোচনা সীমিত রাখবার চেষ্টা করবো।
কেন হুমায়ূন আহমেদের শুধু মাত্র গল্প নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী তা পাঠকের কাছে প্রকাশ না করলে ভুল বুঝবার অবকাশ থেকে যাবে। মানুষের মাঝে একটি ভক্তি সংক্রান্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, কারো ভক্ত হলে অন্য সবকিছুকে বা অন্য কারোকে বিবেচনায় না রেখে শুধুমাত্র তার গুণগান করতে অন্যকে হয় নস্যাৎ করি অথবা বিচারের আবশ্যিকতাই বোধ করি না। তো হুমায়ূন আহমেদ তার বিপুল রচনার ভেতর কিছু ভালো রচনাও আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা একটি প্রচলিত কথা শুনতে পেলাম—হুমায়ূন আহমেদ বাঁচলে মিসির আলী, হিমুকে নিয়ে লেখা নভেলা এবং ছোটগল্পে বেঁচে থাকবেন! সাহিত্যে কোন লেখক প্রাসঙ্গিক থাকবেন কি না থাকবেন তার ভেতরই যেহেতু লেখকের বেঁচে থাকা নির্ভর করে, তাই আমি সেই তর্কে না জড়িয়ে মহাকালের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র তার সম্ভাবনাময় এবং আমার ভালো লাগা গল্পগুলকেই বেছে নিচ্ছি আলোচনার বিষয় হিসাবে।
‘ফেরা’ গল্পটাকে আমার বেছে নেবার কারণটা যদিও একটু ভিন্ন—এই গল্পে আমি হুমায়ূনীয় ‘ল’ বা সিগনেচার এবং ক্রমাগত একই বিষয়ের চর্বিত-চর্বণ যে উনি বাণিজ্যিক কারণে করে গেছেন, তাঁর অন্ধ পাঠককুলকে ঠকিয়েছেন তার ডেমো দেবার জন্য বেছে নিয়েছি। হুমায়ুন আহমেদের এমন অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস আছে, এমনকি এই গল্পগুলিতে সচেতন পাঠকমাত্র তাঁর বিপুল জনপ্রিয় নভেলা ‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর প্রচ্ছন্ন ছায়া খুঁজে পাবেন। হুমায়ূন আহমেদ বোধকরি তাঁর জনপ্রিয়তার নিরাপদ গণ্ডির লক্ষণরেখা ছেড়ে বের হতে কখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি অথবা লেখক যে নিজস্ব নন্দনের সৃষ্টি করেন তেমন কোন নন্দনতত্ত্বের ঘেরাটোপে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সব সময়। ‘ফেরা’ গল্পটা উল্লেখিত উপন্যাসদ্বয়ের মতো একটি শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ সদস্যকে ঘিরে আবর্ত হয়েছে। জরি সবার বড় মেয়ে, সে ক্লাস নাইনে পড়ে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের মুড সুইং তার মধ্যে বিদ্যমান। অবুঝ, অভিমানী, জেদি সে। বাবা-মার অক্ষমতা এমনকি ভাই-বোনের চাহিদার প্রতিও তার তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—সে নিজের চাহিদা পূরণেই বেশি সচেষ্ট। যদিও সেই চাহিদাও খুব সামান্য। পরী পরিবারের দ্বিতীয় মেয়ে, সে কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগে কাহিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। জ্বরের কারণে তার মুখে অরুচি আছে তাই সে বারবার ভাত খাবার আকুতি জানায় মায়ের কাছে। আর সবার ছোট ছেলে দীপু সামান্যতেই তৃপ্ত, মা বা বাবা যা-ই বলেন বা তাকে দিয়ে থাকে তাতেই সে খুশি। হুমায়ূনীয় ‘ল’ অনুযায়ী শাশ্বত বাঙালি মা তার রচনায় যেমন হন; অসহায়, উপায়হীন এই জীবন আর সংসার টানতে টানতে, বাচ্চাদের আবদার মিটাতে না পেরে দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে মায়ার এক সংসারে বেহাল অবস্থায় বেঁচে আছেন, না-বাঁচার অপশনও নেই—এমনই গুরুত্বহীন। বাবার ভূমিকা এই গল্পে সব থেকে সামান্য কিন্তু, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ঘরে ফেরা নিয়েই গল্পের নাম ‘ফেরা’। একটি সংসার পূর্ণ হবার খুব সাধারন একটি গল্প, রাতের খাবারে ভালো কিছু না থাকবার; এমন কি ডিমও না থাকবার মতো মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক দিনের ঘটনা নিয়ে মেয়ে জরির অভিমান আর জেদ দিয়ে গল্পের শুরু। মায়ের অসহায়ত্ব দিনে দিনে তাকে নিঃস্পৃহ করে তুললেও তিনি ছেলেমেয়েদের প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করেন এবং যথারীতি হুমায়ূন আহমেদের সব থেকে সেলেবেল প্রোডাক্ট, মায়া বোধ করেন। বড় মেয়ে জরি বাদে সবার রাতের খাওয়া শেষ হবার পর মায়ের অপেক্ষা বাবার ঘরে ফেরার। ইতিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে বাবা বাসায় ফিরে একটা হুলস্থুল শুরু করে দেন। বেতন ৪০ টাকা বৃদ্ধির উপলক্ষে তিনি একটা বড় রুই মাছ কিনে আনেন এবং যার কারণে পরিবারের সবার ভেতর উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। সবাই এমনকি অসুস্থ পরীও এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে উঠানে বসে মায়ের রান্না করা গরম ভাত আর রুই মাছ ভাজি খেতে বসে যায়। যদিও এই উল্লেখ পাওয়া যায় না, তাদের বাসার উঠান কোন ধরনের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত কিনা বা ততক্ষণে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়ে উঠানটা তাদের বসার উপযোগী হয়ে উঠেছে কিনা! মা হাসিনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গল্প শেষ হয় এমন করে, খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে অকারণ আনন্দে হাসাহাসি করছে, ‘বাসন-কোসন রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বিষ্টিভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।’ এবং পাঠক হিসাবে আমরা একটি সামান্য রাতের আনন্দ-বেদনার গল্পের অসামান্য হবার সম্ভাবনার মৃত্যু দেখে ব্যথিত হয়ে উঠি, যদিও তার এমন গল্পের সংখ্যা অসংখ্য। আমার ভালো লেগেছে মা হাসিনার ভাই রঞ্জুর বিশাল একটি মাছ আনার ঘটনাকে চাপা দিতে মায়ের বলা তার স্বামীর কিনে আনা তারও থেকে লম্বায় বড় একটি চিতল মাছের উল্লেখ। লেখক মায়ের অসহায়ত্ব বোঝাতে নাকি স্বামীকে যোগ্য এবং সক্ষম হিসাবে ছেলেমেয়ের কাছে উপস্থাপন করতে বিষয়টির অবতারণা করেন সেটা যদিও পরিস্কার হয় না।
হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নিজস্বতা তৈরি করতে যেমন কিছু নিজস্ব আবেগীয় ‘ল’ বানিয়েছেন তেমন এমন কিছু শব্দ, বাক্য বা জারগন তৈরি করেছেন যা তাঁর গল্প-উপন্যাসে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা অনেকটা আয়াতের শেষে ঈশ্বরের বন্দনার মতো, প্রয়োজন নেই তবু যুক্ত করা হয়েছে। যেমন—‘যে গভীর ভালবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি’, ‘জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। এ জগত বড় রহস্যময়’, ‘এর জন্ম অদেখা এক ভূবনে’, ‘আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা’, ‘আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না’, ‘নেচার বা ঈশ্বর বা প্রকৃতি—এরা কোন রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না’ ইত্যাদি। এসব বাক্য বা শব্দ পুনঃপুনঃ ব্যবহার করে তিনি যেন তাঁর বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন তৈরি করেন। আপনার যত বিরক্ত লাগুক না কেন এই ট্রেডমার্ক বা সিগনেচার তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করতেন। আরেকটি বিষয় হুমায়ূন খুব সচেতনভাবে করেছেন তাঁর সমস্ত লেখায়। সেটি হলো তাঁর নাটক, উপন্যাস, গল্পের সব পাত্রপাত্রীর প্রায় একই নাম বা একই আর্কেটাইপ সেই সব ক্যারেক্টারের। যার জন্য এক ধরনের ঘোর বা ধন্দ তৈরি হয় পাঠকের মাঝে। আমাদের মাঝে প্রশ্ন জাগতেই পারে হুমায়ূন কি তাঁর সব গল্প, উপন্যাস, নাটককে বা সব পটভূমিকে একটা গল্প বলতে বা ভাবাতে চেয়েছেন? হুমায়ূন গবেষকেরা এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন কিনা জানি না তবে, বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে।
হুমায়ূন আহমেদের অনেক গল্পের ভেতর ‘শিকার’ গল্পটা বেশ ব্যতিক্রম এবং তাঁর এমন আরো কিছু ব্যতিক্রম গল্প আছে, যা পড়ে বিস্ময় জাগে। আমাদের চেনা পরিচিত হুমায়ূনকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না যেন! খানিকটা ধন্দে পড়তে হয়, এটা কি আসলেই হুমায়ূনের গল্প! কার্তিকের সকালে ঘোর লাগা এক বর্ণনা পাওয়া যায় ‘শিকার’ গল্পের শুরুতে। সূর্যের নরম রোদ গায়ে মাখতে মাখতে আমরা দুই বক শিকারির কথোপকথন থেকে জেনে নেই বক ধরার সব থেকে নির্মম পরিণতি। একজন লেখককে প্রতিনিয়ত নিজের সাথে, পারিপার্শ্বিকের সাথে, সমাজ-সংসারের সাথে নিরন্তর বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তিনি কি লিখবেন, কি লিখবেন না, তার বিষয় কি হবে, কি হবে না। আমি অনেকবার বুঝতে চেষ্টা করেছি, তিনি এমন একটি গল্প লিখতে গেলেন কেন? কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, হুমায়ুন হয় নিজেই তাঁর প্রতিনিয়ত লেখার বিষয় দুঃখগাঁথার মনোটনিতে ভুগতে শুরু করেছিলেন অথবা তিনি নিজেই পাঠককে চমকে দিতে চেয়েছেন নতুন বিষয়কে গল্পের পটভূমি করে; হুমায়ুন যেন নিজেকে ছাপিয়ে যেতেই এমন এক পেশার বা জনগোষ্ঠীর গল্প ফেঁদেছেন যা আমাদের অজানা এবং নিজের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিয়তিবাদীদের মতো অমোঘ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এই গল্পে। বক শিকারীদের নির্মম পরিণতি এবং এই ভয়ঙ্কর পেশা যে তাদের নেশার মতো টেনে নিয়ে যায় জলাভূমিতে এবং নিয়তির অবধারিত নিয়মে যেন তারা সবাই অন্ধ হয়ে যেতে থাকে, অন্ধ তাদের হতেই হয় এমন কথা বলে গল্পের শুরুতেই বৃদ্ধ অন্ধ বক শিকারী মতি মিয়া তার এবং ‘নেজামের ভাইস্তা’ নামের আরেকজনের পরিণতির কথা মনে করিয়ে আজরফকে সাবধান করে। আজরফ এ সবের সবই জানে, তবু নেশার অদৃশ্য কোন এক টানে সে উত্তরবন্দের নাবালের জলাভূমির দিকে ছুটে যায় তার পোষা বক অনুফাকে নিয়ে, যার করুণ ডাকে উড়ে যাওয়া বক পাখির দল সাহায্যের জন্য নেমে আসে আর সেই সুযোগে আজরফ হাত দিয়ে হেঁচকা টানে বকের পা ধরে টেনে নামিয়ে পা দিয়ে পাড়িয়ে ধরে, আবারো হাত বাড়ায় আরেকটি বককে ধরতে। এই অংশে লেখক ধরবার প্রক্রিয়াটা বর্ণনার প্রয়াস করলেও ঠিক পরিষ্কার হয় না তা। কারণ বেতের পাতা দিয়ে বানানো চাটাইকে বুনো ঝোপ বলে ক্ষীণ দৃষ্টির বক ভুল করলেও মতি বা বক শিকারী কোথায় থাকবে, কেমন করে সে বকের পা ধরে টেনে নামাবে, সেটা কল্পনা করাটা বেশ দুরূহ হয়ে পড়ে পাঠকের জন্য। আমরা আজরফের ফাঁদ পেতে বসে থাকার সময় হুমায়ূনীয় বেশ কিছু অর্থহীন দার্শনিক প্রশ্ন আজরফের ভাবনার ভেতর দিয়ে পাঠকের সামনে প্রকাশিত হতে দেখি, সচারাচার যেমনটা তিনি সব লেখাতেই করে থাকেন—যেটাকে তিনি নিজের সিগনেচার বানিয়ে ফেলেছিলেন—যার কোন উত্তর হয় না, কোন উত্তর মেলে না এমন সব অর্থহীন পর্যবেক্ষণের দার্শনিক প্রশ্নে। যেমন, ‘শূন্য নীল আকাশের মত অদ্ভুত আর কিছু আছে নাকি?’, ‘বন্দী জীবনেরও একটা মায়া আছে’, ‘এ জগত বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় চোখ কাঁদে। কেন কাঁদে?’। এই প্রশ্নের আগেই আমরা জানতে পারি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী—‘চউখের নিজের একটা জীবন আছে’ সে আগের থেকে বুঝতে পারে, তাই যে চোখটা বকের ধারালো ঠোঁটের ঠোকরে নষ্ট হবে সেটা থেকে আগেই জল পড়তে থাকে, মানে কান্না শুরু করে।
গল্পটা যে একজন বক শিকারীর চোখ নষ্ট হওয়া নিয়ে সেটা পাঠক গল্পের প্রথমেই মতি মিয়ার সাবধান বাণী থেকেই বুঝে নিতে পারবেন এবং যতোই গল্পের ভেতরে পাঠক ঢুকতে থাকবেন ততোই বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক গল্পের রেফারেন্সের ভেতর দিয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, আজরফের বা চোখটা আজ নষ্ট হতে চলেছে। গল্পটা একজন শিকারীর নিস্তরঙ্গ, কিন্তু নির্মম চোখ নষ্ট হবার কাহিনীর দিকে এগিয়ে যায়। পাঠক আরেকটি নির্মমতার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ, আজরফের বা চোখ কাঁদছে। ঠিক তখন আজরফ তার চোখ বাঁচাতেই যেন দ্বিতীয়বারের মতো সিদ্ধান্ত নেয় সে আর পাখি শিকার করবে না। সে তার পোষা বক অনুফাকে মুক্ত করে দেয়। সে বকটিকে তাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু অনুফা যায় না। আজরফ অনুফাকে তার কল্পনায় থাকা চোখ খুঁজে নেওয়া বকটির মত ঋজু, স্বাস্থ্যবান, ধবধবে সাদা পালকের অতিকায় বকের মত দেখতে শুরু করে। আকাশে তখন চক্রাকারে বক নেমে আসছে তাদের মাথার ওপর থেকে। আজরফ প্রতিরোধের কথা চিন্তা করে। পোষা পাখিটি অতিকায় আকার ধারণ করতে শুরু করে। এমন সময় আমাদের চেনা হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সিগ্নেচার মার্ক ঢুকিয়ে দেন—‘এর জন্ম অদেখা এক ভূবনে’ এবং বকগুলো নেমে আসতে থাকে। পাঠককে সাসপেন্সে রাখতে লেখক এখানেই গল্পের ইতি টানেন। শিকার গল্পের বিষয় হিসাবে হুমায়ূন আহমেদ আমাদেরকে একটি দার্শনিক সিঙ্গেল লাইন ম্যাসেজ দেন—শিকারী নিজেও কোন না কোন সময়ে শিকার হন। তাঁর মতো করে বললে, ‘এ জগতে সবাই শিকার, সবাই শিকারী’।
হুমায়ূন বরাবরই উত্তম পুরুষে গল্প বলতে পছন্দ করেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পই উত্তম পুরুষে লেখা। এর দুটো কারণ থাকতে পারে, প্রথমত তিনি প্রথমে ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং জনপ্রিয় হন। পরবর্তীকালে তিনি যখন গল্প লেখা শুরু করেন তখন তিনি এক ধরনের দ্বিধায় পড়েন তাঁর গল্পের মান নিয়ে, তাই তিনি জনপ্রিয় লেখকের [নিজের] ব্যক্তি ইমেজকে ব্যবহার করে সেই গল্পগুলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। আর দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায়, তাঁর বেশিরভাগ গল্প যেহেতু ডায়লগ নির্ভর, তাই উত্তম পুরুষে সহজভাবে তিনি কাহিনী বিস্তার করতে পারেন এবং পাঠককে তিনি গল্পের ভেতর ইনভল্ভ করতে চান শুনবার এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে, যেন পাঠক নিজে গল্পটার একটা অংশ হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত ধারণাটির পক্ষে প্রচুর পাঠক দেখতে পাওয়া যায়। উত্তম পুরুষে লেখা তাঁর বেশিরভাগ গল্প নিতান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ, অতৃপ্তি, শূন্যতা, মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্য সুখের-আনন্দের অসাধারণ উদযাপন। এর ব্যতিক্রম যে একদম পাওয়া যায় না তা না, তাঁর সব থেকে আলোচিত এবং বিখ্যাত গল্প ‘খাদক’ যেমন তাঁর চর্চিত বিষয়সমূহের বাইরে একটি সফল গল্প হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।
গল্পটার সব থেকে বড় গুণ খুব সহজ এবং নিতান্ত সাধারনভাবে বয়ানের পরিমিতি বোধ, গল্পের বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে লেখকের অজপাড়াগাঁয়ে আটকে পড়া এবং বাধ্য হয়ে রুচির বাইরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনাকে বয়ানের মাধ্যমে গল্প এগিয়ে যায়। লেখকের দূরসম্পর্কের আত্মীয় খোন্দকার সাহেব তাকে আপ্যায়নের জন্য এবং এলাকাবাসীর কাছে নিজের পজিশন বুঝাতে গ্রামের সব থেকে বিস্ময়কর ব্যক্তিটিকে উপস্থাপন করে লেখকের বিনোদনের জন্য। মতি খাদক যে শুধুমাত্র তার অতিকায় খাবার গুণের কারণে গ্রামের নামই শুধু উজ্জ্বল করেনি, নিজেও বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে মেডেল, টাকা, বিবিধ পুরষ্কার জিতে এনেছে। সে তার এই বিপুল খাবার খাওয়ার গুণকে নিজের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে—আর কিছুই সে করে না, এই ভীতিকর খাবার গুণ থেকে যে উপার্জন হয় তাই দিয়েই তার সংসার চলে এবং লেখকের সাথে তার কথোপকথনের সুবাদে আমরা জানতে পারি, সে এই জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত তার এই বিদ্যা নিয়ে বেশ অহংকারও বোধ করে। তাকদির এবং রিজিকের ওপর ভিত্তি করে যেভাবে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তার অবস্থান এবং উপায়হীন পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে জীবন-যাপন করেন, খাদক মতি মিয়াও তার ব্যতিক্রম নন। খোন্দকার সাহেব লেখককে চমৎকৃত করতে এবং তার নিজের ও গ্রামের সুখ্যাতি পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে দিতে মতির জন্য একটা আস্ত গরু খাবার আয়োজন করে। রাত জেগে খাবার আয়োজনে দূরদূরান্ত থেকে সম্মানীয় মানুষ, গ্রামবাসী তা চাক্ষুষ করতে উপস্থিত হন। তাদের সাথে সাথে উপস্থিত হয় মতির হাড় জিরজিরে, না খেতে পাওয়া রুগ্ন সন্তানেরা। তারা শুধু দুচোখ ভরা ক্ষুধা নিয়ে তার বাবার কুৎসিত খাওয়া দেখতে থাকে।
লেখক গল্পের ভেতর বেশ কয়েকবার এরশাদের কথা উল্লেখ করে কি পাঠককে কোন ইশারা দেবার চেষ্টা করেন? হুমায়ূন আহমেদ ‘নিজের আনন্দের জন্য লেখেন’ বলে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেখান থেকে তিনি কি সচেতনভাবে সরে এসে একধরনের রাজনৈতিক পজিশন নিতে চাইছেন এই গল্পে? অবশ্য আমরা পরবর্তী বেশ কিছু গল্পে তাঁর এই রাজনৈতিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখতে পাব। এরশাদের লজ্জাহীনভাবে সম্পদ লুটপাট, দেশের সাধারন নিরন্ন, দুস্থ মানুষের তোয়াক্কা না করে গদিতে টিকে থাকার প্রবণতা কি মতির আত্মকেন্দ্রিক, কুৎসিত, ন্যায়-নীতিহীন বেশি খাবার উল্লাসকে লেখক রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন? হুমায়ুন আহমেদ রাজনৈতিক এবং রূপকধর্মী লেখা সাধারণত লেখেননি বলেই আমাদের ধন্দে থাকতে হয়। লেখার শেষভাগে হুমায়ূন তাঁর উইশফুল সমাপ্তির প্রবণতাকে বাদ দিয়ে পাঠকের মানবিক বোধকে জাগিয়ে তুলে তার ভেতর অতৃপ্তি সৃষ্টি করেন, তাকে এক ধরনের অস্বস্তির মুখোমুখি দাড় করান এভাবে, ‘মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে—কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।
মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে—হারলে হারব।
আমি জানি বাস্তবে তা হবে না… মতি খাওয়া শেষ করবে। কোন দিক ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না। তিনি যেন লিখছেন, এত কিছু দেখলে সরকার হয়ে গদিতে থাকা যায় না!
‘মন্ত্রীর হেলিকপ্টার’ গল্পেও আমরা আরো স্পষ্ট রাজনৈতিক হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজে পাই এবং যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা করেন, তা এখনো প্রাসঙ্গিক। মন্ত্রী জোয়ারদার তার গ্রামের বাড়ি যাবেন কিন্তু তার পিএ সোলায়মান কোনভাবে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে জোয়ারদার বেজায় নাখোশ হন সোলায়মানের ওপর এবং তার ট্যুর ক্যান্সেলের ভেতর দিয়ে গল্প এগোয়। সোলায়মান মন্ত্রীর ট্যুর প্লান করেছিল খুব সাধারণভাবে, ট্রেন, গাড়িতে করে সাধারণ মানুষ যেমন করে গন্তব্যে পৌঁছায় তেমন। কিন্তু জোয়ারদার তার গ্রাম এবং নির্বাচনী এলাকায় হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে চান—তার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখাতে এবং গ্রামবাসীদের চমক দিয়ে আলোচনায় থাকতে চান। সোলায়মানের সাথে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে আমরা মন্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি। সোলায়মান তড়িৎ গতিতে মন্ত্রীকে খুশি করতে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে ফেললে তিনি তাকে এলাকায় একজন রোগী বেছে রাখতে নির্দেশ দেন, যাকে তিনি হেলিকপ্টারে করে ঢাকাতে নিয়ে আসবেন। তার মানবিকতা, উদারতার নিদর্শন স্বরূপ তাকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে আবার দেশে পাঠিয়ে তিনি মানুষের মন জয় করবেন। সোলায়মানও সেই নির্দেশ মতো সব ব্যবস্থা করে।
হুমায়ূন আহমেদের সব থেকে বড় যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল—উনি সবকিছু ভিজুয়ালি দেখাতে চেষ্টা করেন, পাঠক যেন তিনি যা দেখাতে চান তাই যেন দেখতে পারেন সে ব্যাপারে তিনি সবসময় অধিক মনযোগী। একই সাথে অন্যকে হিউমিলিয়েট করে তাঁর হিউমার তৈরির, কৌতুকময় পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষমতা অনন্য। যার কারণে সিরিয়াস পরিস্থিতিতে এক ধরনের কমিক রিলিফ দিতে পারেন তিনি, যা একই সাথে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নাটকীয় আবহ তৈরি করে। শুধুমাত্র কৌতুককে ব্যবহার করে তিনি যদি কিছু কাজ করতেন তাহলে পাঠক তার কৌতুকগুলোকে বাংলা সিনেমার অপরিহার্য কৌতুক অভিনেতার কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টার মতো মনে করতো না। যেভাবে কৌতুককে তিনি বেশিরভাগ লেখায় বা কাজে ব্যবহার করেছেন তা মূল বক্তব্যের বাইরে গিয়ে আলাদাভাবে পাঠক-দর্শকের মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, সেই গল্পের মূল বক্তব্য তার কারণে হারিয়ে গেছে! সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ‘খাদক’ বা ‘মন্ত্রীর হেলিকপ্টার’ দুটি গল্পই বেশ সফল।
আলোচ্য গল্পটিতে মন্ত্রী তার এলাকায় গিয়ে নিজে যেমন কিছু কৌতুককর ঘটনার জন্ম দেন তেমন নিজেও বেশ কিছু কৌতুককর পরিস্থিতির শিকার হন। সবকিছু তার পরিকল্পনা মতো ঘটলেও শেষ চমক হিসাবে যে রোগীকে তিনি হেলিকপ্টারে উঠান, তার অবস্থা এতই সঙ্গীন হয়ে যায় যে, সে ঢাকা পর্যন্ত টিকবে কি টিকবে না এমন অবস্থায় মন্ত্রী তাকে নিয়ে আবার এলাকায় ফিরে আসেন। এবং লোকটির মৃত্যু হয়। পিএ’র পরামর্শ মতো পরিস্থিতিকে ম্যানিপুলেট করে তিনি তার পক্ষেই কাজে লাগান, যেমনটা বর্তমানের রাজনীতিবিদরাও করে থাকেন। ধারণা করা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটলে ভবিষতেও এই একই ধরনের ঘটনা ঘটে চলবে। একারণে এই গল্পটা এখনো তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।
হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন। মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধ না, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে ছুঁয়ে গেছে এবং তার প্রভাবে মানুষের জীবন কেমন করে বদলে গেছে তাঁর এমন গল্পগুলোকেই বেশি সফল গল্প হিসাবে ধরা যেতে পারে। তার মধ্য উল্লেখযোগ্য ‘অসুখ’, ‘জলিল সাহেবের পিটিশন’, ‘শীত’ ও ‘শ্যামল ছায়া’। এই গল্পগুলোর ভেতর ‘অসুখ’ এবং ‘শীত’ নামক গল্প দুটি প্রায় একই ধরনের। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর দুস্থ, দুঃসহ অসহায় অবস্থাকে উপজীব্য করে গল্প দু’টি বিস্তার লাভ করেছে। 'অসুখ' শহুরে পটভূমিতে লেখা একজন মায়ের গল্প, যিনি মুক্তিযুদ্ধে তার সন্তান হারিয়েছেন এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ছেলের বন্ধুর কাছ থেকে শুধু তার মৃত্যুর গল্পটা শুনে নিশ্চিত হতে চান যে, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের জবাইয়ের মতো কষ্টকর মৃত্যু হয়নি, অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর গুলিতে মারা গেছে তার সন্তান। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা খোকনের বন্ধু রঞ্জুকে তাই তার স্কুল শিক্ষক বাবা বারবার খুঁজে নিয়ে আসেন খোকনের মায়ের কাছে। রঞ্জু তাকে প্রবোধ দিয়ে সেই গল্পটি শুনিয়ে যাবার কিছুদিন পরই মা আবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। রঞ্জুর আবারো খোঁজ পড়ে বলেই সে এই পরিবার থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। এমন পালিয়ে থাকা রঞ্জুকে একদিন খোকনের বাবা পাকড়াও করে বাসায় নিয়ে আসার ভেতর দিয়ে গল্প শুরু হয়। পাঠক হিসাবে আমরা এক এক করে ঘটনার ভেতর ঢুকতে থাকি এবং গল্পের শেষে আবিষ্কার করি রঞ্জুর মতো মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের অস্বস্তিকর ঘটনাসমূহ থেকে দূরে থাকতে চাইছি।
‘শীত’ গল্পটিও গ্রামীণ এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিবারের গল্প। মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারানো এক বৃদ্ধ পিতার শীত-কষ্ট লাঘবের জন্য একটা কম্বলের আকুতি এবং প্রাপ্তি নিয়েই এই গল্প বিস্তার লাভ করে। গল্পের পেছনে এই সংসারের হাল ধরা সেই মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রীর কঠিন জীবন এবং সংগ্রাম ছাড়াও কিছু কম্প্রোমাইজের ইঙ্গিতময়তা থাকলেও তা ঠিক পরিষ্কার হয় না। আমরা শুধু সেই বিধবা নারীর কষ্টকর জীবনে একাকিত্বের কান্নাই শুনতে পাই।
মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোর ভেতর ‘জলিল সাহেবের পিটিশন’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধারণা করা যেতে পারে, এই গল্প লেখার সময়কাল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন শুরুর প্রথম দিকে। আমরা যেন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের এক প্রতিরূপ দেখতে পাই জলিল সাহেবের ভেতর। এই গল্পে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর স্বভাব সুলভ হিউমার ব্যবহার করে জলিল সাহেবের কষ্টকর পরিকল্পনাকে আরো দুরূহ করে তোলেন। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে আমরা আবারো লেখকের ইনভলভমেন্ট খুঁজে পাই—যুদ্ধে দুই সন্তান হারানো জলিল সাহেব এক সময়ের প্রতিবেশী লেখকের সাথে সখ্যতা করতে, অনুপ্রেরণা, সমর্থন পেতে ছুটে আসেন। তাদের কথোপকথনের ভেতর থেকেই পাঠক জানতে পারেন জলিল সাহেব একটি পিটিশন করছে সরকারের কাছে, যার বিষয় হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদি মারা গিয়েছিল, যারা মেরেছিল সেই অপরাধীদের বিচার হয়েছে, এখনো হচ্ছে আর বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ মানুষ মেরেছে যারা তারা পার পেয়ে যাবে? তাই তিনি সবার কাছ থেকে তাদের বিচারের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন তার পিটিশনের সাথে যুক্ত করবেন বলে। হিমিউলিশন, অসহোযোগিতা, রোগ, জ্বরা কিছুই জলিল সাহেবকে দমাতে পারে না। এক সময় দেশ ছেড়ে এবং জলিল সাহেবের এলাকা ছেড়ে আসবার কারণে লেখকের সাথে তার দূরত্ব তৈরি হয়। লেখক অনেকদিন পর খোঁজে গিয়ে জানতে পারেন, তার অদম্য হালনাগাদের খবরাখবর। এক সময় দীর্ঘ বিরতিতে লেখক জলিল সাহেবের বাসায় গিয়ে জানতে পারেন, জলিল সাহেব মারা গেছেন। কিন্তু তিনি বলে গেছেন—একদিন না একদিন কেউ একজন আসবে এই পিটিশনের ফাইল, দলিল দস্তাবেজ নিতে। কিন্তু লেখক সেই ফাইল নিতে আর যান না। সবার মতো তিনিও অনেক ঝামেলা, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন জলিল সাহেবের নাতনী হয়তো এখনো সেই ফাইলপত্র প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখছে একদিন কেউ আসবে বলে। শেষ লাইনটা এই গল্পের সব থেকে দুর্বল লাইন। যেখানে লেখক বলছেন, ‘এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।’ সামঞ্জস্যহীন এই লাইনটার আগে লেখক যে পরিমিতি বোধের, ইঙ্গিতময়তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই বাক্যটার ভেতর দিয়ে তা নিমিষে উধাও হয়ে যায়।
লেখক বড় বা ছোট হয় না, অতিপ্রজ বা বিরলপ্রজ তাতে কিছু যায় আসে না। আসে যায় তার সৃষ্টিকর্ম কি স্বাক্ষর রেখে যায় সেটার ওপর। পাঠকপ্রিয় হলেই সেই লেখক কালোত্তীর্ণ হবেন, এমন কোন নিয়ম যেমন নেই, তেমনি জনপ্রিয় না হলে লেখক মহকালে হারিয়ে যাবেন এমন ধারণাও অমূলক। গল্পের বিষয় কতটা সময়োপযোগী, কতটা প্রাসঙ্গিকতা ধারণ করতে পারছে তার উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি কর্মটি কতখানি শিল্প হয়ে উঠতে পেরেছে তার ওপরও নির্ভর করে। সাহিত্য হয়ে ওঠা মানে শিল্প হয়ে ওঠা। সেই বিচারে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ভবিষ্যতের সেসব পাঠকের জন্য যারা নির্মোহভাবে—নাটক না, সিনেমা না, লেখকের ব্যক্তি জীবন না, কর্মকাণ্ডে না বা মিডিয়ার টিআরপি বা কাটতি বাড়ানোর পিআর প্রেশারে না; সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে পড়ে, বুঝে-শুনে প্রণোদনা পাবে, প্রাসঙ্গিক মনে করবে তার জন্য।
আমাদের বয়স বেড়েছে, পালাতে পালাতে আমরা ক্লান্ত হয়ে মলম বিক্রেতাদের মোহনীয় ক্লান্তিকর বয়ানের কারণ, উদ্দেশ্য, বিধেয় বুঝে ফেলেছি। বাণিজ্যিক কারণেই মলম বিক্রেতারা তাদের পেশা বদলে ফেলেছে। তাদের নতুন ভড়ং নতুন বয়ান পদ্ধতি, নতুন উপায় বের করেছে, যেটা করতে পারেনি তা হলো—সাহিত্য পদবাচ্যের শিল্পটাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি বা তারা চেষ্টা না করেই নির্বোধ পাঠকের কাছে আবেগের পপকর্ন বিক্রির যোগাড়যন্তর করে গেছেন পূর্বসূরিদের মতো। একই পথের পথিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাহীন জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন ছোট গল্পে ইতিমধ্যে অনেক ম্যাড়ম্যাড়া হয়ে গেছেন, অনেকাংশেই উপযোগিতা হারিয়েছেন বলা যায়। এখনও যেটুকু রঙ জমে আছে সেখানে, সেটুকুতেই খাঁটি হুমায়ূন আহমেদ অবশিষ্ট আছেন বলে মনে করি।





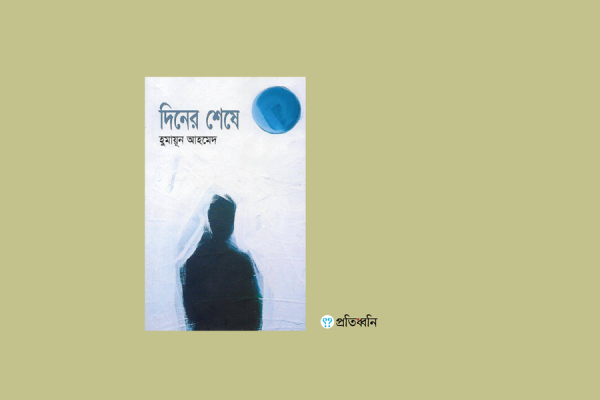

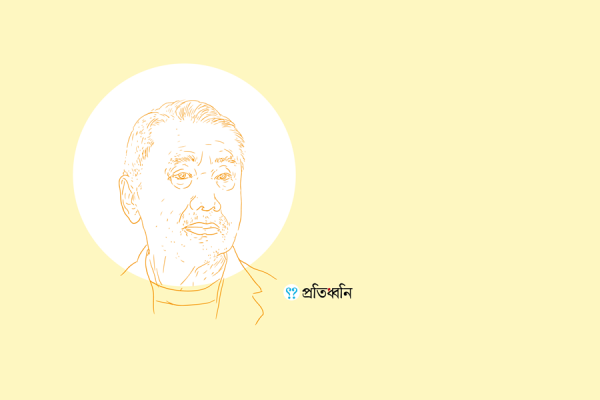
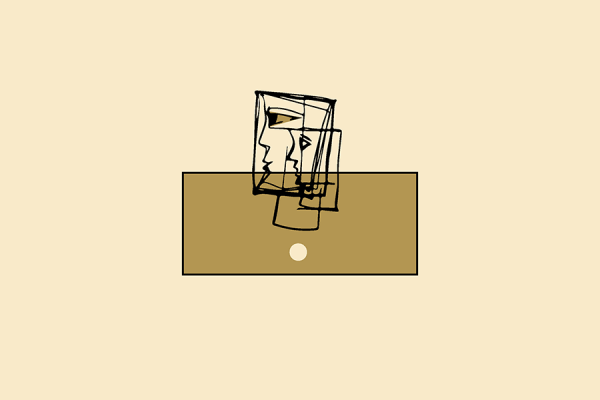
আপনার মন্তব্য প্রদান করুন