মরিয়া আমারে রেহাই দে
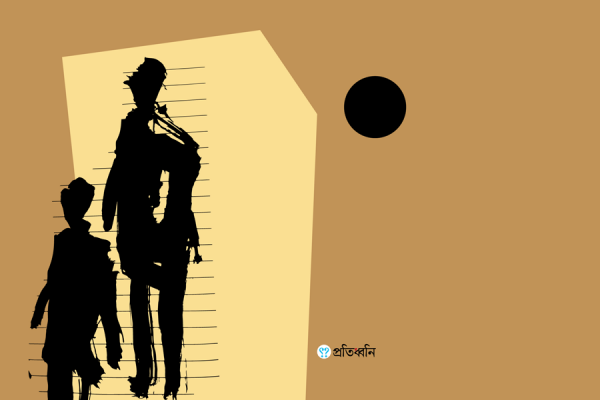
আমি আকলিমা। মোসাম্মাৎ আকলিমা বেগম বড়ভূইয়া। নাম শুনে আমাকে অশিক্ষিত গেয়ো ভূত ভাবার কোনো অবকাশ নেই। আমি গ্রামের হতে পারি, গ্রাম্য হতে পারি, বাবা-মা আমার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অশিক্ষিত হতে পারেন, কিন্তু আমি অশিক্ষিত নই। ডিগ্রি পাশ মেয়ে আমি। তাও বছর আঠাশেক আগের ডিগ্রি পাশ। আর যদি সাল-তারিখ গোনে ডিগ্রি পাশের ইয়ার খুঁজি, তাহলে বয়স আমার আপনারা এই মুহূর্তে যা আন্দাজ করছেন তার থেকে মনে হয় একটু বেশি-ই হবে।
আর আমি আমার বাবা-মায়ের আদরের বিশেষ করে বাবার অতি আদরের বড় মেয়ে ছিলাম। একটা সময় যখন আমি বেশ ছোটো ছিলাম, তখন বাবা বাড়িতে থাকলে আমাকে ছাড়া আহার করতেন না; আমাকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন এবং খাইয়েও দিতেন। আর বাইরে থেকে প্রতিদিন কিছু না কিছু আনতেন আমার জন্যে।
এভাবেই আনন্দে-আহলাদে আটখানা হয়ে আমার শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হচ্ছিল।
সে সময়ে দাদাজানও বেঁচে ছিলেন। আমার দাদাজানের তো ন্যাওটা ছিলাম আমি, মানে দাদাজান আমাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না।
এবার আমাদের বাড়িঘরের কথা একটু বলে নিই। এটাই আমাদের বাড়ি। দাদাজানের করা এক কিয়ারি বাড়ি। তবে এটা আমাদের মূল বাড়ি না। আমাদের মূল বাড়ি হলো শিলচর। শিলচরের দুধপাতিল না কোথায় যেন। আজ থেকে চুয়াত্তর-পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বছর আগে দেশভাগের সময় আমার দাদা তাঁর বাসের মালিক কন্ট্রাকটর রহিম উদ্দিন আহমদের হাত ধরে এ গ্রামে এসে বসত গড়েছিলেন।
সে সময় চারদিকে তখন আনন্দ-উল্লাস আর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। আর ওই দাঙ্গা চলাকালে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত স্বজনহারা লোকজন ছাড়াও আরও একদল লোক দুধের নহর বইবে সোনার পাকিস্তানে বিশ্বাস করে আপার আসাম ও বর্তমানে যেটা দক্ষিণ আসাম, সেই আসামের নিজ বাড়িঘর-ভিটেমাটি ছেড়ে এ তল্লাটের আশেপাশের এক-দুটি গ্রামে যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের একজন হলেন আমার দাদা সাইয়ুব আলি বড়ভূইয়া।
আর তিনি যে একেবারে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন তা কিন্তু না। নিজ জেলায় যে কন্ট্রাকটরের বাস চালাতেন তিনি, একটু আগে যার কথা বলেছি সেই কন্ট্রাক্টর রহিম উদ্দিন আহমদের বাড়ি পাকিস্তানে পড়ায় তিনি তার-ই হাত ধরে তার-ই এলাকায় এসেছিলেন, এবং এখানেও তিনি তাঁর বাস চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন কিছুদিনের মধ্যে-ই।
এবং দেখতে দেখতে বলা যায় চোখের পলকে আমার বড়ফুফু সবতেরা বেগম বড়ভূইয়াকে তাঁর হাতে দ্বিতীয় বউ হিসেবে সমজে দিয়ে তিনি বাড়িও পেয়ে যান মানে তাঁর বাড়িঘর হয়ে যায় জামাইয়ের তরফ থেকে এমনি এমনি।
কিন্তু আমার মতোই আমার এই সুন্দরী-রূপবতী বড়ফুফুর ভাগ্য ছিল ভীষণ খারাপ। বছর পাড়ি দিয়ে মাস দুয়েক যেতে না যেতে-ই স্বামী তাঁর কলেরায় ইহজগত ত্যাগ করলে সতীন আর সৎ ছেলেমেয়েদের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। এবং আবার বছর খানিক পেরুতে না পেরুতে-ই দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গেলেও একসময় আবার ফিরে আসতে হয় ওই স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে।
তারপর তো অলক্ষ্মী উপাধি পাওয়া বড়ফুফুকে আর বিয়ে দেয়া যায়নি। তারও বিয়ের প্রস্তাব আসেনি, আর তিনিও কোনো অবস্থাতে-ই বিয়েতে রাজি হোননি।
আর এভাবে-ই চলছিল দিন-মাস-বছর।
ততদিনে কিন্তু মা এসে গেছেন বাড়িতে, অর্থাৎ তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে বাবার সঙ্গে।
প্রথম প্রথম মায়ের সঙ্গে তাঁর শাশুড়ি এবং ননাসের সম্পর্ক বেশ ভালো-ই ছিল। মা কিন্তু নিজে আমাকে একথা বলেছিলেন। একটা সংসারে দীর্ঘদিন থেকে একসঙ্গে বসবাস করলে স্বাভাবিকভাবে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ঠোকাঠুকি থাকে, এটাই স্বাভাবিক। মায়ের সঙ্গে বড়ফুফুর সম্পর্ক যতদিন দাদি বেঁচে ছিলেন ঠিক ততদিন ওই ঠোকাঠুকির পর্যায়ে ছিল, অর্থাৎ খোঁচাখুঁচি, তর্কাতর্কি এইসব আরকি মোটামুটি কমবেশি হতো।
তারপর দাদির দেহান্তর ঘটলে আস্তে আস্তে মা তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হোন।
একটা সময় তো পান থেকে চুন খসে পড়লেই মা কথা বলতেন, বকবক করতেন তাঁর ননাসের উদ্দেশ্যে। এহেন অবস্থায় বড়ফুফু কী বলবেন, কী করবেন! উঠোনে একাকী বসে কাঁদতেন। মাঝেমধ্যে মায়ের জ্বালাতন যখন চরমে উঠত, তখন বড়ফুফু আর না পেরে অভিশাপ দিতেন। বলতেন, ‘আল্লা, ঠাটা ফালাইস ওউ বেটির উফরে। আমারে শান্তি দিরে না, তোর কোনোগে যেন শান্তি না পায়।’
মা ক্ষান্ত হতেন কিছু সময়ের জন্যে। তারপর আবার যেই লাউ সেই কদু।
বলতেন,‘আমার খাইয়া, আমার পরিয়া, আমারে অভিশাপ দেস। বারো আমার বাড়ি তাকি। বারো।’
বড়ফুফু বলতেন,‘ইগু তোর বাড়ি অইল কিলা! ইগু আমার বাড়ি। আমার বাফোর বাড়ি। তোর বাড়ি নায়।’
মা সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল গালি উচ্চারণ করতেন। বলতেন, ‘হেটামারাউনির পুরি পুন্দেদি তোর বাড়ি ইগু বরি দিমু।’
মায়ের অবিরাম বকাবকি চলত। বড়ফুফু সহ্য করতে না পেরে তাঁর বান্ধবীর বাড়ি, বোনের বাড়ি চলে যেতেন। দিন সাতেক থেকে তারপর বাড়ি ফিরতেন।
ফিরতে না ফিরতে আবার খোঁচা খেতেন। বান্ধবীর বাড়ি হলে মা বলতেন, ‘বান্ধবী না কার বাড়িত গেলায়। রই গেলায় না কেনে? বাঁচিলাম অইলে আমি।’
বড়ফুফু আর কোনো উত্তর করতেন না। কেবল চোখের পানি ফেলতেন।
আসলে আমাদের এই মা ছিলেন আজরাইল টাইপ মানবী। তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে উঠতে পারত না। তাই অনেকে তাঁকে এড়িয়ে চলত। আর বাবা তো কেবল গাইগুই করতেন। কোনো বিষয় নিয়ে পারতপক্ষে মায়ের মুখোমুখি হতেন না। চাল-ডালের ভালো ব্যবসায়ী হলেও অত্যন্ত ভালো মানুষ আমার এই বাবাকে লোকে তাঁর অগোচরে বলত স্ত্রৈণ! কাজেই, বাবা শুধু মাকে বোঝাতেন। বলতেন বড়ফুফুর সঙ্গে দরবার না করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আর আমার বুদ্ধিমান মা অধিকাংশ সময় বড়ফুফুকে অপমান করতেন বাবার বাড়ির বাইরে অবস্থানকালীন সময়ে।
এভাবে গঞ্জনা সহ্য করতে করতে একদিন বড়ফুফু বিষপানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেঁচে গেলেন ডাক্তারদের অবিরাম প্রচেষ্টায়।
তারপর মাস ছয়েক তাঁর ছোটোবোনের বাড়ি গিয়ে থাকলেন। কিন্তু ছোটোবোনের বাড়ি আর কদিন থাকা যায়? সম্মানের তো একটা ব্যাপার- স্যাপার আছে। তাই বাবা গিয়ে তাঁর বড়বোনকে নিয়ে এলেন।
মা তাঁর ননাসকে দেখে বললেন, ‘আইছোনি আফা, আমি তো মনে করছি তুমি রই যেইবায়।’
এভাবে চলতে চলতে একদিন বড়ফুফু হার্ট অ্যাটাকে ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে চলে গেলেন। তখন তাঁর বয়স কত? মনে হয় একষট্টি কিংবা বাষট্টি হবে। হায়রে বড়ফুফু! জীবনে শান্তি পেলে না!
বড়ফুফুর বছর দশেক পরে বাবা, তারপর প্রায় আটবছর পর একদিন মাও ইহজগত ত্যাগ করলেন। মায়ের আত্মার সঙ্গে সকলের আত্মার শান্তি কামনা করছি।
এখন আমি আমার ভাইবোনদের কথা একটু বলে নিই।
আমার তিন ভাই আর আমি সহ দুই বোন। আমার দুই ভাই বড়, আমি তিন নম্বর, তারপর ছোটো একটি ভাই, তারপর সকলের ছোটোবোন।
সকলেই সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। আর আমার বড় দুই ভাই তো দেশে নেই। সবচেয়ে বড়ভাই আমেরিকায় আর মেজোভাই কানাডায় সপরিবারে বসবাস করছেন। গত বছর দুই ভাই ফ্যামেলি নিয়ে এসেছিলেন। এটাই মনে হয় তাঁদের শেষ আসা দেশে।
যাইহোক, আমি বসবাস করি আমার ছোটোভাইয়ের সঙ্গে। অবশ্য বসবাস করি বললে একটি ইতিবাচক বার্তা যায় সকলের কাছে। আসলে আমি শত গঞ্জনা সত্ত্বেও কোনোমতে পড়ে আছি মানে বেঁচে আছি। এই তো জীবন চলছে। আল্লা-খোদা ভয় করি, আর না হলে কোনদিন যে ভবলীলা সাঙ্গ করতাম! বেঁচে থাকার ইচ্ছে আমার কবে মরে গেছে!
অথচ, যখন শরফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তখন কী আনন্দে-ই না দিন অতিবাহিত হচ্ছিল! শরফুদ্দিন ছিল উচ্চশিক্ষিত। আমার কথার মূল্য দিত। আমিও তার কথা শুনতাম। ওর সঙ্গে আমার সাংসারিক জীবন কেবল চার বছরের ছিল। বিয়ের পর ও বলেছিল, ‘শুন আকলিমা। এখন থাক, পাঁচ বছর পর সন্তান নিমু। এখন তো আমরার বয়স কম। একটু আনন্দ-ফুর্তি করি। কিতা কও তুমি?’ সঙ্গে সঙ্গে ওর কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। সকলে তো রোমান্টিক হয় না, ও যখন রোমান্টিক, কাজেই ওর কথা ফেলতে পারিনি।
ও খুব ঘোরাঘুরি করত। সঙ্গে আমিও ঘুরতাম। আর এই ঘোরাঘুরি যে কাল হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত! তখন আমরা পুজোর ছুটিতে কলকাতা গেছি। উঠেছি জাকারিয়া স্ট্রিটের একটি হোটেলে। তারপর এই হাওড়া ব্রিজ দেখছি তো অ্যাসপ্লানেট যাচ্ছি। ঘুরছি আর ঘুরছি। একদিন ও বলল, ‘চলো সেন মহাশয়ের দই আর মিষ্টি খেয়ে আসি। সেন মহাশয়ের দই নাকি খুব-ই বিখ্যাত।’ আর ওই যাওয়া-ই ওর কাল হলো। ফেরার পথে টেক্সি অ্যাক্সিডেন্টে এই বিদেশ-বিভুইয়ে সে মরে গেল। কিন্তু আশ্চর্য আমার কিছু-ই হলো না। একাকী মেয়ে মানুষ কী করি ভড়কে গেলাম। পরে দুজন বাংলাদেশি তরুণের সহায়তায় ওর ডেডবডি দেশে নিয়ে এলাম।
তখন তো বাবা-মা দুজনে বেঁচে ছিলেন। মা খুব কাঁদলেন। কেঁদে-কেটে বুক ভাসালেন। কিন্তু বাবা অভয় দিলেন।
বললেন, ‘যা অওয়ার অই গেছে। আরাইবার কুনতা নাই। মন শক্ত করি উবা। আর পারলে কিছু একটা কর। বিএ পাশ তো তুই।’
তখন আমার কিছু একটা করার ইচ্ছে মন থেকে উবে গেছে। বাবার বার বার তাগিদ সত্ত্বেও প্রথমে কিছুই করলাম না। কিন্তু বাবা তো, তাই লেগে থাকলেন। তারপর আবার তাগিদের পর তাগিদ দিতে লাগলেন। শেষমেশ, বাবার প্রচেষ্টায় শিক্ষক হিসেবে একটা এমপিওভূক্ত স্কুলে ঢুকে পড়লাম।
সময়টা ভালোভাবেই কেটে যেত। মাসিক সম্মানী হিসেবে মোটামুটি একটা ভালো টোকেন মানি পেতাম। ভালোই লাগত।
কিন্তু হেডমাস্টারটা ছিল খুবই খচ্চর! উত্যক্ত করত! তবুও পারতপক্ষে কোনো কিছুই বলতাম না। মেনে নিতে চেষ্টা করতাম। পুরুষদের স্বভাবই হচ্ছে সময় ও সুযোগ পেলেই মেয়েদের উত্যক্ত করা। আর খালি গোলপোস্ট পেলে তো কথাই নেই, কাজ হলো বার বার হানা দেওয়া। একদিন সিন ক্রিয়েট হয়ে গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে খচ্চরটাকে জুতা খুলে মারলাম। কিছুই করতাম না আমি। কিন্তু সবকিছুর তো একটা লিমিট আছে! রুমে একা পেয়ে বুকে হাত দিলে কী আর করার থাকে!
খচ্চরটার চাকরি গেলেও আমি চাকরি ছাড়িনি। ছাড়ার ইচ্ছেও ছিল না। বরঞ্চ করার আশায় এমপিওভূক্তও হয়েছিলাম।
সেই সময় কলিগদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দুজনে অচিরেই বিয়ে করব, ঘর বাঁধব। তারপর এক বৃষ্টির দিনে ওরই বাসায় আবেগ আর ধরে রাখতে পারিনি। কী থেকে কী যেন হয়ে গিয়েছিল শরীরে! ওর তাগাদায় ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিলাম। আর এই একবার মিলনের ফলে যে গর্ভবতী হয়ে পড়ব তা কে জানত? গর্ভবতী হওয়ার পর ওর আসল রূপ প্রকাশ পেল। ও সবকিছু অস্বীকার করে বসল। শেষমেশ, আর না পেরে গোপনে গর্ভপাত করালাম। কাক-পক্ষীও টের পেল না।
কিন্তু কাক-পক্ষী টের না পেলেও ওর জন্যে চাকরি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে সকলেই মনে হয় একটু-আধটু তারপর সবকিছু মনে হয় জেনে গেল। স্কুলে গেলেই অস্বস্তি শুরু হতো। অতিদ্রুত হিরো থেকে জিরো হয়ে গেলাম। আর তখন-ই বিষয়টি আর বাড়তে না দিয়ে চাকরি ছেড়ে চিরতরে চলে এলাম।
তখন আমার বয়স ত্রিশের কোঠায়। ছোটোবোন আসিয়ার বিয়ে দিয়ে ছোটোভাই মহিউদ্দিন কেবল বিয়ে করে ঘরে বউ উঠিয়েছে। মা আছেন, বাবা গত হয়েছেন। আর বড়ভাই, মেজোভাই তো প্রবাসে জীবনযাপন করছেন।
সে সময় বছর পাঁচেক কম চেষ্টা চরিত্র করা হয়নি আমার বিয়ের জন্যে। আত্মীয়রা উঠেপড়ে লেগেছেন। ঘটক ধরা হয়েছে। ঘটক তিলকে তাল বানিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পাত্র পাওয়া যেত তবে সব বুড়ো হাবড়া! একবার মনে হয়েছিল রাজি হয়ে যাই। আমারও তো বয়স কম হলো না। কিন্তু পরক্ষণে-ই বাবার বয়সী কারো সঙ্গে ঘর করার কথা ভাবতে-ই পারতাম না। বাবা আমার মাকে ঘরে তুলেছিলেন বছর বাইশেক বয়সে। তাহলে তো ওরা বাবার বয়সী!
আর সেই সময়ে মহিউদ্দিনের বউ মায়মুনাকে বোঝা যায়নি। মা তাঁর স্বভাবচরিত্র নিয়েই ছিলেন। মায়মুনা মায়ের কথায় কোনো রা করত না। তবে মাঝেমধ্যে মায়ের ওপর রাগ করে একদিন-দুদিন খাওয়া থেকে বিরত থাকত। আর তার বাবার বাড়ি গেলে সহজেই ফিরে আসত না। মা খবর দিলেও আসত না। মহিউদ্দিনকে যেতে হতো। মহিউদ্দিন বউ নিয়ে এসে বাড়িতে চোটপাট করত। এভাবেই সংসার এগোচ্ছিল। কখনো টক, কখনো ঝাল, কখনো মিষ্টি। তবে মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন মায়ের মুঠির মধ্যে সংসার ছিল। বলা যায় মোটামুটি সুন্দরভাবেই সংসার এগিয়ে যাচ্ছিল।
কিন্তু মা গত হওয়ার পর মায়মুনা তার রূপ বদল করল। সে তার স্বরূপে এলো। এখন সে পুরো বাড়ির মালিক। একচ্ছত্র অধিপতি। আর মহিউদ্দিন স্ত্রৈণ!
মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে যাই বড়ফুফুর সঙ্গে মা যা যা করেছেন, মায়মুনা যেন তা দ্বিগুণ আকারে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাকে! ঘরে আর কজন মানুষই বা আমরা আছি। মহিউদ্দিন, মায়মুনা আর আমি। ওদের একছেলে আর একমেয়ে থাকলেও মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়ে গেছে, আর ছেলে এই তো মাস পাঁচেক হয় আইএলটিএস করে কানাডায় পাড়ি জমিয়েছে।
আর জুতা সেলাই থেকে শুরু করে চন্ডিপাঠ পর্যন্ত বাড়ির সবকিছু আমি সামলাই। মনে করি ভাইয়ের সংসারে খাচ্ছি যখন তখন এদিক দিয়ে প্রতিদান দিই। তবুও মায়মুনা সন্তুষ্ট না। সবসময় বকবক করে, খোঁচাখুঁচি করে!
এখন এই তো শেষ মাঘের পড়ন্ত বিকেল। মিনিট ত্রিশেক হয় এই টেবিলে বসে এই লেখা লেখার চেষ্টা করছি। কদিন থেকেই এই লেখালেখির চেষ্টাচরিত্র চলছে।
ওই যে মায়মুনার গলা শোনা যাচ্ছে।
‘আস্তা বাড়ি-উঠান ঝরাপাতায় বরি গেছে। ইতা ডং বাদ দেও। উটো, ঝাড়ু দেও, বালেস্টার আপা। আর খাইয়ো কমাইয়া। শরীল বালা থাকব।’
এমনিতে খাই কম আমি। এই বয়সে বেশি খেলে বেঢপ মোটা হয়ে বিদঘুটে লাগবে। তারপরও খোঁটা দিচ্ছে। মনে হয় যেন সে খাওয়াচ্ছে। আমি আমার ভাইয়ের খাচ্ছি। আর ভাইয়ের ওপর আমার অধিকার আছে। আমার-ই ভাই।
না, আজ একটা উত্তর দিতে হবে। বার বার খালি মাঠে গোল দিয়ে যাবে তা কিন্তু হয় না, শোভনও দেখায় না।
‘ইতা তো আমার কাম নায়, মায়মুনা। আর মনে অয় তুমি যেন খাওয়াইরায়।’
‘তে কে খাওয়ার?’
‘আমার বাইর আমি খাইয়ার।’
‘বেশি মাতিস না। আইজ কইলে কাইল বার অইয়া যাওয়া লাগব।
‘তোর বাড়িনি?’
‘অয় আমার বাড়ি। আমার জামাইর বাড়ি।’
‘অয় তোর বাবায় তোর নামেই বাড়ি লেকিয়া দিসইন।’
‘হেটামারাউনির অলক্ষ্মী। আইজ তোর একদিন কী আমার একদিন। আইজ তুই শেষ। তোরে ঝাড়ু দিয়া যদি না পিটাইছি তে আমার নাম মায়মুনা না। মরস না কেনে। মর। মরিয়া আমারে রেহাই দে।’






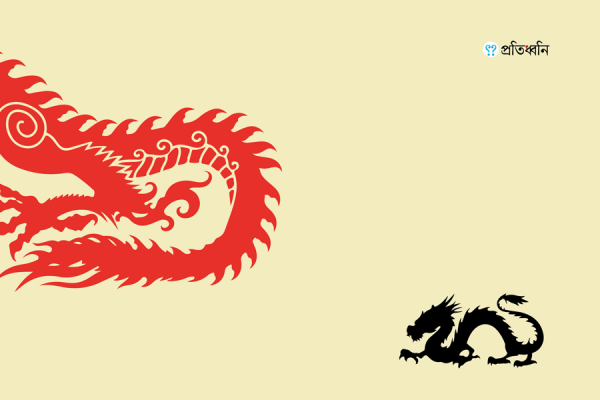
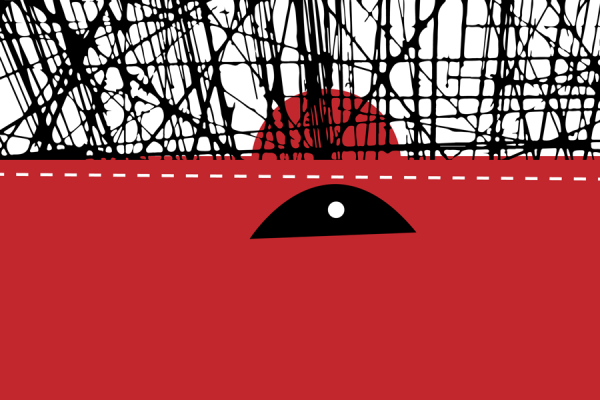

আপনার মন্তব্য প্রদান করুন