জীবনের অলিখিত উপাখ্যান
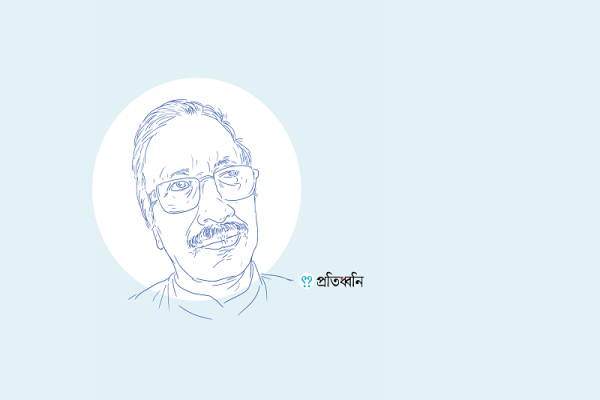
লেখক আপন স্বভাবদোষে যতই অসামাজিক হোক, কিংবা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী যোদ্ধা, সমাজের ন্যূনতম ইউনিট পরিবার তার জন্যও অপরিহার্য। শৈশবে তো বটেই, যৌবনে স্বাধীন-স্বাবলম্বী ও বৃদ্ধবয়সে কিছুটা পরনির্ভর হওয়ার পরও। এ সত্য আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি বালক বয়সেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে। লেখার ও পাঠের কাজটি একা করতে হয় সত্য, কিন্তু নির্জনতা-বিলাসী লেখকেরও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য প্রিয়জনের সান্নিধ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কখনো-বা যৌথ একাত্মতা হয়ে দাঁড়ায়মৌলিক চাহিদার মতো বিষয়। যেহেতু সব মানুষককেই প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদার জোগান দেয় তার পরিবার, পরিবারই তাই সমাজের প্রাথমিক ও একক ইউনিট। যৌবনে ঢাকায় এসে বছর পাঁচেক বিদ্রোহী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের পর আমি পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আবার হাড়েমজ্জায় অনুভব করতে লাগলাম। যে বন্ধুর সঙ্গে মেস-এ থাকি, তার এবং মেসের বাইরেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ও আড্ডায় সাময়িক আনন্দ মেলে। তাদের সঙ্গ পেতে অনেক সময় খালি পেটেও মৃত্যুসঞ্জীবনী সুরা কি তাঁতি বাজারে দেশী জিনিস পানেও আপত্তি করি না। কিন্তু এসব অনিয়মের ফলে ক্ষতির দিকটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততদিনে। যখন-তখন পেটব্যথায় কুঁকড়ে যাই। অ্যাসিডিটির আধিক্যে বমিও করে ফেলি প্রায়ই। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন, গ্যাসট্রিক-আলসার হতে দেরি নেই। নিয়ম করে চলতে হবে। না হলে শুধু পেট না, পেটের নিচে ও উপরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিকল হবে।
শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়ম করে খাওয়া-ব্যায়াম যে জরুরি, এ সচেতনতা তো কৈশোরেও ছিল এবং অনুসরণ করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঢাকায় আসার পর সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে বড় লেখক হওয়ার জন্য রোজ রুটিন করে লিখতে বসাটাও ফরজ। এই ফরজ কাজও কাজা হয় প্রতিদিনই। এসব সমস্যার সমাধান হিসেবে নিজের সংগ্রামী জীবনের উপযুক্ত মেয়েসঙ্গী ও নিজের মনের মতো পরিবার সংগঠনের বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বাইশ বছর বয়সেই বিয়ে করেছিলেন। গাঁয়ের ছেলেরা আরো কম বয়সে করে। আমি বাইশ পেরিয়ে তখন তেইশে, যত দোষ থাক, নিয়মিত বেতন পাওয়ার চাকরিটা তো আছে। অতএব আর দেরি করছি কেন?
আমার বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্ধুরা বিয়ের প্রয়োজনটাকে তেমন পাত্তা দেয় না। বিয়ে ও পরিবার নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা শোনায়। আমার হবু স্ত্রীকেও ‘লিগাল প্রস্টিটিউট’ বলে গাল দেয়। বিয়ে না করেও কত বড় ঘরের ছেলেরা, যেমন মণি সিংহ ও রণেশ দাশ গুপ্ত, সিরাজুল আলম খান সাম্যবাদী সমাজ গড়ার স্বপ্ন-সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেরকম হতে প্রেরণা দেয়।
আবার বিয়ে না করেও দলের মেয়ে কমরেডের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে স্ত্রীর প্রয়োজন মেটানো যায়, এমন উদাহরণও দেয় ঘনিষ্ঠ এক রাজনীতিক বন্ধু। নাম বলব না, এই বন্ধুটি আসলে জাসদ করত, মুজিব আমলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও আন্দোলনে যোগ দিয়ে মাস তিনেক জেলও খেটেছে। জাসদের আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র গণবাহিনীর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল তার। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে প্রকাশ্য রাজনীতি যখন বন্ধ, বন্ধুটি তার দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হারুনর রশীদকে অফিসে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় একদিন। নেতারা জেলে থাকায় দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। ফেনীর কোন কলেজে যেন অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করেছেন। রাজনীতি নিষিদ্ধ বলে পেশাদার বিপ্লবী রাজনীতিকরা তো বেকার বসে থাকতে পারেন না। ঘরোয়া রাজনীতি যেহেতু করা যাবে, এই সুযোগে হারুন ভাই একটা স্টাডি সার্কেল চালাবেন। সেখানে মার্কসবাদী দর্শন, সাহিত্য ও নিজেদের করণীয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে। হারুন ভাই আমাকেও এই সার্কেলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণা জানান। ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি গোপনে আরো প্রেরণা জোগায়, এই স্টাডি সার্কেলে দলের অনেক নারী কর্মীরাও যোগ দেবে। গেলেই পরিচয় হবে সবার সঙ্গে এবং তোমার প্রয়োজনীয় মেয়ে-কমরেডকে পেয়েও যেতে পারো।
বন্ধুর প্রেরণায় তাদের সার্কেলের অনেক ঘরোয়া সভায় যোগ দিয়েছি। বেশ কিছু নারীকর্মীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, যারা দলে প্রথম থেকেই জড়িত ও দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে অনেক। স্টাডি সার্কেলের সভায় দলের বাইরেও অনেক সাংস্কৃতিক-কর্মী আসতেন। নাটক-সিনেমা জগতের বেশ কিছু চেনামুখ, নাম ভুলে গেছি অনেকের, তবে শিল্পী এস এম সুলতান এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়েছিলেন মনে আছে। ‘গণসংস্কৃতি’ পত্রিকার সম্পাদক কুয়াইত-ইল-ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এই স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে। জীবনবীমা ভবনে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সভায় একদিন বর্তমানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সলিমুল্লাহ খানকেও দেখেছিলাম, তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, ‘প্রাক্সিস জর্নাল’ নামে একটা পত্রিকা করতেন। সেই পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মুখদেখা চেনা-পরিচয় হয়েছিল মাত্র। যাহোক, বৎসারিক কাল চলার পর স্টাডি সার্কেলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জাসদও ভেঙে একাধিক দল হলে হারুনুর রশীদ তার গ্রুপ নিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারি দলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক পদ পেয়েছিলেন। অন্যদিকে এই স্টাডি সার্কেলে বৎসারাধিক কাল জড়িত থাকলেও তা আমার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজনীতা বোধ দূর করতে পারেনি, বরং তীব্রতর করেছিল। লাভের মধ্যে ওই সময়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ‘দাঁড়াবার জায়গা’ নামে একটা উপন্যাস লিখতে পেরেছিলাম।
শেখ মুজিবের মতো রাজনৈতিক নেতা সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পর বাম-বিপ্লবী রাজনীতিতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়ানোর উৎসাহ কমে গিয়েছিল আমার। দেশের জন্য রাজনীতি কি সাহিত্য যাই করি, সুশৃঙ্খল জীবনে ফিরেতে পরিবার সংগঠন আশু করণীয় হয়ে উঠেছিল। সব পরিবারের কেন্দ্রে থাকে একজন নারী, গ্রামের বাড়িতে আমার মা যেমন। কিন্তু সেই পরিবারে তো আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ঢাকা শহরেও বস্তি থেকে গুলশানের অভিজাত সব পরিবারের কেন্দ্রেই আছে নারী। কিন্তু আমি আমার প্রয়োজনীয় নারীটিকে খুঁজে পাই কোথায়? এক প্রেমিক বন্ধুর উদারতায় সাময়িক যে প্রেমিকা জুটেছিল, আমার অনেকগুলি প্রেমপত্র বুকের ভিতরে নিয়ে সে ঢাকা ছেড়েই উধাও হয়েছে (ধ্বংসপ্রাপ্ত পত্রসাহিত্য নিবন্ধে উল্লেখ আছে তার)। তার কথা ভেবে লাভ নেই। বুঝে গেছি, দলে-সংগঠনে ভিড়েও যোগ্য জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পাবো না। বায়তুল মোকাররামে বিশেষ করে সোনার দোকানগুলিতে স্বর্ণশিকারী যেসব মেয়েমহিলা আসে, নিউমার্কেটে মার্কেটিং করতে আসে যারা, তাদের দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু তাদের কাউকে পছন্দ করে হুট করে প্রস্তাব দেওয়ার মতো পাগল তো হতে পারি না। উপন্যাসের অনেক নায়িকার প্রেমে পড়তেও ইচ্ছে করে, কিন্তু যতই প্রেমে পড়ি, তারা তো আমার ভাঙা ঘরে বাস্তবে পাশে এসে বসবে না। অতএব স্বপ্ন-কল্পনার জগতে নিজের হবুস্ত্রীকে যথাসম্ভব বাস্তব মূর্তি দিয়ে তার উদ্দেশে চিঠি লিখতে থাকি। অতঃপর এই স্বপ্নসাথীকে বাস্তব জীবনে সত্যি করে তুলতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, যে ঘটনা আমার জীবনে সবচেয়ে গভীর বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করেছে, এবং হৃদয় খুড়েবেদনা জাগানোর ভয়ে যে ঘটনাকে আমার গল্প-উপন্যাসেও ঠাঁই দিতে ভয় পেয়েছি; আজ সরাসরি সেই ঘটনা এ স্মৃতি-নিবন্ধের পাঠকদের জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দীর্ঘকাল নিজের ভেতরে চেপে রাখা হৃদয়বিদারক এ গল্পটি যেমন ঘটেছে, সেভাবেই পরিবেশন করব। বিন্দুমাত্র কল্পনার খাদ মেশাতে হবে না। তবে প্রকৃত সত্যকে বোঝার জন্য পরিবার সংগঠন সম্পর্কিত এ ট্রাজেডির সঙ্গে জড়িত আমার পরিবার, রংপুরের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কর্মস্থল গ্রন্থকেন্দ্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের স্মৃতিটা স্মরণ রাখা জরুরি। কারণ আমার জীবনসাথীকে পাওয়ার বা হারাবার পথটি এসবের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত।
হবুস্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার স্বপ্ন-পরিকল্পনা ও উদ্যোগ দেখে বন্ধুরা অনেকেই আমাকে ‘বিয়েপাগলা’ খেতাব দিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে পাগল মনে হতো না কখনই। কারণ একতাই বল। এ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়েছিল শৈশবেই ঈশপীয় গল্প পড়ে ও শুনে। আর সংঘবদ্ধতা যে কী সাংঘাতিক লড়াকু শক্তি, তা ১৯৭০-৭১ সনে জাতীয় জীবনে প্রমাণিত সত্য হয়ে উঠতে দেখেছি। এই সময়ে স্বভাবজাত দূরত্ব ঘুচিয়ে মুজিবভক্ত পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সবচেয়ে নিবিড় হয়েছিল। একাত্মতার বোধ গভীর হয়েছিল গ্রামবাসী সবার সঙ্গেই। কারণ মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীন স্বদেশ পেতে সংঘবদ্ধ লড়াকু বাঙালি হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের মহানায়ক। তরুণ বয়সে এই সত্য লেখকসত্তাকে প্রভাবিত করার স্মৃতি-কাহিনী একাধিক লেখায় সবিস্তারে বলেছি। এই স্মৃতি-নিবন্ধে স্বপ্নসাথী বা হবুস্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পাগলামিটা বুঝতে, একাত্মতা ভেঙে ক্রমে একা হওয়ার গল্পটা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।
স্বাধীনতা লাভের পর, মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে জাতীয় ঐক্যে ভাঙনের সুর নিজের পরিবারেই টের পাই প্রথম। পিতা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা, ফলে ইউনিয়ন পরিষদের রিলিপ কমিটির চেয়ারম্যান হলেন তিনি। রিলিপ বিতরণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য তার যে ধরণের দরদ ও দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, তার অভাব ব্যর্থ-মুক্তিযোদ্ধা পুত্রের দৃষ্টিতেও দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামে থেকে পিতার বিরুদ্ধে কিংবা সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজনীতি-সংগঠন করা আমার কাজ ছিল না। ছাত্রজীবন শুরুর কথা বলে শহরে নিজের আশ্রয়ে ফিরে যাই। কিন্তু কলেজে গিয়ে ডিগ্রি অর্জনে সময়ের অপচয়ের বদলে ততদিনে বিল্পবী কলম যোদ্ধা হয়ে ওঠার লক্ষ্যটাই চূড়ান্ত করে ফেলেছি।
রংপুর শহরে আমার অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা, বিশেষ করে মুজিববাহিনীতে ছিল যারা, তারা অনেকেই অস্ত্র লুকিয়ে রেখে স্বাধীন দেশে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা বাড়ানোর নানারকম পায়তারা করছিল। শহরের অবাঙালি মালিকদের খুঁজে না পেয়ে তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, দোকান ও বাড়িঘর দখল করেছে অনেকে। স্টেশন রোডে আলমনগরে এরকম একটি দখলকৃত বাড়িতে, যেন রাতারাতি গড়ে উঠেছে ‘চক্রবাক’ নামে একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন। আমার লেখালেখির বাতিকের খবর জানত স্থানীয় ছাত্রনেতাসহ মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের কয়েকজন। মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল ভাই ও ঘনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু ফজলু আমাকে একদিন চক্রবাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে। সংগঠন নতুন হলেও, মেইন রোডের ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একতলা ভবনটি তো নতুন নয়। ভিতরে অনেকগুলো কক্ষ। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের জন্য সাজানো কক্ষ ছাড়াও গানের ক্লাস, পাঠাগার, আড্ডা-আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম চালানোর জন্য আলাদা কক্ষ। বাড়িটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উপযুক্ত খালি জায়গা ছাড়াও পেছনের অংশে নেতা-কর্মীর রাত্রিবাস করার জন্য ছিল একাধিক কক্ষ। গ্যারেজে পলাতক ভবন মালিকের একটি বিকল কারও ছিল।

বিয়ের একবছর পর সস্ত্রীক লেখক
‘চক্রবাক’ অফিসের কাছে শহরের নিষিদ্ধ পল্লী ছিল। বেশ্যালয়ের পরিবেশ ও কাণ্ড-কীর্তি দেখার কৌতূহল নিয়ে এক সন্ধ্যায় জনৈক বন্ধুকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলাম অনেকক্ষণ। সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সন্ধ্যায় তোমাকে দেখলাম না, কোথায় ছিলে?’ হাসিমুখে সত্যি জবাব দিলাম। সভাপতি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। দেখার কৌতুহল মেটানো ছাড়া খারাপ কিছু করিনি, পকেটে অতো টাকাও ছিল না—নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও তিনি বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। পাঠক বন্ধুরা আমার বয়ানকে আশা করি শতভাগ সত্য জানবেন।
নতুন গজিয়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য লজিংবাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি ‘চক্রবাক’ অফিসের একটি কক্ষে উঠে বসবাস শুরু করি। অতপর গান শেখার ক্লাস, সাহিত্যের আড্ডা-অনুষ্ঠান, নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন, একুশে উদযাপনের প্রস্তুতি ও একুশে সংকলন প্রকাশ, চাঁদা তোলা, সেমিনার কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন—সব কাজেই শরিক হতে বেশ উৎসাহ বোধ করি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে একাত্মতার বোধ ভেঙে একা হতে থাকি। সংগঠনের নেতাদের সঙ্গেও বিরোধের সম্পর্কটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিরোধের কারণ ব্যাখ্যায়, নিজের দোষ ও অযোগ্যতার দিকটা কবুল করি আগে।
ক্লাস সিক্স থেকেই বাড়িছাড়া ও শহরে ছিলাম বলে বাবা-মা তেমন আদব-কায়দা শেখানোর সুযোগ পায়নি। মনোভাব যে গোপন করে চলতে হয় এ সমাজে, মুখে এক ও মনে আরেক রকম থাকা কৌশলও বটে—সেটা শিখিনি। ভিতরের আবেগ-চিন্তা অকপটে প্রকাশ করতে পারলেই আনন্দ হত। বাকস্বাধীনতা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে গেলেও ভয় পেতাম না। তাছাড়া বিখ্যাত কবি-লেখক হওয়ার স্বপ্নটা এমনভাবে বলতাম, যেন হয়েই গেছি। শহরে স্বাধীনভাবে থেকে ‘ইঁচড়ে পাকা’ হয়ে গিয়েছিলাম সন্দেহ নেই। আর যৌবনের স্বভাবগত বিদ্রোহ তো ছিলই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু খোঁচা দিয়ে বলত, কুয়ার ব্যাঙ সমুদ্রে পড়লে এরকমই লম্ফঝম্ফ করে! বয়সে প্রায় দ্বিগুণ বড় ‘চক্রবাক’ সংগঠনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সভাপতি দাদার সামনেও সিগারেট টানতাম। বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপানের বিষয়টিও গোপন করার প্রয়োজন বোধ করতাম না। আরেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে বলেছিলাম, ‘আপনাকে তো মনে হয় ভূষি মালের বস্তা।’ আরেকটা উদাহরণ দিলে নিজের দোষটা আরো পষ্ট হবে। ‘চক্রবাক’ অফিসের কাছে শহরের নিষিদ্ধ পল্লী ছিল। বেশ্যালয়ের পরিবেশ ও কাণ্ড-কীর্তি দেখার কৌতূহল নিয়ে এক সন্ধ্যায় জনৈক বন্ধুকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলাম অনেকক্ষণ। সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সন্ধ্যায় তোমাকে দেখলাম না, কোথায় ছিলে?’ হাসিমুখে সত্যি জবাব দিলাম। সভাপতি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। দেখার কৌতুহল মেটানো ছাড়া খারাপ কিছু করিনি, পকেটে অতো টাকাও ছিল না—নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও তিনি বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। পাঠক বন্ধুরা আমার বয়ানকে আশা করি শতভাগ সত্য জানবেন।
স্বাধীনতার পর প্রথম একুশে উদযাপন উপলক্ষে ‘চক্রবাক’ থেকে যে সংকলন বের হয়, সেখানে আমি একাধিক লেখা দেওয়ার পর একটাও ছাপা হয় না। কারণ ব্যাখ্যায় সম্পাদক জানান, লেখা মনোনীত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শহরের জাদরেল সাহিত্য-অধ্যাপককে। তিনি আমার কোনো লেখাই পছন্দ করেননি। বলার কিছু নেই। ততদিনে আমিও বুঝে গেছি, বড় লেখক হওয়া ছোট শহরে থেকে সম্ভব নয়। যে সংগঠনে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার কর্তাব্যক্তিদের সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় আগ্রহ বা গুণাবলী যেমনই থাক, সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যবোধ ছিল সামান্য। তাছাড়া দখলকৃত বাড়ি ও সংগঠনে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে তাদের যতটা প্রচেষ্টা, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের দায়টা তেমন আন্তরিক মনে হয়নি। শুধু কবিতা ছাপা না হওয়ার দুঃখে কি সংগঠন ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে গীবত গাইছি? মোটেই না। আমার জীবনে সংঘটিত ট্রাজিক ঘটনাটি বলার জন্যই ‘চক্রবাক’ নিয়ে এটুকু ভূমিকা করতে হলো। পরিবার থেকে পাকাপাকি বিচ্ছিন্ন ও পিতা কর্তৃক কার্যত ত্যাজ্যপুত্র হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছি শুরুতে। বাড়ি ছাড়ার পর, ‘চক্রবাক’ ও ছোট জেলা-শহর আমার বড় লেখক হওয়ার পক্ষে অনুকুল নয় বুঝে, শহরের সব বন্ধুকে শেষ বিদায় জানিয়ে বাহাত্তর সালেই রাজধানী ঢাকায় এসে দাঁড়াবার জায়গা খোঁজার সত্যি গল্পও বলেছি। এখন আবারও একা হওয়ার বাস্তবে আসি।
ঢাকায় এসে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কাজের অভিজ্ঞতা বছর চারেক পুরো না হতেই, প্রতিষ্ঠানটির কাজের সঙ্গে একাত্মতা বোধ বাড়ার বদলে তার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্কটি স্পষ্ট হতে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য বই জগতের উন্নয়ন হলেও, ব্যক্তিগত উন্নয়নটাই যেন সবার কাছে মূখ্য। স্বায়ত্ত্বশাসিত ছোট অফিস বলে পরিবেশটাও ছিল অনেকটা ‘চক্রবাক’ তথা বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মতো। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাউকেই স্যার ডাকতাম না। অপছন্দ করতাম যাদের, সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেও ভয় পেতাম না। ওই সময়ে নিজের রাজনৈতিক জ্ঞান অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। চোখে কোনো তত্ত্বের চশমা না লাগিয়েও পষ্ট দেখতে পেতাম, সমাজে একদল লুণ্ঠন ও শোষণ করছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠের দলটি শোষিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলাম শোষিত-লুণ্ঠিতদের দলে। অফিসে ওই সময়ে টাইপিষ্টকে মুদ্রাক্ষরিক বলা হত। মুদ্রাক্ষরিকের কাজ করার সময়ে দুনিয়ার মজুরের সঙ্গেও একাত্মতাবোধ এক ধরনের শক্তি জোগত। ব্যক্তিগত কাজ টাইপ করতে দিলে মুখের উপর না করে দিতাম কাউকে-বা, বিশেষ করে যাদের শোষক-লুটপাটকরীদের শাসনযন্ত্রের ধামাধরা অফিসরা মনে হতো। যাহোক, অফিসেও নিজের স্বভাবদোষে বেশ একা হতে লাগলাম।
অবশ্য দুনিয়ার মজদুরশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম থাকার আবেগটা একেবারে ভিত্তিহীন অবেগ ছিল না। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও, অফিসের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য আমাকে পছন্দ করত। তাদের নিয়ে গ্রন্থকেন্দ্রে রেজিস্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছিলাম, সেই ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু অফিস ইউনিয়ন-সংগঠনের রাজনীতি আমার ব্যক্তিগত পরিবার সংগঠনে কোনো সহায়তা করেনি। যারা সাহায্য করেছে, এবার তাদের কথায় আসি।
রবীন্দ্রনাথের ২২ বছর বয়সে বিয়ে করার ঘটনা নিজেকে প্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু তিনিও তো পছন্দমতো নিজের প্রেমিকাকে নয়, পারিবারিকভাবে অভিভাবকদের পছন্দমতো বিয়ে করেছিলেন। আমার পরিবার-প্রধান পিতার সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাতে তেমন আশা করতে পারি না। তারপরও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করতে ছোট ভাই সঞ্জুকে ঢাকায় এনে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলাম। দু’ভাই মিলে শাজাহানপুর এলাকায় একটা ঘর ভাড়া করে থাকি। এখানেও সমস্যা হলো, ব্যাচেলরদের কেউ বিশ্বাস করে না, বাসা ভাড়া দিতেও চায় না। অতএব সব মুশকিল আসানের জন্য পরিবার ও পরিবারের কেন্দ্রে বিপরীত লিঙ্গের উপযুক্ত জীবনসাথীর বিকল্প নেই। সংসারে থেকে সে বাস্তবে যা দিতে পারবে, শত প্রেমিকা চিঠিতে দুই মণ প্রেম দিয়েও কি তার পাশে দাঁড়াতে পারবে? কিন্তু সমস্যা হলো, তাকে খুঁজে পাই কোথায়?
যে কোনো ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা আমার মনের ব্যামো হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত জীবনসাথীর সনে সকল সংগ্রামে একাত্ম হতে নয় শুধু, বলা যায় একদেহে লীন হয়ে যাওয়ার কামনাতেও বড় অস্থির হয়ে উঠি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে ‘বিয়েপাগলা’ খেতাব পাইনি শুধু, কেউ-বা ‘ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল’ করে সত্যি-মিথ্যে সম্ভাব্য পাত্রীর মুলো ঝুলিয়ে আমার কাছে ঘুষ হিসেবে চা-নাস্তাও খেয়েছে বিস্তর। এভাবে মাস কয়েক চেষ্টা করে অবশেষে তার সন্ধান মিলল। শুরু হলো আমার জীবনের সবচেয়ে রোমঞ্চকর ও বেদনাদায়ক অধ্যায়টির।
রংপুরে ‘চক্রবাক’-এর এক কর্মী গোলাম কিবরিয়া খোকন ঢাকায় এসে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আর এক জন অচেনা কর্মী ঢাকায় কী এক চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এলে অফিসে পরিচয় হলো। তাকে বাসাতেও নিলাম। সে দু’ভাইয়ের গরিবি সংসারের আশু চাহিদাটি উপলব্ধি করে উপযুক্ত এক পাত্রীর সন্ধান দিল।মেয়েটি ‘চক্রবাক’-এর সঙ্গে জড়িত, গান শেখে, কবিতা-গল্পও লেখে। নাম ক [ছদ্মনাম]। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। দেখতেও ফর্সা-লম্বা, মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। চক্রবাকের কাছে আলমনগরেই নিজেদের বাড়ি। শহরে নিজেদের বাড়ি আছে শুনে ভয় পেয়ে বলি, এই মেয়ে তো আমার মতো গরিবের ঘরে আসতে চাইবে না। ঘটক মামা আশ্বাস দিয়ে বলে, স্টেশন-মাস্টার পিতা হঠাৎ মারা যাওয়ায় পরিবারটি এখন অভিভাবক শূন্য ও গরিবি দশায় আছে। বড় ভাই কোনোমতে একটা মুদিদোকান চালায়। আর বড় বোন মাস্টার্স করে সবে শহরের বাইরে একটা বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনায় ঢুকেছে। আমার যেমন ঢাকায় এসে স্বনির্ভর ও লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছিল, স্বনির্ভর হয়েই ছোট ভাইটিকেও মানুষ করার চেষ্টা করছি, আমার সম্ভাব্য জীবনসাথী ক-ও একই স্বপ্ন দেখছে—ঢাকায় এসে চাকরি করবে, কবিতা-গানও করবে, তারপর অভাবী পরিবারে অন্তত ছোটবোনকে সাহায্য করবে। সন্ধানদাতা জোর গলায় বলল, এটা হলে দুজনই উপযুক্ত জীবনসাথী পাবেন। ঘরেবাইরে লড়ার জোগ্য কমরেড হবেন দুজনই। এবং শুভ কাজটি ঘটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তার আত্মবিশ্বাস ষোলোআনা। বন্ধু খোকনও ক-কে চিনত, দূর-সম্পর্কিত ঘটক মামাকেও চেনে, সেও জোর সমর্থন দিল। আমি হবু-জীবনসাথীর জন্য বাস্তব অবস্থার পটভূমিতে নিজের স্বপ্ন-পরিকল্পনার সংবিধান তো আগেই রচনা করে রেখেছিলাম। সেই সংবিধানের কপি, ছবি ইত্যাদি ঘটক মামার হাতে দিয়ে ফলাফল জানার জন্য অস্থির অপেক্ষা করতে লাগলাম।
কিছুদিনের মধ্যে জবাব এলো। সবকিছু জেনে ও আমার ছবি দেখে এবং লেখা পড়ে মেয়ে সম্মত। ক তার ছবি ও হাতে লেখা কবিতাও পাঠিয়েছে। কবিতার চেয়ে হাতের লেখা সুন্দর। নাম জেনেই মন ডেকেছিল, আর ছবিটি দেখামাত্রই মন বলে উঠল—এই সেই মেয়ে, যার জন্য এতদিন তুমি অপেক্ষা করছো। চিঠি চালাচালিতেই কথাবার্তা মোটামুটি চূড়ান্ত হলো। আমি দেখতে যাবো, বাস্তব দেখাদেখির পর্ব শেষে সম্মতি দিলেই বিয়ে হবে এবং বিয়ের পরদিনই বউ নিয়ে ঢাকায় আসব। বিয়ের সামাজিকতার নামে বাজে খরচ কোনো পক্ষই করব না।বিয়ে করব বলে দু’রুমের একটা বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম। বউ দেশ থেকে শিগগির আসবে বলে ওয়াদাও করেছিলাম বাড়িঅলাকে। কলেজ ছুটি থাকায় আমার ছোটভাইটি তখন বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি নিজের ‘শুভ বিবাহ’ কারণ দেখিয়ে অফিসে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গেলাম রংপুরে।
‘চক্রবাক’ আমার দেখা স্টেশন রোডের সেই বিশাল বাড়িটি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। তবে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীনদের ধরপাকড় করে আলমনগরেই আর একটা ছোট পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ নিয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। পরিচিত নেতা-কর্মীদের অনেকেই চাকরি নিয়ে বা চাকরির ধান্ধায় কেটে পড়েছে। কিন্তু কর্ণধার সভাপতির কোথাও যাওয়ার বা করার কিছু নেই বলেই হয়তো, কিংবা হতে পারে সাংস্কৃতিক কাজের প্রতি তার নেশা ও নিষ্ঠার কারণেও, নতুন চক্রবাক অফিসে অবস্থান করে সংগঠনকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হলে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি আগেই জেনে গেছেন সব। সংগঠনের গানের ক্লাসে কিশোরী বোনকে নিয়ে এসেছিল সে। সভাপতি দাদাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার চোখের ভাষা তো হাজার ওয়াল্ট-পাওয়ার বাল্বের মতো উজ্জ্বল ছিলই, তার লাজুক চোখের ভাষাতেও সম্মতি বুঝলাম। কথা বলার আগে চার চোখের মিলনেই যেন বিয়েটা হয়েই গেল।
এরপর রাতেই মেয়ের বড়ভাই তুল্য এক অভিভাবক এলো পাত্র দেখতে। তাকে নামে ও চেহারায় চিনতাম। রংপুর বেতারে নিয়মিত গান করে, সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও শহরে পরিচিত, বাতেন সরকার নাম। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে বাড়িতে বেকার বসে আছেন। আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের পর রেস্টুরেন্টে বসে চা-সিগারেটের সঙ্গে বাতেন ভাইকে নিজের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, স্বপ্ন-পরিকল্পনা সবই মন খুলে বললাম। বুঝলাম, আমাকে তার পছন্দ হয়েছে এবং এ বিয়ে উভয়ের জন্য ভালো হবে বলে মত দিলেন। এরপর নিজের মতটি জানানোর জন্য সরাসরি চলে গেলেন মেয়ের বাড়িতে। রাতে ঘটক মামার ঘরে আমার থাকার আশ্রয় হলো। মেয়ের বাড়ি থেকে আসা হবু-জামাইকে আপ্যায়নের পোলাউ-কোর্মা ইত্যাদি সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে ক-এর হাতের রান্নাও ছিল দু’পদের, যা ঘটক মামা চিনিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ক-এর হাতের রান্নার স্বাদটাই বেশি ভালো লেগেছিল। ক আমার জন্য ধোপদুরস্ত বিছানা-বালিশও পাঠিয়েছিল। এসব তৃপ্তিদায়ক আচরণের পর, মেয়ের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমার জন্য অস্বস্তিকর একটা প্রস্তাব এল। বিবাহ যেহেতু একটি সামাজিক ব্যাপার, এবং আমার যেহেতু বাবা-মা জীবিত আর বাড়ি খুব দূরেও নয়, মুরব্বি-অভিভাবকের কেউ উপস্থিত না থাক, নিদেন পক্ষে তাদের মতটা নেওয়া জরুরি। তাদের কথাটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমি পড়লাম মহাফ্যাসাদে। ছোট ভাইটিকে ঢাকায় নেওয়ার পরও পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। কথাবার্তাও হয় না। বিয়ে করব বলে তার মতামতের ধার ধারিনি। কিন্তু আমার বাবা-মায়ের প্রতি মেয়েপক্ষের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে সম্মত না হয়ে উপায় রইল না। সিদ্ধান্ত হলো, আমি আগামীকাল বাড়িতে যাব। তার পরদিন মেয়ে পক্ষের বড়জোর জনা দশেক লোক আমাদের বাড়ি দেখতে যাবে। আমার পিতার মত নিয়েই চলে আসার পরদিনই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হবে এবং পরদিন নববধূ ক-কে নিয়ে আমি ঢাকায় যাব। ক-ও এরকম মত দিয়েছে জেনে বহুদিন পর গেলাম বাড়িতে।
বাড়িতে গেলেও পিতা আমাকে এড়িয়ে চলেন। মুখোমুখি কথাবার্তা হয় না। ছোট ভাইটির মাধ্যমে আমার ‘বিয়েপাগলা’ হওয়ার খবর চাউর হয়েছিল বাড়িতে। এবার নিজেই স্বজনদের সামনে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পাত্রী ঠিক করার কথা বলে আব্বার সম্মতি চাইলাম। তিনি মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে পাত্রীর বংশপরিচয়, আসল বাড়ি, ভাইয়ের কী ব্যবসা, বাড়িঘরের চেহারা কেমন—ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমি এসব খোঁজ নেওয়া জরুরি মনে করিনি। পিতা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত দিলেন, বিয়ে করাটা যখন এতই জরুরি, উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে আমি বিয়ে দেব ওর।
বাড়িতে গেলেও পিতা আমাকে এড়িয়ে চলেন। মুখোমুখি কথাবার্তা হয় না। ছোট ভাইটির মাধ্যমে আমার ‘বিয়েপাগলা’ হওয়ার খবর চাউর হয়েছিল বাড়িতে। এবার নিজেই স্বজনদের সামনে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পাত্রী ঠিক করার কথা বলে আব্বার সম্মতি চাইলাম। তিনি মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে পাত্রীর বংশপরিচয়, আসল বাড়ি, ভাইয়ের কী ব্যবসা, বাড়িঘরের চেহারা কেমন—ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমি এসব খোঁজ নেওয়া জরুরি মনে করিনি। পিতা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত দিলেন, বিয়ে করাটা যখন এতই জরুরি, উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে আমি বিয়ে দেব ওর। রাতেই পরিচিত ঘটককে ডেকে পাঠালেন। আমার পছন্দের মেয়ের ব্যাপারে তার আপত্তি দেখে আবার বিদ্রোহী হতে হলো। সামনে গিয়ে বললাম, ‘বিয়ে করব আমি, আর মেয়ে পছন্দ করে দেবেন আপনি? এটা কেমন কথা! এসব গ্রাম্য নিয়ম আমার জন্য খাটবে না। আমি তো কচি খোকা নই, সব দেখেশুনে মেয়ে পছন্দ করেছি। আমার বিয়েতে আপনার একটা টাকাও খরচ হবে না। কোনো মুরব্বিকেও থাকতে হবে না, কারণ বিয়ে করেই বউকে নিয়ে ঢাকা চলে যাব আমি। শুধু কালকে মেয়েপক্ষের লোকদের আপ্যায়ন করে মতটা দিলেই আপনার দায়িত্ব শেষ হবে।’
মা ও ছোট ভাই এবং আরো কিছু স্বজন পক্ষে থাকায় আব্বা মনে হয় নত হলেন। পরদিন মেয়েপক্ষের লোকজনদের আপ্যায়নে কোনো কার্পণ্য করেননি। মত দেননি শুধু, বেয়াই যেহেতু জীবিত নেই, বিয়ের পর তার বক্তব্য বেয়ানকে বলার জন্য একটি চিঠি লিখেও মেয়ের ভাইয়ের হাতে দিয়েছিলেন। আমার সম্পর্কে কী ক্ষোভ-দুঃখের কথা লেখা ছিল সে চিঠিতে জানি না। পরদিন গাঁয়ের ভাবীরা ঘটা করে বাড়িতে আমার গায়ে হলুদ দিল। গীত ও নাচে বাড়ি মাতালো প্রতিবেশী বুড়ি দাদি। তারপর বিকেলে ছোট ভাইসহ চারজন বারযাত্রী নিয়ে ট্রেনে চেপে শহরে গেলাম বিয়ে করতে।
কথা ছিল মেয়েপক্ষ স্টেশন থেকে বরকে রিসিভ করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কিন্তু কাউকে না দেখে, পায়ে হেঁটেই কাছাকাছি দূরত্বে গেলাম চক্রবাক অফিসে। সেখানে ঘটক মামা ও সভাপতি দাদাকেও পেয়ে গেলাম। তাদের মুখ ভার। ঘটক মামা নিজেও গতকাল আমাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের ভোজ খেয়ে সাফল্যের আনন্দ নিয়ে এসেছে। এখন কান্নাচাপা নতমুখ কেন? সংগঠনের সভাপতি দাদা জানালেন, ‘সবই ঠিক ছিল রে মঞ্জু, কিন্তু মেয়ের বড় বোন বাড়িতে এসে গোল বাধিয়েছে। ছেলের ছোট চাকরি, বেতন কম, লিনথিন দেখতে—এসব শুনে আপত্তি করছে সে।’ সভাপতি দাদা নিজেও তাদের বাড়িতে গিয়ে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু ওরা এখন রাজি না।
এমন ঘটতে পারে, ভুলেও ভাবিনি একবারও। জীবনের সেরা হোঁচটটি খেয়েও মনে হলো, কোথায় যেন একটা চক্রান্ত আছে। বললাম, ‘আমাকে মেয়ের বাড়িতে নিয়ে চলেন, আমি ক-এর সঙ্গে কথা বলব।’ সভাপতি বললেন, ‘আমি ক-কে ডেকেও কথা বলেছি, সে আগে মত দিয়েছিল, কিন্তু এখন রাজি না।’ তারপরও আমি সে বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে সভাপতি জানাল, মেয়েকে নিয়ে তার বড় বোন আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই তার কর্মস্থলের বাসায় চলে যাওয়ার কথা, এতক্ষণে চলে গেছে নিশ্চয়।
ঘটক মামা ও উপস্থিত আরো দু’একজন বিষণ্ন বদনে চুপচাপ। বরযাত্রীদের মধ্যে আমার ছোট ভাইটি সশব্দে কেঁদে উঠল প্রথম। তার কান্না সংক্রমিত হলো অন্যদের মাঝেও। কিন্তু বর যেন পাথর হয়ে গেছে। ঘটক মামা আমাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তার ঘরে নিয়ে গেল। যে ঘরে দুদিন আগেও জামাই-আদর ভোগ করে গেছি, বিয়ের আগেই যে মেয়ে তার সম্মতি বোঝাতে আমাকেই শুধু নিজের হাতের রান্না খাওয়ায়নি, বিয়ের পরদিনই আমার সঙ্গে ঢাকা যাবে বলে চক্রবাকের এক বন্ধুকে ঢাকার নতুন সংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েও বিয়েতে তার সম্মতি নিশ্চিত করেছিল। এখন রাত জেগে, হয়তো-বা সারা জীবনব্যাপে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক মেয়ের কাছে পাওয়া আঘাতের পরিমাণ আমাকে মাপতে হবে। বিয়েবাড়ির খাওয়ার বদলে কান্না নিয়ে ছোটভাইয়েরা একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি ঘুমাতে পারি না। জীবনের সমস্ত সুখস্বপ্ন-প্রেরণা-বিশ্বাস এক দমকায় উড়িয়ে দিয়ে কলিজা ছিন্নভিন্ন করা এমন ঝড়ের মুখে পড়িনি কখনো। এমন ঝড়ের মধ্যেও মনে হলো, বাড়িতে ফিরে পিতাকে মুখ দেখাতে পারবো না এ জীবনে। বাকি জীবনটা মদ খেয়ে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের চেয়েও করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। অথবা যে কোনো প্রকারেই হোক—বিশ্বাসঘাতক প্রতারক ক-কে খুন করতে হবে, তা হলে ফাঁসিকাঠে ঝোলার আগেও হয়তো-বা আত্মা কিছুটা শান্তি পাবে আমার। সারা রাত ঝড়ের দোলায় আকাশ-পাতাল দুলেও কোনো সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারলাম না।
পরদিন আমার চেনাজানা অনেকের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। ঘটনা জেনে তারা সহানুভূতি দেখায়, নাকি ‘বিয়ে পাগলা’ বরের উচিত শিক্ষা দেখে মজা পায়—বুঝতে পারি না। তবে বয়োজ্যাষ্ঠ বন্ধু বাতেন ভাই সকালে এসেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানান, গত রাতে সে এক জায়গায় নাটক মঞ্চায়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবে না, মেয়ের পরিবারে এ কথা জানিয়ে নিশ্চিত ছিল সে বিয়েটা রাতেই সম্পন্ন হবে এবং সকালে আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে আসবেন তিনি। কিন্তু আজ ভোরে সব ঘটনাই অবগত হয়েছে বাতেন ভাই। আমার হাত চেপে ধরে বললেন, ‘আপনি আজকের দিনটা আমাকে সময় দিন, ভাইদের নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করুন। দেখি আমি কী করতে পারি।’
বাতেন ভাইয়ের সহানুভূতি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ঘণ্টা তিনেক পর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন আমার পুরোনো হাই স্কুলের পাশের এক হোমিও দোকানে। স্কুলে পড়ার সময় এই দোকানের সমুখ দিয়ে স্কুলে যেতাম ও ভিতরে ডাক্তারি চেয়ারে বসা বুড়ো ডাক্তারটিকেও অনেক দেখেছি। একবার আমাশয় রোগে তার ঔষধ খাবো কিনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেও হোমিও অষুধের উপর আস্থা জাগাতে পারিনি। বাতেন ভাই আজ ভিতরে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বৃদ্ধ ডাক্তার তার পিতা। আমাকে দোকানে কিছুক্ষণ বসতে বলে কোথাও চলে গেলেন তিনি। বুড়ো ডাক্তার এবং পরে আরো এক অচেনা মুরব্বি আমার ইন্টারভিউ নিতে লাগল। ঘণ্টা খানেক সেখানে অবস্থানের পর আমি বরযাত্রী ছোট ভাইদের কাছে ফিরে গেলাম। হোটেলে নিয়ে খাওয়ালাম তাদের। বিকেলের মধ্যে শিল্পী বন্ধু বাতেন ফিরে এল আবার। সকাল থেকে ছোটাছুটি করে, মোটামুটি সব আয়োজন সম্পন্ন করে একান্তে সুখবরটি জানালেন আমাকে। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সত্যই আমাকে তার পছন্দ হয়েছে এবং আমার জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজনটাও যথাযথ উপলব্ধি করেছেন তিনি। ক তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী বান্ধবীর ছোটবোন, সে হিসেবে তারও ছোটবোন ছিল। তারা শেষ মুহূর্তে এমন অবাঞ্ছিত ব্যবহার করায় আমার মতোই দুঃখ পেয়েছেন তিনি। এই সংকট থেকে আমাকে উদ্ধারের জন্য বিকল্প পাত্রী ঠিক করে ফেলেছেন। পাত্রী আসলে তার আপন ভাগ্নী, নিজের মেয়েও বলা যায়। শহরের উপকণ্ঠে নিজেদের বাড়ি, পিতা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বোন-দুলাভাইকে বলে বাতেন ভাগ্নীকে নিজেদের বাড়িতে এনে শহরের স্কুলে পড়িয়েছেন। এখন বেগম রোকেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছে। আমি যেরকম জীবনসঙ্গী খুঁজছি এবং বন্ধুটি আমার প্রয়োজন যেরকম বুঝেছে, তাতে তার ভাগ্নী সাহেদা কোনো দিক দিয়েই আমার অযোগ্য হবে না। এখন সন্ধ্যায় দেখার পর আমি দেখেশুনে মত দিলে রাতেই বিয়ে হবে।
আমার দুঃসময়ে বন্ধুর আন্তরিক সহানুভূতি ও ছোটাছুটি দেখে, তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। বললাম, ‘মেয়েকে দেখার প্রয়োজন নেই। দেখতে সে যেমনই হোক, সব জেনেশুনে আপনার ভাগ্নীও যদি মত দিয়ে থাকে, তাহলে আপনাকেও এখনই মামা ডাকতে আমার আপত্তি নেই।’
সন্ধ্যার পর চক্রবাকের বেশ কিছু বন্ধু বরযাত্রী দলে যোগ দিল। মেয়ের নানা-বাড়িটিও আমার চেনা, কারণ স্কুলে পড়ার সময় এ মহল্লাতেও বছর কয়েক ছিলাম আমি। সন্ধ্যার পর তবু আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রী দেখানো হলো। বন্ধুরাই কথাবার্তা বলল। আমি দেখলেও মেয়ে চোখ তুলে আমাকে দেখেনি [তবে পরে স্বীকার করেছে সে, আমি বাথরুমে যাওয়ার সময় ঘরের ফুটো দিয়ে নিজের হবুস্বামীকে দেখার চেষ্টা করেছিল এবং আধামাধা দেখেছেও]। যাহোক, মেয়ে দেখার পর বিবাহের তাবৎ আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে সামাধা হলো। আমার বরযাত্রী ভাই-বন্ধুরা মহাতৃপ্তিতে বিয়ের খাওয়া খেতে লাগল।
প্রথম পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে অনিবার্য মিলনের মাঝখানে সহসা যে প্রচণ্ড স্বপ্ন-বিধ্বংসী ঝড় সামলে ভিতরের কান্নাকে চেপে রেখেছিলাম, তা নববধূকে একান্তে পাওয়ার আনন্দে চোখে উছলে উঠেছিল। চোখে কান্না নিয়ে বলেছিলাম, ‘মামার কাছে সবই তো শুনেছো, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে না তো? সুখে-দুঃখে আমার পাশে সারাজীবন থাকবে তো?’ সাহেদা ওরফে আমার সাজু ঘাড় দুলিয়ে এবং আমার হাত ধরেও সম্মতি দিয়েছিল। আমিও মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম, যে কোনো মূল্যে তাকে সুখী করার চেষ্টা করব এবং কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করব না তাকে।
বিবাহ-নাট্যের এ খবর ওদিকে গ্রামের বাড়িতেও আমার পিতা জেনে গেছে। কারণ মেয়ের নানাজি তার শিল্পী ছেলের উপর নির্ভর করে মত দেয়নি। গোপনে তারপরিচিত ও বিশ্বস্ত এক বন্ধুর বন্ধুর মাধ্যমে আমার চৌদ্দগোষ্ঠীর খবর জেনেছে এবং তার মত পাওয়ার পরই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিল। নানা-শ্বশুরের সেই বন্ধু ছিল আব্বারও বিশেষ পরিচিত। তার কাছেই সব জেনে বিয়ের পরদিনই আব্বা পুত্রবধূর জন্য শুভেচ্ছা-উপহারসহ আমাদের বংশের একজন মুরব্বিকে পাঠিয়েছিল শহরে। আমি খুব খুশি হইনি, কারণ এ ঘটনা তো পিতার কাছে আমার এক ধরনের পরাজয়ও ছিল।
বিয়ের পরদিন ছিল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্র জয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে বাতেন মামা গান করবেন। তার আমন্ত্রণে নববধূকে নিয়ে গেলাম সেই অনুষ্ঠানে। সেখানে ক-এর ছোট বোন পারুলকে দেখে চমকে উঠেছি। বেলা ও তার গোটা পরিবারকে সাজুও চিনত। পারুল জানাল, ক আজ বড় আপার সঙ্গে তার কলেজের বাসায় চলে গেছে। যাওয়ার আগে বাতেন ভাইকে দেওয়ার জন্য একটা চিঠি দিয়ে গেছে, সেই চিঠি দেওয়ার জন্য এসেছে সে। তার মানে আমি ক-কে বিয়ে করতে আসার দিন রাতে বাড়িতেই ছিল সে? প্রশ্নটা মনে জাগলেও ক, ক-এর চিঠি ও তার বোনকে নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতুহল দেখাইনি আর। মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠান দেখেছি। আয়োজকদের অনুরোধে মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আবৃত্তি করেছি। সন্দেহ নেই, শ্রোতাদের মধ্যে আমার সাজু সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল স্বামীর আবৃত্তি। কিন্তু অন্যদের মতো জোরে তালি বাজায়নি স্বভাবজাত লজ্জায়। পরদিন আমার নানা-শ্বশুর আমাদের যৌথসংসার ও জীবনসংগ্রামের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের দুজনের সঙ্গে ঢাকাযাত্রায় শরিক হয়েছিলেন।
মাসিক ১৪০ টাকা ভাড়ার দু’রুমের টিনের বাসাটির একটু বয়ান দেওয়া দরকার। ল্যাট্রিনটা বারোয়ারি হলেও গোসলের জন্য ছোট বাথরুম ছিল। বাসার দু’রুমে মেঝেতে পাতার উপযোগী দুটি গোটানো বিছানা। আমার বই কিংবা বানানো পোটলায় মাথা রেখে শোয়ার অভ্যাস ছিল, ফলে বিছানায় ভালো বালিশও ছিল না। ফার্নিচার বলতে একটা বাঁশের বুকসেল্ফ ও কিছু বই। রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় হাঁড়ি-পাতিল আর কেরোসিনের স্টোভ কিনেই সন্তুষ্ট ছিলাম। কাপড় রাখার জন্য ঝোলানো রশিই যথেষ্ট ছিল, একটা আলনা পর্যন্ত কেনার প্রয়োজন বোধ করিনি। পরিবার গড়তে ফ্রিজ-টিভি-ফার্নিচারের শৌখিনাতে স্বপ্নেও মাথায় ঘেঁষতে দেয়নি সত্য, কিন্তু সংসার চালাতে টুকিটাকি নানা জিনিস—যেমন শিলপাটা, মাছ-কাটার জন্য বটি, বাসন মাঁজার ছাই ইত্যাদি হাজারো তুচ্ছ ও দামী জিনিও অপরিহার্য, এসব সত্য ক্রমে স্ত্রীর কাছে মানতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু প্রথম ঢাকায় এসে নতুন সংসারের চেহারা দেখে নববধূ হতাশ হয়েছিল, নাকি আমার কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে খুশি হয়েছিল—সেই ভালো বলতে পারবে। তবে আমার রসিক নানাশ্বশুর হেসে মন্তব্য করেছিল, ‘সাহেদা, ফকিরের ঘরে বড় ঝোলা নিয়া আইলাম মনে হইতেছে।’ আমি হেসে উভয়কে বোঝাতে চেয়েছি, কষ্ট না করলে কৃষ্ণ মেলে? সংসারে সুখী হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মহব্বত আর বিশ্বাসটাই হলো আসল জিনিস। বড় হওয়ার জন্য ঘর ভরা দামি জিনিসপত্রের বদলে সিম্পল লিভিং আর হাই থট দরকার। এটা শুধু আমার কথা না নানাজি, মহানবী থেকে শুরু করে বিশ্বের বড় বড় লেখকরাও বইয়ে লিখে গেছেন। উদাহরণ দিয়েও দেখালাম, ঘরে দুটি চৌকি থাকলে ছোট্ট বাসায় কতটা জায়গা দখল করে রাখত। আর মেঝের বিছানাগুছিয়ে রাখলে দেখেন কতোটা খালি জায়গা পেয়ে যাচ্ছি।
নানাজি আমার পুঁথিপড়া বিদ্যা ও বাস্তবজ্ঞানকে তেমন আমল দিলেন না। পরদিন বাজার থেকে একটা সেমিখাট-আলনা ও আরো টুকিটাকি জিনিস কিনে এনেছিলেন। সংসারযাত্রায় নাতনিকে দু’চারদিন সহযোগিতা করে অশ্রুসিক্ত অফুরাণ দোয়ায় আমার পরিবার সংগঠনের ভিতটি পাকাপোক্ত করে দিয়ে বিদায় নিলেন। এভাবে, ১৯৭৬-এর ৭ মে যে দাম্পত্য যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে সুখে-দুঃখে দুজনে একাত্ম থেকে সামনে এগুনোর লড়াই এ লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বিয়ের ছয় বছরের মধ্যে দুজনের পরিবার-সংগঠনে আরো দুই সদস্য যোগ দিয়েছে। বয়সে শিশু হলে হবে কী, নিজেরা হাঁটা শেখার আগেই, সমস্ত প্রতিকুলতা ঠেকিয়ে সামনে এগিয়ে চলার জন্য সন্তানই বাবা-মায়ের ‘জীবন-ইঞ্জিনে’বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে। দু’সন্তানের মা-বাবা হওয়ার পর ওদের মানুষ করার লক্ষ্যটা আমাদের দুজনেরই প্রধান অঙ্গীকার হয়ে উঠেছিল। এর ফলে বড় লেখক হওয়ার যে লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা এসেছিলাম, তা দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিংবা বিসর্জন দিয়েছিলাম কি? না, এক দিনের জন্যও নয়। ছেচল্লিশ বছর নিজের সংসার বা পরিবার-সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ জোর গলায় এটুকু অন্তত দাবি করতে পারি, নানারকম কষ্ট ও বাধাবিঘ্নের মধ্যে দুজন মানুষের যৌথ অস্তিত্ব রক্ষার ভিতর দিয়ে যে বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্কটা তুলনামূলকভাবে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে সম্পর্কজাত সুখ তছনছ করতে ও সম্পর্কসেতু ভাঙার জন্য ভিতর থেকে, কখনো-বা বাইরে থেকে ছোটখাটো আঘাত, এমনকি বোমা-রকেট হামলার মতো বড় আঘাতও আসতেই পারে, সেই আঘাতে ভেঙে যায় বহু সম্পর্ক। সম্পর্কজাত সুখ ক্ষণস্থায়ী বা মিথ্যে হয়ে গেলেও ভাঙার বেদনা কিন্তু অনেকের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, ভোলা যায় না সহজে। বিয়ের পরও আমি যেমন ভুলতে পারিনি না-পাওয়া ক-কে।

ছেলে ও মেয়ের পক্ষের চার নাতির সঙ্গে সস্ত্রীক লেখক
প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় তাকে দেখে নেওয়ার শপথ করেছিলাম সেই ঝড়ের রাতেই। বিয়ের মাসাধিক কাল পর নতুন শ্বশুরবাড়ি গেলে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যও গোপনে একদিন সরাসরি তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দরজার কড়া নাড়লে দরজা খুলে অবাক হয়েছিল সে। স্বাগত জানিয়ে ঘরে বসিয়েছিল।
প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় তাকে দেখে নেওয়ার শপথ করেছিলাম সেই ঝড়ের রাতেই। বিয়ের মাসাধিক কাল পর নতুন শ্বশুরবাড়ি গেলে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যও গোপনে একদিন সরাসরি তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দরজার কড়া নাড়লে দরজা খুলে অবাক হয়েছিল সে। স্বাগত জানিয়ে ঘরে বসিয়েছিল। ভিতরে গিয়ে মা কিংবা অন্য অভিভাবকদের অনুমতি নিয়েই সম্ভবত, নিভৃত ঘরে বসে মুখোমুখি কথা শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে। বিয়েটা না হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী করেছিল সে ‘চক্রবাক’-এর সভাপতি দাদাকে এবং দ্বিতীয়ত আমাকেও। কারণ তার বড়বোন বাড়িতে এসে বর সম্পর্কে জানতে সভাপতি দাদাকে ডেকে তার মতামত জানতে চেয়েছিল। সভাপতি সত্যি কথাই বলেছিল। যেমন, ছেলেটি উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া টাইপের, ইচ্ছে করেই উচ্চশিক্ষা নেয়নি, নেশা-ভাং করত, ছোট চাকরি, বেতন কম, বাপে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল ইত্যদি। সভাপতি এরকম যদি বলে থাকে, মিথ্যে বলেনি অবশ্যই। কারণ নিজের সম্পর্কে লেখা স্বপ্ন-পরিকল্পনার সংবিধানে ক-এর কাছে আমি তো অযোগ্যতা বা দুর্বলতার দিকগুলি লুকাইনি। এগুলো থেকে মুক্ত হয়েই সুশৃঙ্খল জীবনে ফেরার জন্যই পরিবার সংগঠন ও জীবনসঙ্গীর সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছিল। ক-এর জবাব ছিল, আমার লেখা পড়ে আমার উপর তার বিশ্বাস জেগেছিল। কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর তার মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগেনি। কিন্তু সভাপতির কথা শুনে তার বড়বোন ও মায়ের মধ্যে স্বভাবতই দ্বিধা-ভয় জেগেছিল কিছুটা। ভালো করে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছিল তার বড় বোন। ক মা-বোন কি সভাপতি দাদার সামনে তাদের মতের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনি। তবে অপেক্ষায় ছিল বর তাদের বাড়িতে আসবে। আমি যেমন ক-কে বিয়ে করার জন্য নিজের পিতার মতের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলাম, তেমনি বরযাত্রী বাড়িতে উপস্থিত হলেই সে মা-বোনের বিরুদ্ধে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু সারারাত অপেক্ষার পরও বর বাড়িতে আসেনি। পরদিন আমার বিয়ের খবর শুনে প্রিয় বাতেন ভাইকে নিজের জীবন ধ্বংস হওয়ার দুঃখ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়ে বড় বোনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল সে।
আমি জানি না তার এ বিবৃতি কতটুকু সত্য। সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরও বিয়েটা না হওয়ার জন্য কে কতটা দায়ী—এ নিয়ে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করার চিন্তা দূরে থাক, নিজেও আর ভাবতে চাইনি। তবে তার চোখে কান্না দেখে দুর্বল হয়েছিলাম বোধহয়। সত্যই কি তবে সে আমাকে পছন্দ করে ভালবাসার জীবনসঙ্গী হতে চেয়েছিল? ভিতরের প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা ছাপিয়ে এই প্রশ্ন মনে বড় হয়ে উঠেছিল। আমার পকেটে তো সিগারেট-দেশলাই ছিলই। বাড়িটি যেহেতু টিনের কাঁচাবাড়ি, আগুন ধরিয়ে দিলে ভস্মীভূত হতে সময় লাগত না। কিন্তু তার বক্তব্যের সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্যই হয়তো, সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলাম—ঠিক আছে, সামাজিক সম্পর্ক নাই-বা হলো, আমরা অন্তত বন্ধু হতে পারি। সে আপত্তি করেনি, পত্রযোগাযোগর জন্য নিজ হাতে তার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিল।
এরপর ডাকযোগে পত্রবন্ধুত্বের সম্পর্কটা দ্রুতই নিবিড় হয়ে উঠেছিল। বাস্তবে দিতে পারেনি বলেই হয়তো, চিঠিতে যেন ভালবাসা উথলে উঠত দুজনেরই। আমাদের প্রথম সন্তান হওয়ার খবর শুনে তাকেও নিজের সন্তান দাবি করেছিল সে। বছর দুয়েক পরে ঢাকায় এসে এক আত্মীয়বাড়িতে উঠেছিল ক। উদ্দেশ্য একটা চাকরি জোগাড় করে স্বনির্ভর হবে। ঢাকায় থেকে লেখালেখি করবে। চিঠি হয়ে অনেকবার এসেছিল বলেই সশরীরেও একদিন এসেছিল আমার অফিসেও। স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে তাকে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। তার আত্মীয়বাড়িতে অবস্থানে সাময়িক কিছু সমস্যা হয়েছিল বলে আমাদের বাসাতেও কিছুদিনের জন্য মেহমান হিসেবে ছিল সে। ততদিনে খিলগাঁয় রেললাইনের ধারে দুই শত টাকা ভাড়ার বাসায় উঠে আমাদের সংসারের শ্রী-চেহারা কিছুটা উন্নত হয়েছিল।
ক-এর সব চিঠি না দেখালেও তাকে বন্ধু হিসেবে নেয়ার সত্যটি সাজুর কাছে গোপন করিনি। সহজ-সরল স্বভাবের মেয়ে সে, ভালবাসত বলে আমাকে বিশ্বাসও করত। তাছাড়া ক মামার ছোট বোন, আমার আগে থেকেই তাদের চেনাজানা। সমবয়সী পরিচিত ক-কে নিজ সংসারে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিতে দ্বিধা করেনি সে। বেডরুমে আমাদের দেড় বছরের শিশুপুত্রকে মাঝখানে নিয়ে তারা দু’বান্ধবী শোয়, অন্য ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে আমি একা।
একজন অভিভাবক ও ভাগ্যদেবতার কাছে আত্মসমর্পন করে আমার জীবনসাথী হয়েছে, অন্যজন আমাকে পছন্দ করেও চক্রান্তজালে আটকে পড়ে আমার সঙ্গে জোট বাঁধতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজ দুজনই আমার ঘরে। দুজনই আমাকে ভালোবাসে। দুজনের যৌথ ভালবাসা অনুভব করেও রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। ইসলাম ধর্মে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখার সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী কি স্বামীকে সমান ভালোবাসতে পারে? নাকি নারীকে নিছক শরীরী ভোগ্যপণ্য ভেবেই এরকম বিধান রাখা হয়েছে? কোনো পুরুষও কি সমানভাবে একাধিক নারীকে একসঙ্গে সমান ভালবাসতে পারে? সাজু ও ক—কাকে আমি বেশি ভালবাসি? ওদের দুজনের মধ্যে আমার জন্য কার ভালোবাসার ওজন বেশি? সমাজে সাধরণ মানুষের বিশ্বাস, জীবন, মৃত্যু, রেজেক, ধন-দৌলতের মতো বিয়ের ব্যাপারটাও আল্লাহর হুকুমেই ঘটে। এটাই কি তবে ধ্রুব সত্য? নাকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নায়োকোচিত গুণের অভাবই এরকম ট্রাজিক ঘটনার জন্য দায়ী? আমি তো ক-এর জন্য অপেক্ষা করিনি। এতকিছুর পরও, ভুল শোধরানোর জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তার পাশে গেলে সে আমাকে গ্রহণ করবে—চিঠিতে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে। কিন্তু নিরাপরাধ স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে হারানো প্রেমকে সত্য প্রমাণ করবে, কোনো প্রেমিক কি এমন অমানবিক হতে পারে, হওয়া উচিত? সমাজে অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার মতো আমাদের সামান্য জীবনের সুখ-শান্তি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই চক্রান্তকারী আসলে কে? এসব দার্শনিক জিজ্ঞাসা, বলা যায় আজাইরা ভাবনায় নির্ঘুম রাত কাটে আমার!
এভাবে কটা দিন কাটার পর, অফিস থেকে ফিরে একদিন দেখি, ক নেই। একেবারেই চলে গেছে তার সেই আত্মীয়বাড়িতে। আমার কাছে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। সহসা তার চলে যাওয়ার কারণটি জানাতে সাজু তার কঠোর অবস্থানটি জানিয়েছে, চিঠি লিখে তার স্বামীকে সবটুকু ভালবাসা দেওয়ার কী অধিকার আছে তার? এতই যদি ভালবাসা, আমাকে নিয়ে সংসার করুক সে, সন্তানকে নিয়ে সে চলে যাবে। এ কথা শুনে, ক বিদায় নেওয়ার সময় কথা দিয়েছে, আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না আমার সঙ্গে।
ক-কে না-পাওয়ার রাতে যেমন পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, সেরকম পাথর হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কী করার আছে? আমি সন্তানকে কোলে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছি। মিছে এক কাজের অজুহাত দেখিয়ে রাতে নির্জন ট্রেনলাইনের উপর গিয়ে একা বসে থেকেছি অনেকক্ষণ। টলস্টয়ের অ্যানা ক্যারানিনা ট্রেনের তলায় আত্মহত্যা করেছিল। রেললাইনের ধারে বাসা হওয়ায় এরকম দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যার খবর নিজেও শুনেছি। আত্মসংকট ও জীবনযন্ত্রণা কতটা গভীর হলে মানুষ ট্রেনের নিচে মাথা বিছিয়ে দিতেও ভয় পায় না? আমার জন্যও কি যন্ত্রণা মুক্তির এটাই মোক্ষম পথ? সংকটে ক-কে একটা চাকরি কি আশ্রয় দেওয়ার মতো বিন্দুমাত্র মুরদ নেই আমার। তার জন্য আমার বন্ধুত্ব-ভালোবাসার কী দাম? ত্যাগী স্ত্রী ও সন্তানের মুখ মনে পড়ে। বড় লেখক হওয়ার অপূর্ণ স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। রাতের ট্রেনগুলি আমার যন্ত্রণা-কষ্টের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে নির্বিঘ্নে চলে যায়। আমিও উঠে নিজের ঘরে ফিরি।
এভাবেই ক জীবন থেকে বিদায় হয়েছিল। তার সমস্ত চিঠি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি একদিন। আর কখনো লিখিনি তাকে। সেও লেখেনি। অতপর বিজয়ী স্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম থেকে পরিবারে সুখে-দুঃখে যৌথজীবন নির্বাহ করে চলেছি চার দশকের বেশি সময় ধরে। লেখাটা এরকম একটি বাক্য দিয়ে শেষ করা যেত, কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পেত না। বিয়ের পর পরই সাজু রংপুরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে একটা চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু সুখেদুঃখে আমার পাশে থাকবে বলে সেই চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছে। সারাজীবন স্বামীসেবা কম করেনি। সংস্কার বশে কখনো আমাকে নাম ধরে ডাকেনি সত্য, কিন্তু রেগে গিয়ে জন্তু-জানোয়ার বলতেও দ্বিধা করেনি। দীর্ঘ জীবনে কখনো মনে হয়েছে, তার কাছে সত্যিকার ভালবাসা পাইনি বলে ভিতরে আমার ভিতরে এত প্রেমতৃষ্ণা। তারও একইরকম অনুভ‚তি হয় বলেই হয়তো-বা আমার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছে অনেক সময়। কিন্তু অধিকতর ভালবাসা পাওয়ার বা দেওয়ার বিকল্প মানুষ আমরা দুজনের কেউ-ই পাইনি জীবনে। এ দেশে সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের সংসার এরকম জোড়াতালি দিয়েই চলে বোধহয়।
আমার বাসা থেকে বিদায় নেওয়ার বছর কয়েক পর অফিসের এক সহকর্মীর কাছে ক-এর খবর জেনে চমকে উঠেছিলাম। আমি যেমন টাইপ-সর্টহ্যান্ড শিখে চাকরিতে ঢুকেছিলাম, সেও সেরকম একটি চাকরি পেয়েছে বড় একটি সরকারি সংস্থায়। ঢাকাতেই আছে। অফিসের ঠিকানা পেয়ে একদিন গিয়েছিলাম দেখতে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল সে-ও। কুশলবার্তা জানিয়েছিল। বিয়ে করেছে অবশেষে। যে আত্মীয়বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়িরই কাজিন সম্পর্কিত একজন। একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। তার কন্যাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় বাসার ঠিকানা দিয়েছিল সে। কিন্তু আমার পুত্র-কন্যাকে দেখার আগ্রহ দেখায়নি।
বেশ কিছুদিন পর এক ছুটির দিনে গিয়েছিলাম ক-এর বাসায়। তার স্বামী বাসায় ছিল না। ঘরে বসিয়ে চা-নাস্তা খাইয়েছে। আমার পরিবারের কুশলাদিও জেনেছে। তিন/চার বছর বয়সী মেয়েটা আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। বিদায় দেওয়ার সময় মেয়েটি তার মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছিল, আর তার মা ক-এর চোখে ছিল ছলছলে অশ্রু। এ পৃথিবীতে সেটাই আমাদের শেষ দেখা।
২০০১ সালে শহরতলির বাড়ি ছেড়ে, আমরা যখন কলাবাগানের ভাড়া বাসায়, আমার মামাশ্বশুর বাতেন মামা এসেছিলেন সেই বাসায়। আমাদের বিয়ের বছর দুয়েক পর বিয়ে করেছিলেন তিনিও। শহরের একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ায় স্কুলের কাজে ঢাকা এলে বাসায় আসতেন। রংপুরে গেলে মামা-শ্বশুরের বাড়িটাই ছিল যেন প্রকৃত শ্বশুরবাড়ি, এত আন্তরিক আদর-যত্ন করতেন। ক সম্পর্কে কোনোদিনই একটি কথাও বলেননি আমাদের। আমিও জানতে চাইনি কিছু। সেইবার কলাবাগানের বাসায় এসে বিষণ্ন কণ্ঠে ভাগ্নীকে জানিয়েছিলেন খবরটা। ক আর নেই! হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ মারা গেছে।
সেই শোকসংবাদ শোনার পর গত একুশ বছরে কতো শোকবার্তা শুনে বিয়োগ-ব্যথায় বুক ক্রমে ভারী হয়ে উঠছে! ১৯৭৬-এর ৬ ও ৭ মে আমার বিয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন যারা, আমার বাবা, মা, ছোটভাই, বিয়ের ঘটক, সপরিবার বাতেন মামা, শুভাকাঙ্ক্ষী, কি চক্রান্তকারী কেউই আর বেঁচে নেই। তারপরও হৃদয় খুড়ে সেই বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতিচারণ করছি কেন? ইচ্ছে ছিল, নিজের পরিবার-সংগঠনে ট্রাজিক-নাটকীয় ঘটনার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এমন একটি গভীর প্রেমের উপন্যাস লিখব, যেখানে অনেক দার্শনিক জিজ্ঞাসারও জবাব খুঁজব। ‘দাম্পত্য বিলাস’ নামের একটি উপন্যাস সাজুকে উৎসর্গ করে লিখেছিলাম ‘যে তুমি সঙ্গে আছো ছায়ার মতো’, আর আত্মজৈবনিক ট্রাজিক প্রেমের উপন্যাসটি লেখা হলে ক-এর নামে উৎসর্গ করে লিখব, ‘যে তুমি হারিয়ে গিয়েও জেগে থাকো অপার বেদনায়’। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই লেখা শুরু করতে পারিনি। লেখার জন্য সেই গভীর ক্ষত অন্তহীন বেদনা-স্রোতে জাগাবার ভয়েই হয়তো। নিজেরও যেহেতু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে, উপন্যাসটি লেখার আগেই সহসা শেষ বিদায়ের আশঙ্কা থেকেই বোধহয়, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লেখার মতো আত্মকথার এ বইতে ঠাঁই দিলাম তাকেও।*
► লেখাটি লেখকের প্রকাশিতব্য স্মৃতিকথামূলক বই ‘পথে নেমে পথ খোঁজা’য় অন্তর্ভূক্ত হবে।




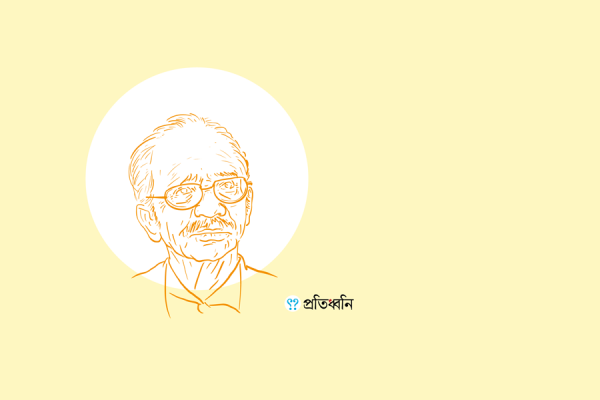

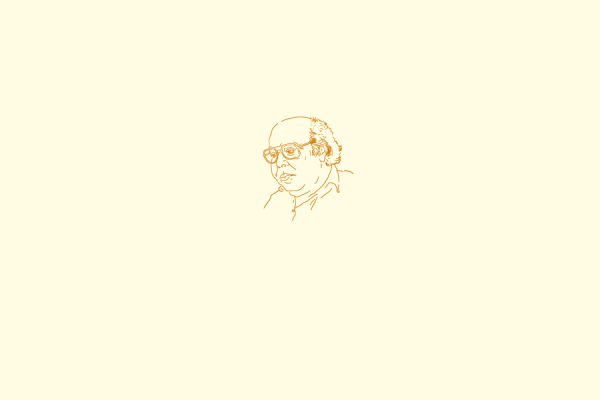
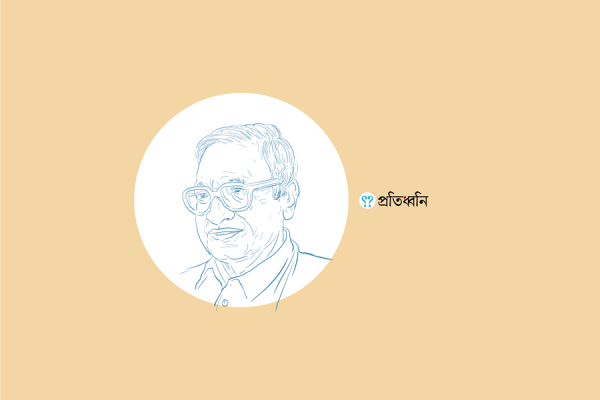

আপনার মন্তব্য প্রদান করুন