ঔপন্যাসিক স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচের নোবেল বক্তৃতা
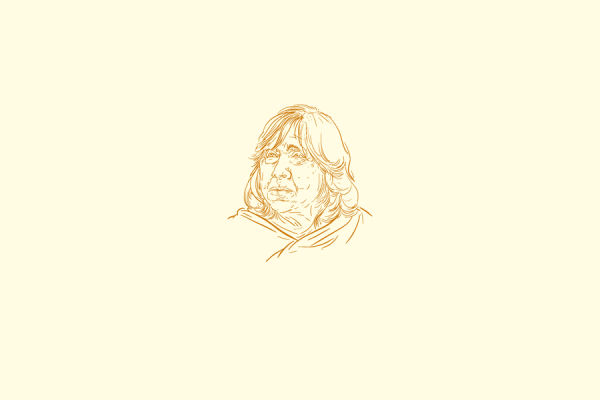
স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ
স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ ১৯৪৮ সালে ইউক্রেনে জন্মগ্রহণ করেন। বেলারুশিয়ান বাবা ও ইউক্রেনিয়ান মায়ের সাম্যবাদী আদর্শে বেড়ে উঠেন তিনি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালে মিনিস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পড়াশোনা শেষে তিনি প্রথমে শিক্ষকতা ও পরবর্তীকালে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন।
তার বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতামতের জন্য অধ্যয়ন শেষে তাকে পোলিশ বর্ডারের পাশে একটা আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকাতে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তিনি মিনিস্কে ফিরে আসেন এবং সেল’সকাঝা গেজেট পত্রিকাতে চাকরি নেন। প্রথম গ্রন্থ “ওয়ার’স আনওমেনলি ফেইস”(১৯৮৫); দীর্ঘদিন ধরে বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করা শতশত নারীর সাক্ষাৎকারের সম্মিলনে এই বই লেখা হয়েছিল। আরেকটি অনবদ্য বই “ভয়েজেস অব ইউটোপিয়া”তে তিনি সোভিয়েত জীবনকে বহু ব্যক্তির বহু স্বরে বয়ান করেছেন।
স্ভেতলানা ইতিহাস থেকে রসদ সংগ্রহ করে কাহিনী সৃষ্টির এক অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সাহিত্য শৈলী অবলম্বন করেছেন। একই ঘটনা সংশ্লিষ্ট বহু মানুষের সাক্ষ্য থেকে বহু স্বরের সমাবেশের মাধ্যমে একটা সম্পূর্ণ যুগ, কখনো কখনো একটা পুরো শতাব্দীকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন। ১৯৯৭ সালে রচিত “ভয়েজেস ফ্রম চেরনোবিল” বইটি ১৯৮৬ সালের পারমাণবিক দুর্যোগের ভয়ংকর প্রভাব নিয়ে লেখা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাঝে মিথ্যা চেতনা কি করে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে তার এক অকাট্য দলিল এই বইটি।
১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সাল পযর্ন্ত চলমান সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা “জিংঙ্কি বয়স- সোভিয়েত ভয়েস ফ্রম এ ফরগটন ওয়ার” (১৯৯০) তথ্য সাহিত্যের ধারায় একটি অভিনব সংযোজন। চলমান ঘটনা ইতিহাস হওয়ার পূর্বেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখার এক অনন্য পদ্ধতি। এই গ্রন্থ সমাজতন্ত্রের বিপথগামীতা ও অসারতার অনুলিপি। ২০১৩ সালে রচিত “সেকেন্ড-হ্যান্ড টাইম: দ্য ডিমাইজ অব রেড (ও) ম্যান” তার “ভয়েজেস অব ইউটোপিয়া” থিমের আরেকটি সংযোজন।
তার সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম দুটি অনুপ্রেরণার একটি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নার্স ও নারী সৈনিক সোফিয়া ফেদোরচঙ্কোর (১৮৮৮-১৯৫৯) নোটবুক। আরেকজন হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেলারুশিয়ান লেখক আলেস আদামোভিচের (১৯২৭-১৯৯৪) প্রামাণ্য প্রতিবেদন। সোভিয়েত শাসনের কঠোর সমালোচনা করার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে—কখনো ইতালি ও ফ্রান্স, কখনো জার্মান ও সুইডেনে ছিলেন।
প্রামাণ্য উপন্যাস লিখন শৈলীর ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবেদন ও কল্পকাহিনীর ব্যবধানকে অনেকটাই মিলিয়ে দিয়েছেন। তার লেখায় বহুস্বরের বয়ান প্রস্ফুটিত হয়। মানব যাতনা, চেতনা ও সাহসিকতার স্তম্ভ হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে তিনি এক অনন্য নজির। ২০১৫ সালে সাহিত্য সৃষ্টির অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
|| সম্পাদকীয় নোট ||
বেলারুশিয়ান ঔপন্যাসিক স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ পরাজিত যুদ্ধের প্রান্তর থেকে শিরোনামের বক্তৃতাটি দেন নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশানের অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান প্রতিধ্বনি পত্রিকাকে বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশের কপিরাইট প্রদান করেছে। আমরা নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান ও স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। প্রতিধ্বনির জন্য এটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও সমালোচক পলাশ মাহমুদ।
স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচের নোবেল বক্তৃতা || পরাজিত যুদ্ধের প্রান্তর থেকে
আজকে এই বিশ্ব মঞ্চে আমি একা দাঁড়িয়ে নেই...
শতশত স্বর আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তারা সবসময়ই আমার সাথেই আছে। বলা যায় সেই ছেলেবেলা থেকেই আছে। আমি সম্পূর্ণ গ্রামের আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছি। আমার খেলার সঙ্গীদের সাথে সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতাম আর সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরে আসতাম। গ্রাম্য নারীরা তাদের ছোট ছোট কুটিরের পাশের ব্যাঞ্চে বসে গল্প করতো আর তাদের ক্লান্ত কণ্ঠের আওয়াজ আমাদের চুম্বকের মতো টানতো। তাদের করোরেই বাবা, স্বামী এমনকি কোন সন্তানও ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের গ্রামে কোন পুরুষ বাস করতো বলে আমার মনে পড়ে না। মহাযুদ্ধের সময় প্রতি চারজন মধ্যে একজন বেলারুশিয়ান উধাও হয়ে গেছে। হয় যুদ্ধের ময়দানে নয় তো দলীয় কোন্দলের কবলে পড়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে নাই হয়ে গেছে। যুদ্ধের পর আমরা সব বাচ্চারা পুরুষশূন্য এক নারীর জগতে বেড়ে উঠেছি। আমার যতোটুকু মনে পড়ে। নারীরা মৃত্যু চেয়ে ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতো বেশি। যুদ্ধে যাওয়ার দিনগুলোতে নারীরা তাদের শখের পুরুষদের কি বলে বিদায় জানাতো তার স্মৃতিচারণ করতো। তাদের ফিরে আসার দীর্ঘ অপেক্ষার দিনগুলোর কথা বলতো। তখনও তারা কি পাষানে বুক বেঁধে অপেক্ষায় ছিল তার গল্প বলতো। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল তবু তারা এক বুক আশা নিয়ে অপেক্ষা করে যাচ্ছিল। “ওর যদি একটা হাত না থাকে, ওর যদি দুটি পা হারিয়ে ফেলে, আমি তবুও কোন পরোয়া করি না, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই, আমার নিজের কাধে ওকে নিয়ে বয়ে বেড়াবো, তবু ও ফিরে আসুক।” একটা মানুষের হাত থাকবে না, পা থাকবে না, তবুও কেউ একজন তাকে ছেড়ে যাবে না, এই ঘটনাটা আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসা আসলে কি...
শৈশবে শোনা সেই সব পথের পাঁচালীর কিছু বেদনার সুর বলে যাই...
প্রথম স্বর:
“তুমি কেন সবকিছু জানতে চাচ্ছো? এটা খুবই বিষাদ ভরা গল্প। যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে আমার জীবন সঙ্গীর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি সেনা ট্যাংকের ক্রু হিসাবে বার্লিনের পথে ছিলাম। আমার মনে আছে, আমরা রাইখস্ট্যাগের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর সাথে তখনও আমার বিয়ে হয়নি। একদিন আমার কাছে এসে বললো, ‘চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি। আমি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।’ আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমরা পুরো যুদ্ধের সময়টাতে নোংরা, আবর্জনা ও রক্তের মাঝে বসবাস করছিলাম। গালাগালি ও কটুবাক্য ছাড়া কিছু শুনতে পেতাম না। আমি বললাম, ‘এই সৈনিক পোশাক ছেড়ে প্রথমে আমাকে আবার নারী হয়ে উঠার সময় দাও। কিছু ফুল নিবেদন করো। প্রেমের কিছু মধুর গুঞ্জন কানে কানে বলো। যুদ্ধ শেষে আমি আমার জন্য একটা ফুলেল পোশাক বানাবো।’ আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। মনে হলো ওকে জোরে একটা ঘুষি দেই। সেও যেন সব বুঝতে পারছিল। তার একটা গাল খুব মারাত্মকভাবে পোড়া ছিল। ক্ষতটা পুরোটা গালে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার কথা শুনে ওর চোখ থেকে নোনা জলের ধারা পোড়া ক্ষতটা বেয়ে নেমে আসচ্ছিল। এটা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমি বলে ফেললাম, ‘ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো।’ আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়েছে। আমাদের চারপাশে তখন ছাই আর চূর্ণ-বিচূর্ণ ইট পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা যুদ্ধের মাঝে ছিলাম।”
দ্বিতীয় স্বর:
আমরা চেরনোবিল পারমাণবিক কারখানার কাছেই থাকতাম। আমি একটা রুটির দোকানে কাজ করতাম। মিষ্টি পিঠা বানাতাম। আমার স্বামী ছিলো একজন দমকল কর্মী। বেশিদিন হয়নি আমরা বিয়ে করেছি। বাজারে গেলেও আমরা একজন আরেকজনের হাত ধরেই রাখতাম। এতোটা প্রেমে আমরা ডুবে ছিলাম। যেদিন পারমাণবিক চুল্লির বিস্ফোরণ হলো সেদিন আমার স্বামী অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রে দায়িত্বরত ছিলো। তারা প্রাত্যহিক দিনের বাসায় পরার শার্ট গায়ে দিয়েই আগুন নেভাতে গিয়েছিল। ভাবতে পারেন পারমাণবিক কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছিল কিন্ত কোন অগ্নিরোধক পোশাক সরবরহ করা হয়নি। আমাদের বেঁচে থাকাটা এমনই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। জেনে অবাক হবেন ওরা সারাটা রাত ধরে আগুন নিভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো। জীবনের জন্য অসহ্যনীয় প্রাণসংহারী শ্বাসরূদ্ধকর রশ্মি গ্রহণ করচ্ছিল রাতভর। পরেরদিন সকালে তারা সোজা মস্কোর উদ্দেশ্যে উড়াল দিয়েছিল। তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণে কেউ অসুস্থ হলে কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচার আশা থাকে না। আমার প্রিয় স্বামীর প্রাণশক্তি বেশি ছিলো, একজন খেলোয়াড় ছিলো তো যার কারণে সে হয়তো কিছু বেশি দিন বেঁচে ছিল। সবার শেষে পৃথিবী ছেড়েছে। আমি যখন মস্কো গেলাম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালো ওকে একটা বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন কক্ষে রাখা হয়েছে। বাইরের কেউ ওই কক্ষে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। আমি দু’হাত জোড় করে মিনতি করে বললাম, ‘কিন্তু আমি যে ওকে ভালোবাসি। শুধু একবার এক পলক দেখতে চাই।’ ওরা বললো, ‘আপনার যাওয়ার দরকার নাই। সৈন্যরা উনার সেবা করছে।’ আমি বললাম, ‘কিন্তু আমি ওকে আমার প্রানের থেকেও বেশি ভালোবাসি।’ ওরা আমাকে ধমক দিয়ে বললো, ‘আপনি যে মানুষটাকে ভালোবাসতেন তিনি আর আগের মানুষ নেই। তিনি অনেকটা জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছেন যাকে সংক্রমণ মুক্ত করতে হবে। আপনি কি বুঝতে পাচ্ছেন?’ ওদের কোন কথাই যেন আমার কান দিয়ে ঢুকছিল না। আমি সেই একই কথা বার বার চিৎকার করে বলে যাচ্ছিলাম: আমি ভালোবাসি, আমি অনেক অনেক ভালোবাসি... শুধু একবার ওকে দেখার জন্য আমি গভীর রাতে অগ্নি-নির্গমনের পথ বেয়ে উপরে উঠে যেতাম... মাঝে মাঝে রাতের প্রহরীকে অনুরোধ করতাম... এমনকি তাদের কিছু অর্থ ঘুষ দিতাম যেন আমাকে যেতে দেয়... এতো কিছুর পরও ওকে আমি ছেড়ে যাইনি। ওর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি ওর সাথেই ছিলাম। ও মারা যাওয়ার কয়েক মাস পর আমি একটা কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলাম। কিন্তু হায়! বাচ্চাটি মাত্র কয়েক দিন বেঁচে ছিল। হায়! আমার মেয়েটি... আমরা দুজনে এই বাচ্চাটার জন্ম নিয়ে অধীর ছিলাম। আবেগ তাড়িত ছিলাম। সেই আমিই কি না শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেললাম... এখন আমি জানি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল। আমার গর্ভে থেকে আমার বদলে ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি শুষে নিয়েছিল। ও খুব ছোট ছিল… খুবই খুঁদে... পুঁচকে একটা মেয়ে... কিন্তু আমি তো বাবা আর মেয়ে দুজনকেই খুব ভালোবাসতাম। তুমি কি কখনো ভালোবাসা দিয়ে কাউকে মেরে ফেলতে পারো? মৃত্যু ও ভালোবাসা এতো মিলেমিশে থাকে কেন? জীবনে তারা হাত ধরাধরি করে একসাথে আসে কেন? কেউ কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে? সমাধির সামনে দাঁড়ালে আমার হাটু ভেঙে আসে... মাথা নিচু হয়ে যায়...
তৃতীয় স্বর:
“প্রথম যখন আমি একজন জার্মানকে হত্যা করলাম... আমার বয়স তখন মাত্র দশ। দলীয় আনুগত্য আমাকে সমর অভিযানে যেতে বাধ্য করেছিল। ওই জার্মান সৈন্যটা আহত হয়ে খোলা মাঠে পড়েছিল। আমাকে বলা হলো আমি যেন তার পিস্তলটা নিয়ে আসি। আমি দৌড়ে গেলাম। তার দুই হাতের মুষ্ঠিতে পিস্তলটা শক্ত করে ধরা ছিল। ঠিক আমার মুখের দিকে তাক করে রেখেছিল। কিন্তু ও গুলি ছোড়ার আগেই আমি গুলি করে ওকে মেরে ফেললাম।
কাউকে হত্যা করতে আমি মোটেই ভয় পেতাম না। যুদ্ধের সময় এটা নিয়ে আমি তেমন করে ভাবিও নাই। অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছিল। আমরা মৃতদের ভীড়েই বাস করছিলাম। অনেক অনেক বছর পর, একদিন আমি ওই জার্মান সৈন্যটাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। এই বিষয়টা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাত দেখার মতো... ওই একই স্বপ্ন আমি দিনের পর দিন বারবার দেখতে লাগলাম... আমি আকাশে উড়ে যেতে চাইছি... জার্মানটা আমাকে আটকে রাখছে... আমি লাফিয়ে শূন্যে উঠছি... উড়ে যাচ্ছি... উড়ে যাচ্ছি... ও আমাকে ধরে ফেলছে... আমি ওর সাথে মাটির দিকে পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি... আমি কোন একটা অন্ধ কূপে পড়ে যাচ্ছি... আমি উঠে দাড়াতে চাচ্ছি... ও আমাকে উঠতেই দিচ্ছে না... ওর জন্য আমি উড়তেই পারছি না...
এই একই স্বপ্ন... আমাকে যুগের পর যুগ তাড়া করেছে...
আমি আমার ছেলেকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি। ও অনেক ছোট ছিল তাই বলিনি। তার বদলে আমি ওকে রূপকথার গল্প শুনাতাম। আমার ছেলেটা এখন অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু এখনও আমি তাকে আমার দুঃস্বপ্নের কথা বলতে পারি না।”
ফ্লবেয়ার নিজেকে সবসময় ‘মানব-কলম’ বলতেন। একইভাবে আমি নিজেকে ‘মানব-কান’ বলতে চাই। আমি যখনই কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই তখনই কোন না কোন একটা শব্দ, কিছু শব্দগুচ্ছ, অনেক অনেক বিস্ময়বোধক ধ্বনি কুড়িয়ে নিয়ে আসি। আমি সবসময়ই ভাবি—কোন চিহ্ন ছাড়া কতো কতো মানব আখ্যান পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কালের অন্ধ গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মানুষের কথ্য কাহিনির এই দিকটা সাহিত্যে পুরোপুরি তুলে আনতে পারে নাই। আমরা এটাকে প্রশংসা করি না আবার এটা নিয়ে চমকিত হই না কিংবা আনন্দিতও হই না। কিন্তু আমাকে এটা খুব আকর্ষণ করে। আমাকে মুগ্ধতার শিকলে বন্দী করে রাখে। মানুষের কথার বলার প্রক্রিয়াটা আমি খুব পছন্দ করি... মানুষের নির্জন, নিঃসঙ্গ কথার স্বর শুনতে আমি খুব ভালোবাসি। এটা আমার সবচেয়ে বড় আবেগ, অনুরাগ ও উচ্ছ্বাসের জায়গা।
আজকে এই মঞ্চে পৌঁছানোর পথটা অনেক দীর্ঘ ছিল-প্রায় চল্লিশ বছর হবে। মানুষ থেকে মানুষের কাছে যেতে হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের কথা শুনতে হয়েছে। আমি দাবি করবো না যে প্রথম থেকেই আমি এই পথের পথিক ছিলাম। এমনও অনেক সময় গেছে যখন আমি মানুষের আচরণে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি যেমন পুলকিত হয়েছি তেমনি বিষাদেও ভুগেছি। মাঝে মাঝে আমি জীবনে যা শুনেছি, যা জেনেছি তার সবকিছু ভুলে যেতে চেয়েছি। এমন এক সময়ে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম যে সময়টায় আমি অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিলাম। একই সাথে জীবনে অনেকবার আমি মানুষের মহিমাকে অবলোকন করেছিলাম আর প্রাণভরে কাঁদতে চেয়েছিলাম।
আমি এমন এক দেশে জন্মেছি যেখানে ছেলেবেলা থেকে আমাদের মৃত্যুকে বরন করতে শেখানো হয়। আমাদের মৃত্যু কি জিনিস শেখানো হয়। আমাদের শেখানো হয় মানুষ জন্মেছে তার সকল কিছু ত্যাগ করার জন্য। সবকিছু নিঃশেষ করে তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। আমাদের শেখানো হয়েছিল মানুষকে মন দিয়ে নয় অস্ত্র দিয়ে ভালোবাসতে হবে। আমি যদি অন্য কোন দেশে জন্ম নিতাম তাহলে হয়তো এই নিষ্ঠুর পথে হাঁটতে হতো না। অশুভ শক্তি খুবই নির্মম। এর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রতিষেধক নিতে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত শিকার ও শিকারীর সমাবেশে বাস করে আসচ্ছি। যদিও আমাদের পিতা মাতারা অবিরাম এই ত্রাসের ভেতর বাস করে আসছিল। কিন্তু তারা কখনোই আমাদের এই বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলেনি। আমাদের জীবনের বাতাস বিষাক্ত হয়ে ছিল। অশুভ শক্তি আমাদের উপর সবসময় সজাগ চোখে তাকিয়ে ছিল।
আমি এই পর্যন্ত পাঁচটি বই লিখেছি। কিন্তু আমি মনে করি তারা সব মিলিয়ে একটি বই। আদর্শ জগতের ইতিহাস নামে একটি বই।
ভারলাম শালামভ একবার বলেছিলেন, ‘মানবতার প্রকৃত পুর্নজন্মের লক্ষে আমি এক মহাযুদ্ধের অংশীদার । এক পরাজিত যুদ্ধ।’ আমি ওই মহাযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছি। এই যুদ্ধের জয় ও পরাজয়ের ইতিহাস নতুন করে লিখতে চেয়েছি। বসুন্ধরার বুকে মানুষ কি করে স্বর্গরাজ্য বানাতে চেয়েছে তার মহাইতিহাস। পৃথিবীকে একটা স্বর্গ! একটা সূর্যনগর বানাতে চেয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্তের সমুদ্র ছাড়া আর কিছু কি অবশিষ্ট ছিল? এই জগৎ মানুষের নষ্ট জীবনের হাহাকারে ভরা। এমন এক সময় ছিলো যখন বিংশ শতাব্দীর কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ সাম্যবাদের তুলনায় নগন্য ছিল (অক্টোবর বিপ্লব ও এর প্রতীকগুলো)। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী এবং সারাবিশ্বের সাধারণ মানুষকে সাম্যবাদের চেয়ে অধিক অন্য কোন রাজনৈতিক মতবাদ এতোটা গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে নাই। রেইমন্ড অ্যারন মনে করতেন রুশ বিপ্লব হলো ‘বুদ্ধিজীবীদের আফিম’। কিন্তু সাম্যবাদের ধারণাটা প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো। আমরা একে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বক্তৃতায় খুঁজে পাবো। এরেস্টোফেনেসের সময় সম্পর্কে স্বপ্নে খুঁজে পাবো যেখানে ‘জগতের সবকিছুতে সবার মালিকানা’ থাকবে। টমাস মুর ও টমাসো কম্পানেল্লা... পরবর্তীতে সেইন্ট-সিমোন, ফারিয়ার এবং রবার্ট ওয়েনের লেখাতেও সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। রুশ অন্তরাত্মায় এমন এক প্রানশক্তি ছিলো যা সাম্যবাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারতো।
বিশ বছর আগের একদিন। আমরা চোখ ভরা জলে অভিশাপ দিতে দিতে এই সোভিয়েত ‘লাল সাম্রাজ্য’কে বিদায় জানিয়ে ছিলাম। এখন অতীতকে ইতিহাসের নিরীক্ষাক্ষেত্র হিসাবে আরো স্পষ্ট ভাবে দেখতে পারি। কারণ সমাজতন্ত্রের বাহাস এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। নতুন প্রজন্ম এক নতুন বিশ্বের ছবি নিয়ে আবিভূত হচ্ছে। অনেকেই নতুন করে মার্ক্স ও লেনিনের পাঠ শুরু করছে। রাশিয়ার শহরে শহরে স্ট্যালিনের নতুন নতুন জাদুঘর তৈরি হচ্ছে। স্ট্যালিনের নতুন নতুন ভাস্কর্য নির্মিত হচ্ছে।
‘লাল সাম্রাজ্য’ হয়তো আর নেই কিন্তু ‘লাল মানুষ’, অন্যভাবে বললে—‘হোমো সোভিয়েতকাস’ রয়ে গেছে। সে সবসময়ই থেকে যাবে।
আমার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন। তিনি তার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কার্ডটা রেখে দিয়েছিলেন। আমি ‘সভোক’ শব্দটি কখনোই ব্যবহার করতে চাই না। সোভিয়েত মানসিকতার জন্য নির্ধারিত এমন অবমাননাকর উপাধি ব্যবহারে আমি ঘোর বিরোধী। তাহলে দেখা যাবে এই শব্দটা আমার বাবার বেলায় ব্যবহার করতে হচ্ছে কিংবা আমার বন্ধুর মতো কাছের মানুষকে এই নামে ডাকতে হবে, যা আমি কখনোই চাই না। কারণ তারা সবাই ওই এক সমাজতন্ত্র থেকে উৎসারিত। এদের মধ্যে অনেকেই আপাদমস্তক ভাববাদী। বলা যায় কল্পপ্রিয় ধারার। আজকের দিনে এদের ‘রোমান্টিকসের দাস’ নামে ডাকা হচ্ছে। আদর্শ রাষ্ট্রের দাসও বলা যায়। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, তারা চাইলে অন্য রকম এক জীবন কাটাতে পারতো কিন্তু তারা সোভিয়েত জীবনকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজে আসছি। সেই সময়ের সোভিয়েত নামক বিশাল দেশটার আনাচে কানাচে আমি দুরন্ত পথিকের মতো ঘুরে বেরিয়েছি। হাজার হাজার লোকের জবানবন্দি নিয়েছি। এটা ছিল সমাজতন্ত্র আর এটাই ছিল আমাদের জীবন। আমি একটু একটু করে সমাজতন্ত্রের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা ‘অন্দরমহলের’, ‘গার্হস্থ্যের’ ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। মানুষের অন্তর-আত্মায় সাম্যবাদ কিভাবে কাজ করেছে তার ইতিহাস লিখতে চেয়েছি। এটা আমাকে মানবসত্তা নামক সেই ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রের একজন স্বতন্ত্র ব্যাক্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়েছে। একজন ব্যক্তির জীবনেই সবকিছু ঘটে যা আপনাকে বাস্তবতার আসল চেহারা চিনতে সাহায্য করবে।
যুদ্ধের ঠিক পরপরই তীব্র অভিঘাত থেকে থিওডোর এডোর্নো লিখেছিলেন: ‘আউশউইৎসের পর কাব্য রচনা করা একটা বর্বরতা।’ আমর শিক্ষাগুরু আলেস অ্যাডামোভিচ যার নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। উনি একবার বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর দুঃস্বপ্নগুলো নিয়ে গদ্য রচনা করা একটা অপবিত্র কাজ। কোন কিছুই আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু সত্য যেভাবে আছে সেভাবেই প্রকাশ করুন। একটা ‘উপরই-সাহিত্য’ (super-literature) সৃষ্টি করা আবশ্যক। সাক্ষীদের জবানবন্দি নেয়া আবশ্যক। এখানে নীৎশের একটা কথা মনে পড়ে—কোন শিল্পীই বাস্তবতার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বাঁচতে পারে না। সে কখনোই বাস্তবতাকে এক ধাপ উর্ধ্বে নিতে পারে না।
একটা ভাবনা আমাকে সব সময় পীড়া দিতে থাকে তা হলো সত্য কখনো একজনের হৃদয়ে বা একটা মনে পুরোপুরি অবস্থান করে না। সত্য কোন না কোনভাবে খন্ডিত রূপে থাকে। সত্যের অনেক রূপ। সত্যের তারতম্য হয়। সত্য জগতের সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। দস্তেয়ভস্কি মনে করতেন মানব জাতি নিজেই অনেক কিছু জানে। সাহিত্যে যতো না লেখা আছে তার চেয়ে বেশি সে নিজেই জানে। তাহলে আমি আসলে কি করি? আমি মানুষের যাপিত জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অনুভূতি, চিন্তা ও শব্দকে একত্রিত করি। আমি আমার সময়কে সংগ্রহ করি। আমি প্রাত্যহিক জীবনের স্পন্দনকে ধরার চেষ্টা করি। ইতিহাসের বিশাল চিত্রপটে যে জিনিস বাদ পড়ে যায়, আড়ালে থাকে বা আমরা অবজ্ঞা করে বাতিল করে দেই তাকে খুঁজে আনি। আমি নিখোঁজ ইতিহাস নিয়ে কাজ করি। আমাকে প্রায়ই শুনতে হয় আমি যা লিখি তা কোন সাহিত্য নয় বরং স্রেফ একটা দলিল মাত্র। তাহলে আজকের দিনে সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আগের কাল থেকে আজকের জীবন অধিক গতিশীল। সাহিত্যের বিষয়বস্তু তার আকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। কখনো ভেঙে নতুন রূপ নেয়। কখনো দিক পরিবর্তন করে। কখনো নদীর জলের মতো তীরে উপচে পড়ে সব আকৃতি সমতলে মিশিয়ে দেয়। সঙ্গীত, চিত্রকর্ম এমনকি দালিলিক শব্দেরাও প্রামাণ্য প্রতিবেদনের সীমানাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। তথ্য ও গল্পের মধ্য আদতে তেমন কোন স্পষ্ট সীমারেখা নেই। একটা আরেকটার সাথে অনায়াসে মিশে যেতে পারে। সাক্ষীরাও নিরপেক্ষ থাকে না। একজন ভাস্কর যেভাবে মার্বেল নিয়ে কসরত করে সেভাবে একজন গল্পকার সময় নিয়ে কুস্তি করে। তারা অনেকটা স্রষ্টা ও অভিনেতার মতো।
আমি অতি সাধারণ ও সামান্য মানুষের ব্যাপারে উৎসুক থাকি। সামান্য, মহৎ মানুষের প্রতি আমার অসামান্য মনোযোগ। কারণ এরা জীবনে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে থাকে। কারণ এই ক্লেদ ও ক্লিষ্টতাই মানুষের জীবনকে বিস্তৃত করে তোলে। আমার বইতে এরা নিজেদের জবানে নিজেদের ইতিহাস বিবৃত করে। ক্ষুদ্র ইতিহাস ও বৃহৎ ইতিহাস যুগপৎ বয়ান করে। কি ঘটে গেছে কিংবা কি ঘটে চলছে তাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নাই। আমাদের শুধু এই ইতিহাসকে বলে যেতে হবে। কি ঘটেছে তাকে স্পষ্ট করে বলার মাধ্যমেই শুরুটা করতে হবে। কিন্তু এই সঠিক বিবৃতিতে আমাদের যতো আশঙ্কা। আমরা আমাদের অতীতের সাথে মানিয়ে চলতে পারি না। দস্তয়ভস্কির ‘ডেমনস’ উপন্যাসে শাটভ স্টাভরোগিনের সাথে কথার শুরুতেই বলে: ‘পৃথিবীর শেষ সময়ে এসে আমরাই দুটি প্রাণী যাদের অন্তহীন অসীমতার যুগসন্ধিতে এসে দেখা হয়েছে। তাই এই অহংবাদী স্বরভঙ্গি পরিত্যাগ করে একজন সামান্য ও সাধারণ মানুষের স্বরে কথা বলো। অন্ততপক্ষে জীবনে একবার হলেও মানুষের স্বরে কথা বলে দেখো।
ঠিক এভাবেই আমার মুখ্য চরিত্রদের সাথে আমার আলাপচারিতা শুরু হয়। চরিত্ররা তাদের নিজেদের সময়ের কন্ঠ হয়ে উঠে। অবশ্যই তারা শূন্যগর্ভ থেকে কথা বলে না। কিন্তু এটাও সত্য মানুষের আত্মার মূলে প্রবেশ করা কঠিন। এই পথ সংবাদপত্র, টেলিভিশনের তথ্য প্রমাণে সাজানো। শতাব্দীর কুসংস্কার, পক্ষপাতমূলক আখ্যান ও প্রতারনার কাটায় আকীর্ণ।
আমি আমার দিনলিপি থেকে কিছু অংশ পড়ে দেখাবো সময় কি করে এগিয়ে যায়। কিভাবে মানুষের চিন্তার নদী শুকিয়ে যায়। কিভাবে আমি এই পথের পিছু নেই।
১৯৮০-১৯৮৫
আমি যুদ্ধ নিয়ে একটা বই লিখছি। যুদ্ধ নিয়ে কেন? কারণ আমরা যুদ্ধ দিয়ে গড়া মানুষ। আমরা সবসময়ই কোন না কোন যুদ্ধের মধ্যে থাকি কিংবা কোন যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই থাকি। যদি আরেকটু কাছ থেকে দেখি তাহলে লক্ষ্য করবো আমরা সবাই সবকিছুকে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে চিন্তা করি। ঘরে বাইরে সবখানে। এই কারনেই এই দেশে জীবনের মূল্য এতো কম। সবকিছুই যুদ্ধকালীন চলমান।
একটা প্রচ্ছন্ন সংশয় নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে আরেকটা বই আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু কিসের জন্য? একবার কোন এক ভ্রমণের সময় আমার এক নারীর সাথে দেখা হয়েছিল যে কিনা যুদ্ধের সময় চিকিৎসক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন। তারা যখন শীতের সময় লাডোগা হ্রদ পার হচ্ছিল, শত্রুপক্ষ নড়াচড়া লক্ষ্য করে তাদের দিকে গুলি ছুড়তে লাগলো। ঘোড়া ও মানুষেরা একে একে সবাই বরফের পানির নিচে পড়ে গেলো। আমি একজনকে মারাত্মকভাবে আহত ভেবে আকড়ে ধরে টেনে তীরের দিকে তুলে আনতে লাগলাম। ‘আমি তাকে তুলে আনলাম, সে সম্পূর্ন ভেজা আর নগ্ন ছিলো। আমি ভাবলাম হয়তো তার পোশাক ছিড়ে গিয়েছিলো। তীরে উঠার পর লক্ষ্য করলাম, মানুষ নয় অতিকায় একটা স্টার্জন মাছ তুলে এনেছি।’ তারপর সে কিছু অপাংক্তেয় কথার স্ফুলিঙ্গ ছাড়তে লাগলো: মানুষ কষ্ট ভোগ করছে বুঝলাম কিন্তু পশু, পাখি, মাছ—এরা কি দোষ করছে বলতে পারো? আরেকটা ভ্রমণের সময় অশ্বারোহী বাহিনীর এক চিকিৎসকের গল্প শুনেছিলাম। যুদ্ধের সময় তিনি শেলের গর্ত থেকে এক আহত সৈন্যকে তুলতে গেলেন। তারপর দেখলেন যে সে একজন জার্মান সৈনিক। তার পা ভাঙা ছিল আর অনবরত রক্ত ঝরছিল। তিনি বললেন, ‘সে আমার শত্রু পক্ষের সৈন্য! এমন অবস্থায় আমি কি করবো? আমাদের দলের সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণে মাটির উপর মারা পড়চ্ছে, আহত হচ্ছে। কিন্তু আমি ওই জার্মানকে ব্যান্ডেজ করে হামাগুড়ি দিতে দিতে উপরে উঠে আসলাম। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা এক রুশ সৈনিককে তুলে এনে চেতনা ফিরিয়ে আনলাম। সজাগ হয়েই রুশ সৈন্যটা ওই জার্মান সৈন্যকে হত্যা করতে চাইলো। জার্মান সৈন্যটাও আত্মরক্ষার জন্য মেশিনগান তাক করে রুশ সৈন্যকে মারতে উদ্যত হলো।’ তিনি মনে করে বলতে লাগলেন, ‘আমি একজনকে জোরে থাপ্পড় দিলাম, সাথে সাথে অন্যজনকেও। আমাদের পাগুলো রক্তের লালে রঞ্জিত হয়ে ছিল।’ ‘শত্রু কি মিত্র সবাই লাল রক্তে মিলেমিশে একাকার।’
এটা এমন এক যুদ্ধ যা আগে কখনও শুনিনি। একজন নারীর যুদ্ধ। এটা কোন বীরপুরুষের কাহিনী নয়। এটা এক বাহিনীর হাতে আরেক বাহিনী হত্যার বীরত্বের গল্প নয়। একজন নারীর করুন আর্তনাতের সুর এখনও আমার কানে বাজে। ‘যে কোন যুদ্ধ শেষে তুমি যে কোন প্রান্তরে হেঁটে যাও। দেখবে যোদ্ধারা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সবাই তরুণ, সবাই সুদর্শন। তারা আকাশের দিকে চোখ মেলে শুয়ে আছে। একপক্ষ কি অপরপক্ষ সবার জন্যই তোমার হৃদয় করুণ রসে আর্দ্র হয়ে উঠবে।’ ‘উভয় পক্ষের সবাই’—এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার পরবর্তী বইয়ের বিষয়বস্তু ঠিক করে দেয়। হত্যা ছাড়া যুদ্ধের আর কোন লক্ষ্য নাই। নারীদের স্মৃতির আয়নাঘরে যুদ্ধের ছবিটা এমনই। যে লোকটা কিছু দিন আগে হাসছিল, সিগারেট খাচ্ছিলো—আজকে সে আর নাই। নারীরা পুরুষের এই নাই হয়ে যাওয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি বলতো। ‘সব থাকা’ বিষয়গুলো যুদ্ধের সময় কি করে চোখের নিমিষে ‘সব নাই’ হয়ে যায় তা নিয়ে কথা বলতো। শুধু মানুষ নয়। সময় পর্যন্ত নাই হয়ে যায়। উনি ১৭ ও ১৮ নাম্বার যুদ্ধ ফ্রন্টে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিলেন। জীবনে কাউকে কখনো হত্যা করার চিন্তাও করেননি। কিন্তু তারা নিজেরা মরার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। স্টালিনের জন্য জীবন দিতে অকুতোভয় ছিলেন। এই কথাগুলো তুমি ইতিহাসের পাতা থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারবে না। গর্বাচেভের সোভিয়েত পুনর্গঠনের আগ পর্যন্ত এই বইটা আলোর মুখ দেখেনি। সেন্সর বোর্ডের একজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘তোমার বইটি পড়লে দেশের একটা তরুণও যুদ্ধে যেতে চাইবে না।’ সাথে এও বলেছিলেন, ‘তোমার গল্পের যুদ্ধগুলো অন্যমাত্রার ভয়ংকর। তোমার কাহিনীতে কোন বীরযোদ্ধা নেই কেন?’ আমি কোনো বীরের খোঁজে ছিলাম না। আমি আমার গল্পের মাধ্যমে ইতিহাসের পর্দার ওপাশে থাকা প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের বয়ান তুলে আনতে চেয়েছিলাম। এ কথা শুনে ওরা আমাকে আর কোন প্রশ্ন করেনি। মানুষ আসলে কি চিন্তা করে? দুনিয়া কাঁপানো আইডিয়াগুলো সম্পর্কে মানুষ আসলে কিভাবে তার কোন খোঁজই আমরা রাখি না। যুদ্ধের ঠিক পরপর একজন ব্যক্তি যেভাবে গল্পটা বলে, একদশক পরে ওই একই ব্যক্তি ওই একই যুদ্ধ নিয়ে ভিন্ন গল্প বলবে। তার মধ্যে একটা আগাগোড়া পরিবর্তন চলে আসবে কারণ ততদিনে সে তার পুরো জীবনটা স্মৃতির বলয়ে আটকে ফেলেছে। তার পুরো সত্তাকে অখণ্ড রূপে দেখতে পারবে। সেই সময়ে সে কিভাবে তার জীবনটা যাপন করেছে। সে কি কি পড়েছে, কি কি দেখেছে, কার কার সাথে চলেছে, কিসে কিসে তার বিশ্বাস ছিল, সবকিছু। তারপর সে ভাববে আসলেই কি সে সবকিছু মিলিয়ে সুখী ছিল। কথ্য দলিল অনেকটা প্রাণসংস্থার মতো। মানুষের পরিবর্তনের সাথে তারাও পরিবর্তিত হয়।
আমার অকাট্য বিশ্বাস—১৯৪১ সালের যুদ্ধের নারীদের মতো নারী এ জগতে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। ‘লাল’-এর ধারণা এই সময়ে সর্ব শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি রুশ বিপ্লব ও লেনিনের ধারণা থেকেও শীর্ষে। তাদের বিজয়ের আলোয় গুলাগের দীপ্তিতেও ফিকে লাগবে। আমি মন থেকে ওইসব নারীদের অনুরাগভাজন হয়ে আছি। কিন্তু তুমি তাদের সাথে লেনিনকে নিয়ে কথা বললে তারা কিছুই বুঝবে না। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেও কাজ হবে না। সবচেয়ে দুঃসাহসিক সৈন্যদল এবং সবচেয়ে স্পষ্টভাষী যুদ্ধ বিজেতাদের সরাসরি সার্বিয়া নেওয়া হয়েছিল। অন্যদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সবকিছু নীরবতার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছিল। একবার আমি এক সৈন্যের মুখে এটাও শুনেছিলাম: ‘আমরা শুধুমাত্র জীবনে একবারই স্বাধীন ছিলাম, তাও আবার যুদ্ধের ময়দানে।’ জীবনের যাতনা আমাদের একমাত্র মূলধন। আমাদের একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ তেল নয় প্রাকৃতিক গ্যাস নয়—শুধুই জীবন যন্ত্রণা। এটা একমাত্র বস্তু যা আমরা বিরতিহীন ভাবে জীবন থেকে উৎপাদন করে যাচ্ছি। আমি সব সময় একটা উত্তরের সন্ধানে আছি: কেন আমাদের যাতনা আমাদের স্বাধীনতায় পরিণত হয় না। তাহলে সবকিছুই কি বিফলে গেলো? চাদায়েভ ঠিকই বলেছিলেন, রাশিয়া হলো স্মৃতি শূন্য দেশ। আস্ত স্মৃতিভ্রংশের চারণভূমি। এই উক্তিটা সমালোচনা ও প্রতিফলন এর এক বিশুদ্ধ চেতনা।
এতোকিছুর পরও আমাদের পায়ের নিচে মহৎ কিছু গ্রন্থ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।
১৯৮৯
আমি এখন কাবুলে আছি। আমি আর যুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে চাই না। কারণ এখানে আমি স্বয়ং নিজেই যুদ্ধে লিপ্ত। প্রাভদা সংবাদপত্রে লিখেছে, ‘আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম আফগানদের সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করছি।’ সব জায়গায় জনমানুষের যুদ্ধ ও জাগতিক বস্তুর জন্য যুদ্ধ চলছে। সব সময় যুদ্ধের সময়।
গতকাল ওরা আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যায়নি। তারা বললো, ‘ইয়ং লেডি, আপনি আজ বরং হোটেলেই থাকেন। না হলে পরে আপনার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।’ আমি হোটেলে বসে ছিলাম। আর ভাবছিলাম। অন্যদের সাহসিক কাজ ও তারা জীবনে যে ঝুঁকি নিয়ে থাকে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা একটা অনৈতিক কাজ। আমি কাবুলে দুই সপ্তাহ ধরে আছি। যুদ্ধ যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রত্যক্ষ ফল এই অনুভূতি থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারছি না। যুদ্ধ আমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য লাগে।যুদ্ধের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত সরঞ্জামের আয়োজন খুবই সুবিশাল। যুদ্ধের অস্ত্রগুলো যে খুব দৃষ্টিনন্দন তা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। মেশিনগান, মাইন, সাজোয়া যান। মানুষকে কতোটা উৎকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করা যায় তার জন্য মানুষ তাদের ভাবনার কোনো কমতি রাখে নাই। এটা সত্য ও সুন্দরের মাঝে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তারা আমাকে একটা ইতালিয়ান মাইন দেখালো আর আমার ভেতরের নারী মনের প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘মাইনটা সুন্দর কিন্তু কেন এটা সুন্দর?’ তারা তাদের সামরিক শব্দ ভান্ডার দিয়ে আমাকে ব্যাখ্যা করলো। যে কোন দিক থেকে কেউ যদি এই মাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চালায় কিংবা একপা ফেলে তাহলে অর্ধেক বালতি মাংসের দলা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ এখানে অস্বাভাবিক বিষয়ে এমন সুরে কথা বলে যেন সবকিছুই স্বাভাবিক। কোন বিচার ছাড়া সবকিছুকে মেনে নেয়। আচ্ছা! তুমি তো জানো, এখন যুদ্ধ চলছে... তাই এই মৃত্যুর বিভীষিকাময় ছবি দেখে কেউ কি উন্মাদ হয়ে যাবে? যুদ্ধে মানুষ মারা যাবে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। এই যেমন, ওইখানে একটা মানুষ মরে মাটিতে পড়ে আছে। তাকে কে মেরেছে? কোন বস্তু? এই মৃত্যু কি তার কপালের অমোঘ পরিণতি ছিল? না, সে মরেছে আরেকজন মানুষের নৃশংসতার ফলে।
আমি ‘ব্ল্যাক টিউলিপ কিভাবে বোঝাই করে তা দেখেছি (যে উড়োজাহাজ করে হতাহতদের জিংঙ্ক কফিনে করে বাড়িতে পাঠানো হয়)। মৃতদের প্রায়ই চল্লিশের দশকের ঐতিহ্যবাহী সামরিক পোশাকের সাথে যোধপুরী আটশাট পাজামা পরানো হয়। মাঝে মাঝে এই পোশাকগুলো সব মৃতদের জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যায় পাওয়া যায় না।’ সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে গালগপ্পো করছিল, ‘তারা নতুন কিছু মরদেহ কফিনের বদলে ফ্রিজে চালান করেছে, কারণ শবদেহ থেকে পচা শূকরের মাংসের মতো দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল।’ আমি এই বিষয়ে লিখতে চাচ্ছি। আমার মনে হয় দেশের কেউই আমার এই কথাগুলো বিশ্বাস করবে না। আমাদের সংবাদপত্রগুলো সব সময় সোভিয়েত সৈন্যদের মিত্রতা নিয়ে খবর প্রকাশ করে। আমি অনেক যোদ্ধাদের সাথে কথা বলেছি। অনেকেই স্বেচ্ছায় এসেছে। আমি খেয়াল করলাম বেশিরভাগই উচ্চ শিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছে। অনেকেই বুদ্ধিজীবী গোত্রের যেমন শিক্ষক, চিকিৎসক, গ্রান্থারিক—সহজে বললে সবাই কম বেশি পাঠের অনুরাগী ছিল। তারা সত্যি আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্র কায়েম করার স্বপ্নে বিভোর ছিল। আর এখন তারা নিজেদের নিয়ে নিজেরাই উপহাস করে। আমাকে এয়ার পোর্টের একটা বিশেষ স্থান দেখানো হয়েছিল যেখানে জিংকের কফিনগুলো সূর্যের আলোতে চকচকে করে এক রহস্যময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করছিল। আমাকে যে অফিসারটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল সে হঠাৎ বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, ‘কে জানে... হয়তো আমার কফিনটাও ওইখানে সারিবদ্ধ থাকতে পারতো... আমাকে হয়তো এই কফিনের ভেতর আটকে রাখতো... আমি আসলে কি জন্য এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি... কিসের আশায়?’ তার নিজের মুখের কথায় সে নিজেই ভয় পেয়ে গেলো। সাথে সাথে আমাকে অনুরোধ করলো, ‘অনুগ্রহ করে আমার কথাগুলো আপনার লেখায় আনবেন না।’
রাতের বেলায় আমি ওই সব মৃতদের স্বপ্নে দেখলাম। তাদের সবার চেহারাতে কি বিস্ময় লেগে আছে। যেন বলতে চাইছে, ‘কি বলছো? আমি আর বেঁচে নেই! সত্যি আমাকে হত্যা করা হয়েছে?’
আমি একদল সেবিকাদের সাথে একটা আফগান বেসামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমরা বাচ্চাদের জন্য নানা উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম। খেলনা, চকোলেট আর বিস্কুট। আমার হাতে পাঁচটি টেডি বেয়ার ছিল। আমরা ব্যারাকের মতো বানানো একটা হাসপাতালে গেলাম। কারও কাছে একটা কম্বল ছাড়া শোবার জন্য আর কিছু ছিল না। একজন আফগান নারী কোলে করে একটা বাচ্চা নিয়ে আমার সামনে এলো। সে কিছু বলতে চাচ্ছিলো। গত দশ বছরে প্রায় সকল আফগান অল্পস্বল্প রাশিয়ান শিখেছে। আমি বাচ্চাটাকে একটা খেলনা দিলাম। বাচ্চাটা দাঁত দিয়ে তা কামড়ে নিল। আমি অবাক হয় জানতে চাইলাম, ‘দাঁত দিয়ে কেন?’ মা বাচ্চাটির শরীর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিলো। আমি দেখলাম বাচ্চাটির দুটি হাত নেই। ‘রাশিয়ানদের বোমা বিস্ফোরণে ওর হাত দুটা হারিয়েছে।’ কথা শোনা মাত্র আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। আমি শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। কেউ একজন মাটিতে পরার আগে আমাকে ধরে ফেললো।
আমি দেখেছি আমাদের গ্রাড রকেটগুলো আফগান গ্রামগুলোকে চাষের জমিতে রূপান্তরিত করেছে। আমি একটা আফগান কবরস্থানে গিয়েছিলাম। গোরস্থানটা প্রায় একটা গ্রামের সমান বড়। সমাধিক্ষেত্রের মাঝখান থেকে এক আফগান নারীর আর্তচিৎকার ভেসে আসছিল। আমার মনে আছে মিনস্কের এক কবরখানায় জিংক কফিন সমাধিস্থ করার সময় এমনই তীব্র চিৎকার শুনেছিলাম। এই আওয়াজ কোন মানুষ বা পশুর নয়। এটা কাবুলের কবরস্থানে শোনা সেই নারীর আর্তনাদের সমতুল্য।
আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ভ্রমণের সময় আমি পুরোপুরি স্বাধীন ছিলাম না। কিন্তু আমার লেখার বিষয়বস্তুর প্রতি আমি নিবেদিত ছিলাম। আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসও ছিল। আমাদের সবারই যার যার মতো স্বাধীনতা আছে। আফগানিস্তানের আগে সমাজতন্ত্রের একটা মানবিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম। কিন্তু আফগানিস্তান থেকে আমি আমার অতীতের সকল বিভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলাম।
‘আমাকে ক্ষমা করো বাবা,’ ফিরে এসে বাবাকে দেখা মাত্র বললাম, ‘সমাজতন্ত্রের উপর যেন আমি বিশ্বাস রাখি সেভাবেই তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছো। ওইসব তরুণ সৈন্য যাদের তুমি সমাজতন্ত্রের আদর্শের শিক্ষা দিয়েছো (আমার বাবা-মা দুজনেই স্কুল শিক্ষক ছিলেন) তারা বিদেশের মাটিতে যাদের তারা ভালো করে চেনে না তাদের নির্বিচারে হত্যা করছে। তোমার সকল সাম্যবাদী বুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা হত্যাকারী, বাবা। তুমি কি বুঝতে পারচ্ছো বাবা!?’ আমার কথা শুনে বাবা কেঁদে ফেললো।
অনেকেই আফগানিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু ভিন্ন চিত্রও আছে। আফগানিস্তান ভ্রমণের সময় এক তরুণ আমার দিকে কর্কশ সুরে চিৎকার করে বলেছিল, ‘তুমি তো একজন নারী, পুরুষ নও। তুমি কী বুঝবে যুদ্ধ কি? তুমি কি মনে করো যুদ্ধ মানুষ শখ করে সুন্দর মরণ মরতে আসে যেমনটা উপন্যাস বা চলচ্চিত্রে দেখা যায়? গতকাল আমার এক বন্ধু খুন হয়ছে। ওর মাথায় গুলি বিধেছিল। নিজের মাথা থেকে পড়ে যাওয়া মগজ হাতে নিয়ে প্রায় দশ মিটার দৌড়ে গিয়েছিল।’ সাত বছর পর ওই তরুণের সাথে আমার আবার দেখা হয়েছিল। তখন সে একজন সফল ব্যবসায়ী যে আফগানিস্তানের স্মৃতি নিয়ে গল্প করতে ভালোবাসতো। সে আমাকে ডেকে বললো, ‘আপনি যেন কি কি বিষয়ে বই লিখেন? গল্পগুলো খুব ভীতিকর।’ যুদ্ধের মড়ার মাঝে যে তরুণকে জানতাম তার থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ হয়ে উঠেছিল। যে কিনা বিশ বছর বয়সে মরণ থেকে পালাতে চাইতো।
আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি আসলে যুদ্ধ নিয়ে কেমন বই লিখতে চাই। আমি এমন এক মানুষের গল্প বলতে চাই যে বন্দুকের গুলি ছুড়বে না। যে কিনা মানুষকে হত্যা করবে না। যে যুদ্ধের কথা ভাবলেই আত্মপীড়া ও বিষাদে ভুগবে। কোথায় পাবো এমন মানুষ? এখনো তার দেখা পাই।
১৯৯০-১৯৯৭
রুশ সাহিত্য খুবই চমকপ্রদ। কেননা বিশ্বে এটাই একমাত্র সাহিত্য যা সুবৃহৎ দেশের বিশালসংখ্যক মানুষের গল্প নিয়ে নিরীক্ষা করার সুযোগ পায়। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আপনি কেন সবসময় বিয়োগাত্মক কাহিনী লিখেন?’ আমি উত্তর দেই, ‘কারণ আমরা এমন জীবনই যাপন করি।’ আজকে যদিও আমরা আলাদা আলাদা অনেকগুলো দেশে বাস করি। কিন্তু আপনি সব দেশেই ‘লাল’ মানুষ পাবেন। তারা সবাই একই রকম জীবন থেকে আহুত। সবাই একই স্মৃতির অংশ।
দীর্ঘদিন যাবৎ চেরনোবিল নিয়ে লেখা থেকে আমি নিজেকে দূরে রেখেছিলাম। আমি জানতাম না ঠিক কিভাবে চেরনোবিল নিয়ে লিখতে হবে। কি কি কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। কোন চোখে বিষয়টা দেখতে হবে। ইউরোপের এক কোনায় লেগে থাকা আমার এই ছোট্ট দেশটা সম্পর্কে বিশ্ববাসী তেমন কিছুই শুনে নাই। কিন্তু এখন এই দেশের নাম সারা দুনিয়ার মানুষের মুখে মুখে। আমরা বেলারুশিরা এখন চেরনোবিলের মানুষ বলে পরিচিত। প্রথম সাক্ষাৎটা ছিল অজানা। এখন এটা খুব স্পষ্ট যে সাম্যবাদ, জাতিসত্তা, ও নতুন ধর্ম উদ্ভবের হুমকি ছাড়াও আমাদের জন্য নানান বৈশ্বিক বর্বরতা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল, যার বেশিরভাগই আমাদের কাছে চোখের আড়ালে ছিল। চেরনোবিল ঘটনার পর আস্তে আস্তে প্রকাশিত হতে লাগলো।
আমি একবার দেখলাম একটা কবুতর একটা গাড়ির জানালায় আছড়ে পড়ায় ট্যাক্সি চালক বিরক্ত হয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগলো। প্রতিদিনই দুই থেকে তিনটা পাখি গাড়ির কাচে আছড়ে পড়ে কিন্তু পত্রিকাগুলো প্রচার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।
শহরের পার্কের গাছের পাতাগুলো সব একত্রে জড়ো করা হতো, শহর থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা হতো। দূষিত এলাকার মাটি কেটে নিয়ে দূরে কোথাও পুঁতে রাখা হতো। মাটি খুঁড়ে মাটি পুঁতে রাখা হতো, আগুন কাঠের গাছ পুঁতে রাখা হতো, ঘাসও চাপা দেয়া হতো। সবাই কেমন যেন একটু পাগলাটে হয়ে গিয়েছিল। একজন বৃদ্ধ মৌয়াল একবার আমাকে বলেছিল, ‘সেদিন সকালে আমি বাগানে কাজ করছিলাম। কিছু একটার অভাব, একটা শূন্যতা বোধ করছিলাম। একটা চেনা গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম না। খেয়াল করলাম বাগানে একটা মৌমাছিও নেই। একটা মৌমাছির ডাকও শুনতে পাই নাই। একটাও না। কি? কি হচ্ছে এই সব? দ্বিতীয় দিন এমনকি তৃতীয় দিনও তাদের উড়তে দেখি নাই। তারপর একদিন শুনলাম যে পারমাণবিক কারখানাতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কারখানাটা বেশি দূরে ছিল না। অনেকদিন পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার কথা আমরা তেমন জানতে পারি নাই। মৌমাছিরা বুঝতে পেরেছে। আমরা বুঝতে পারিনি।’ খবরের কাগজে চেরনোবিল নিয়ে সকল তথ্যই সামরিক ভাষায় প্রকাশ করা হতো: বিস্ফোরণ, বীরযোদ্ধা, সৈনিক, উচ্ছেদ... কারখানায় কেজিবি ঠিক ঠাক কাজ করছে। তারা গুপ্তচর ও নাশকতাকারী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে পশ্চিমা গোয়েন্দা বাহিনী সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে হেয় করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। চেরনোবিলের দিকে সামরিক সরঞ্জাম রওনা দিয়েছিল ও সৈন্যদল সেখানে জড়ো হচ্ছিল। রাষ্ট্র এমন সব ব্যবস্থা নিচ্ছিল মনে হতো যেন যুদ্ধ চলছে। কিন্তু আজকে এই নবযুগে চকচকে নতুন অস্ত্র হাতে ধরা সৈন্য একটা পরিতাপের ছবি। সে শুধু একটা কাজই করতে পারতো তা হলো ব্যাপক পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি শুষে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।
আমার চোখের সামনে চেরনোবিল-পূর্ব লোকেরা চেরনোবিলের লোকে পরিণত হলো।
আপনি বিকিরণ কখনো দেখতে পারবেন না, একে স্পর্শ করতে পারবেন না। এমনকি এর ঘ্রাণও নিতে পারবেন না। আমদের চারপাশের জগৎ যতোটা চেনা ততোটা অচেনা। আমি যখন ওই এলাকা দেখতে গেলাম তখন আমাকে বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে আমি যেন কোন ফুল না ধরি, কোন ঘাসে না বসি, কোন কূপ থেকে পানি পান না করি। মৃত্যু সবখানে ঘাপটি মেরে আছে। কিন্তু এই মৃত্যু অন্য সব মৃত্যু থেকে আলাদা। মুখোশ পড়ে থেকে সম্পূর্ণ অচেনা চেহারা নিয়ে ঘুরতে হবে। যে সকল বয়োবৃদ্ধ যুদ্ধকে টেক্কা দিয়ে বেঁচে ছিলো তাদের সবাইকে সরিয়ে নেয়া হলো। তারা আকাশে তাকিয়ে ভাবতো, ‘সূর্য ঝলমলে, কোন ধূয়া নাই, কোন গ্যাস নাই। কেউ গুলি চালাচ্ছে না। তাহলে এটা আবার কেমন যুদ্ধ? আমরা কেন আবার বাস্তুচ্যুত হলাম?’
প্রতিদিন সকালে সবাই খুব উদ্দীপনা নিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিতো। কী ঘটছে তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠতো। তারপর হতাশ হয়ে কাগজটা সরিয়ে রাখতো। কোন গুপ্তচর খুঁজে পাওয়া যায় নাই। কেউ বিদেশী গণশত্রুর সন্ধান পায় নাই। শত্রু ও গুপ্তচর বিহীন পৃথিবী এক অচেনা জগৎ যেন। এটাই ছিল আমাদের জন্য নবযুগের আরম্ভ। আফগানিস্তানের পট পরিবর্তনের পর চেরনোবিলের বিভীষিকা আমাদের আরো একধাপ মুক্ত করে দিল।
আমার কাছে দুনিয়াটা যেন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলো: চেরনোবিল এলাকায় ঢোকার পর আমি নিজেকে বেলারুশিয়ান, রাশিয়ান এমনকি ইউক্রেনিয়ান হিসাবে ভাবতে পারি নাই বরং নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায় এমন এক জৈব সংগঠনের প্রতিনিধি মনে হয়েছে। যুগপথ দুটি মহাবিপর্যয় ঘটে গেলো: একটা হলো সামাজিক বলয়ে সমাজতন্ত্রের গণ্ডি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, অন্যটা হলো মহাজাগতিক বলয় যেখানে চেরনোবিল ঘটে গেছে। সাম্যবাদী সাম্রাজ্যের পতন সবাইকে বিচলিত করে তুলেছে। প্রত্যেকে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে লাগলো। কি দিয়ে বাজারে করবে? কি কি খাবার কিনবে? কিভাবে বেঁচে থাকবে? কি বিশ্বাস করবে আর কি বিশ্বাস করবে না। এই অকালে কোন ব্যানার অনুসরণ করবে? কিভাবে মহৎ কোন আদর্শ ও আইডিয়া ছাড়া বেচেঁ থাকা যায় তাই কি শিখতে হবে? কেননা আদর্শ ছাড়াই বেঁচে থাকার সময় এখন। ‘লাল’ মানুষকে এমন শত শত প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে ব্যস্ত থাকতে হতো। কেন সে আর তার মাঝে অস্তিত্ববান ছিলো না? স্বাধীনতার শুরুর দিনগুলোতে সে এমন করে অস্তিত্ব সংকটে ভোগে নাই। আমার চারপাশ মানুষের শঙ্কিত মুখ দিয়ে পূর্ণ ছিল। আমি অপার হয়ে তাদের কথা শুনতাম...
আমার দিনলিপি এই পর্যন্ত থাক ...
যখন সাম্রাজ্যের পতন হয় তখন আমাদের সাথে কি কি ঘটে? পূর্বে বিশ্ব বিভক্ত ছিল একভাবে: শিকার ও শিকারী যা আমাদের গুলাগ দিয়েছে। ভাই ও বোনদের কোন্দল যা আমাদের যুদ্ধ দিয়েছে। মনোনীত ব্যক্তিবর্গ এটা প্রযুক্তির অংশ ও সমকালীন বিশ্বের নিশানা। আমাদের সোভিয়েত জগৎ এমন ধারায় বিভক্ত হয়েছে। একদল বন্দীত্ব বরণ করেছে। আরেক দল তাদের বন্দী করেছে। আজকের দিনের বিভক্তি স্লাভোফিলিস ও ওয়েস্টার্নাইজারস, ফ্যাসিবাদী-দেশদ্রোহী ও দেশপ্রেমীদের মাঝে। বিভক্তি যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে আর যাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় দল নিয়ে আমি বলবো সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের জন্য চরম অগ্নিপরীক্ষা। কেননা বেশিদিন আগে নয় যখন সবাই সমতার মধ্যেই ছিল। ‘লাল’ মানুষেরা তাদের খাবার টেবিলে বসে যে মুক্ত রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিল তার সদর দরজার চৌকাঠ পাড় হতে পারেনি। রাশিয়া তাকে রেখেই আলাদা হয়ে গেছে। সেও রিক্ত হস্তে একলা পড়ে রইলো। নিঃস্ব ও লাঞ্চিত। মারমুখো ও বিপজ্জনক।
এখানে কিছু মন্তব্য পড়বো যা আমি সারা রাশিয়া ভ্রমণকালীন শুনেছিলাম।
‘আধুনিকায়নের ছোঁয়া শুধু শারাশকাসগুলোতে পাবেন, ওই সমস্ত বন্দি শিবির যেখানে শুধু বিজ্ঞানী ও ফায়ারিং স্কোয়াডের লোকেরা থাকে।
‘রাশিয়ানরা কখনো ধনী হতে চায় না। বরং ধনী হতে তাদের ভয় লাগে। রাশিয়ানরা তাহলে আসলে কি চায়? তারা শুধু একটা জিনিসই চায়। অন্য কেউ যেন ধনী না হতে পারে। হলেও তাদের থেকে বেশি ধনী যেন না হয়।’
‘এখানে কোন সৎ লোক পাবেন না কিন্তু সাধু লোকের অভাব নেই।’
‘এমন কোন প্রজন্ম দেখি নাই যারা চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয় নাই। রাশিয়ানরা স্বাধীনতা বোঝে না। তাদের দরকার একজন কসাক আর চাবুকে দাগ।’
‘রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ হলো “যুদ্ধ” ও “কারাগার”। তুমি মজার ছলে কিছু চুরি করবে তারা তোমায় জেলবন্দি করবে। তুমি বেরিয়ে আসো তারা আবার মজার ছলে তোমায় জেলে ভরবে।’
‘রাশিয়ান জীবন কেমন যেন ধূর্ত ও ঘৃণ্য হয়ে যায়। তারপর একদিন এর আত্মা জেগে উঠে আর বুঝতে পারে যে সে আর এই জগতের কেউ নয়।
... বস্তু যতো বেশি পঙ্কিল ও নৃশংস হয়ে উঠে, আত্মার জন্য তার স্থান ততো বেশি বিস্তৃত হয়...’
‘নব বিপ্লবের বা উন্মাদনার জন্য আর কারোই কোন উদ্দ্যম নাই। কোন প্রাণশক্তিও অবশিষ্ট নাই। রাশিয়ানদের জন্য এমন আইডিয়া দরকার যা তাদের শিঁরদাড়ায় কাপুনি ধরিয়ে দিবে।’
‘রাশিয়ানদের জীবন পাগলা গারদ ও যুদ্ধ শিবিরের মাঝে ঝুলে আছে। সমাজতন্ত্র মরে যায়নি। শবদেহগুলো এখনো জীবন্ত।’
আমি একটা কথা বলার সুযোগ হাত ছাড়া করবো না যে ১৯৯০ দশকের বছরগুলোতে আমাদের যে সুযোগ ছিল তা আমরা হেলায় হাত ছাড়া করেছি। একটা প্রশ্ন সবসময় আমাদের মুখের সামনে ঝুলছিলো: আমরা কেমন দেশ চাই? একটা ক্ষমতাবান দেশ নাকি সমৃদ্ধ দেশ যেখানে সবাই প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি নিয়ে বাস করতে পারবে? আমরা প্রথমটা বেছে নিয়েছি—একটা শক্তিশালী দেশ! আমরা এখন ক্ষমতার যুগে বাস করছি। রাশিয়ানরা ইউক্রেনিয়ানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের মৃত্যু-মৃত্যু খেলা। আমার বাবা বেলারুশিয়ান, আমার মা ইউক্রেনিয়ান। এই হলো অধিকাংশ লোকের চালচ্চিত্র। রাশিয়ান বোমা সিরিয়ার মানচিত্র ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে।
ভরসার সময়গুলো ভয়ের সময় দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। যুগের মোড় ঘুরে যাচ্ছে। উল্টো পায়ে অতীতের অন্ধকার সময়ে ফিরে যাচ্ছে। আমরা এখন একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড সময়ে বাস করি।
মাঝে মাঝে আমি একটা সংশয়ে পড়ে যাই যে আমি বোধ হয় ‘লাল’ মানুষের ইতিহাসটা পুরোপুরি লিখে শেষ করতে পারি নাই।
আমার তিনটা বাড়ি আছে: আমার পিতৃভূমি বেলারুশ যেখানে আমার পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। আমার মাতৃভূমি ইউক্রেন যেখানে আমি জন্মেছি। আমার সাংস্কৃতিক ভূমি রাশিয়া যে দেশটা ছাড়া আজকের আমার আমিকে কল্পনা করতে পারবো না। সবগুলো দেশই আমার প্রানের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে আজকের দিনে ভালবাসার কথা বলা এক কঠিন কাজ।
উৎস লিংক: Svetlana Alexievich–Nobel Lecture–NobelPrize.org
কপিরাইট © Nobel Prize Foundation 2015
বাংলা কপিরাইট © Pratidhwanibd.com






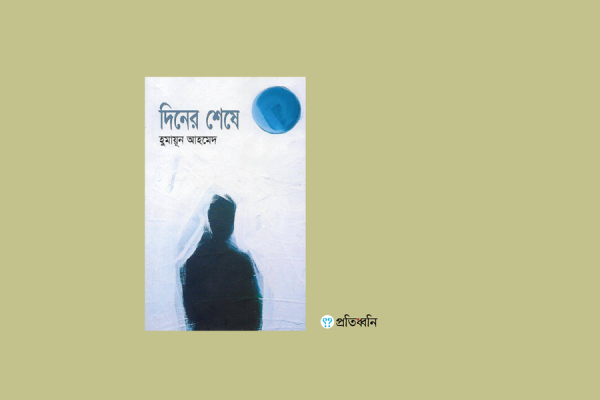

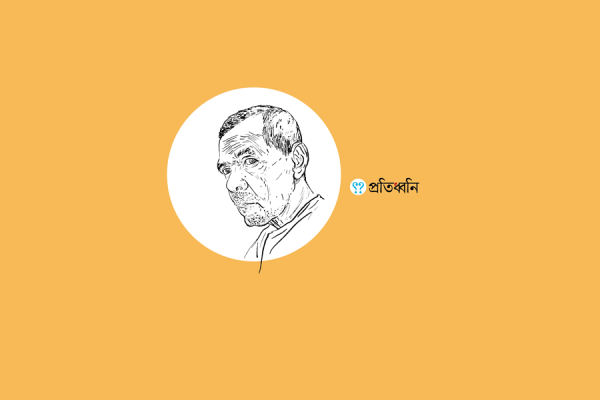
আপনার মন্তব্য প্রদান করুন