ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের নোবেল বক্তৃতা

|| হ্যারল্ড পিন্টার ||
হ্যারল্ড পিন্টার ১০ অক্টোবর ১৯৩০ সালে লন্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধ-বিরোধী ও ইহুদী-বিদ্বেষী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, যার প্রভাব তার নাটকগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। মাত্র নয় বছর বয়সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাকে লন্ডন ছাড়তে হয়েছিল এবং বারো বছর বয়সে ফিরে এসেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে মৃত্যুর মহামারী ও ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন তার স্মৃতি মন থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারেননি। হ্যাকনি গ্রামার স্কুলে পড়ার সময় তিনি জোসেফ ব্রেয়ারলির নির্দেশনায় ম্যাকব্যাথ ও রোমিওসহ নানা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি রয়্যাল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্য তিনি মঞ্চ অভিনেতা ডেভিড ব্যারন নামে ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি অভিনেত্রী ভিভিয়ান মার্চেন্টের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি লেখক ও ইতিহাসবিদ লেডি আন্তোনিয়া ফ্রসারকে বিয়ে করেন।
১৯৫৭ সালে তিনি দ্য রুম প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যসাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। একই বছর দ্য বার্থডে পার্টি নাটকটি রচনা করেন যা স্মরণকালে সবচেয়ে ব্যর্থ মঞ্চ নাটকের উপাধি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নাটকটি সবচেয়ে বেশি মঞ্চায়িত হয় ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে। দ্য কেয়ারটেকার (১৯৫৯) এবং দ্য হোমকামিং (১৯৬৪) তার যুগান্তকারী দুটি নাটক। নাট্য সাহিত্যের বিশ্বমঞ্চে এ নাটক দুটি তাকে নাট্যকার হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। হ্যারল্ড পিন্টারকে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ নাট্যসাহিত্যের অগ্রনায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়। আধুনিক কালোত্তীর্ণ সাহিত্যে তিনি এতো শক্তিশালী প্রভাব রেখেছেন যে তার নাটকের বিশেষ আবহ ও প্রতিবেশের শৈলী নাট্য ভাষায় ‘প্রিন্টারেস্ক’ শব্দটি বিশেষণ পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
পিন্টার মঞ্চনাট্যের মৌলিক উপাদানগুলো পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। যেমন—আবদ্ধ স্থান ও অপ্রত্যাশিত ও অননুমেয় সংলাপ। যার ফলে মানুষ একে অন্যের করুণাপ্রার্থী হয়ে পড়ে এবং মানুষের চরিত্রের কৃত্রিমতা ও ভণিতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ক্ষুদ্রতম আখ্যানভাগের ফলে চরিত্রের মধ্য ক্ষমতার-দ্বীপ প্রকট হয়ে উঠে আর সংলাপের লুকোচুরি চলতে থাকে। পিন্টাররের নাটকগুলোকে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের একটা বিশেষ প্রকার হিসাবে দেখা হয়। পরবর্তীকালে ‘ভীতিমূলক প্রহসন’ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এমন এক রচনাশৈলী যেখানে খুব সাধারণ হাস্যরসাত্মক আলাপচারিতার মধ্য প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তা দেখিয়ে দেয়। বলা যায় এক রকম ত্রাসের বিলাস চলতে থাকে। পিন্টাররের অধিকাংশ নাটকের চরিত্রগুলো বাহ্যিক শক্তির অনুপ্রবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। এমন কি নিজেদের আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি থেকেও তারা প্রভাবিত হতে চায় না। এটা করতে গিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত পরিসর ও পরিস্থিতিতে আবদ্ধ করে রাখে। অতীতের বিভ্রান্তিকর রূপ ও ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় নিয়ে মানুষের অস্থিরতা পিন্টাররের নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পিন্টার তার নাট্যসাহিত্যের প্রারম্ভিক-পর্বে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদের চর্চা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ল্যান্ডস্কেইপ (১৯৬৭) এবং সাইল্যান্স (১৯৬৮) গীতিনাট্যের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিলেন। ওয়ান ফর দ্য রোড (১৯৮৪), মাউন্টেইন ল্যাংগুয়েজ (১৯৮৮), দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (১৯৯১) ও অন্যান্য নাটকে তিনি রাজনৈতিক বিষয়কে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু পিন্টাররের রচনাকালের এই অতিসাধারণীকরণ তার অন্যান্য শক্তিশালী সৃষ্টি যেমন নো ম্যান’স ল্যান্ড (১৯৭৪) ও অ্যাশেজ টু অ্যাশেজ (১৯৯৬) নাটকগুলোকে আড়াল করে ফেলে। তার নাট্য সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবাহিকতা এক কথায় অনন্য। তার রাজনৈতিক নাটকগুলো অন্যায় ও অবিচারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের এক বিকাশ পর্ব হিসাবে দেখা যেতে পারে।
১৯৭৩ সাল থেকে পিন্টারকে একজন লেখকের পাশাপাশি মানবাধিকারের একজন সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পিন্টার মঞ্চ নাটক ছাড়াও রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লিখেছেন। দ্য সার্ভেন্ট (১৯৬৩), দ্য অ্যাকসিডেন্ট (১৯৬৭), দ্য গো-বিটুইন (১৯৭১) ও জন ফাউলসের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত দ্য ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্ট’স ম্যান (১৯৮১) তার রচিত বিখ্যাত চিত্রনাট্য। তিনি নির্দেশক হিসাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন। পিন্টার তার নাটকে মানুষের আটপৌরে জীবনের কলতান ও কড়চার মাঝে অন্তর্নিহিত বাস্তবতার তিক্ত সত্য বের করে আনা এবং দুঃশাসকের সুরক্ষিত গৃহ জবর দখলের নিপুণ চিত্র অঙ্কনের দক্ষতার জন্য ২০০৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
|| সম্পাদকীয় নোট ||
ব্রিটিশ নাট্যকার ও লেখক হ্যারল্ড পিন্টারের শিল্প, সত্য ও রাজনীতি শিরোনামের বক্তৃতাটি দেন নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশানের অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান প্রতিধ্বনি পত্রিকাকে বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশের কপিরাইট প্রদান করেছে। আমরা নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান ও হ্যারল্ড পিন্টারের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। প্রতিধ্বনির জন্য এটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও সমালোচক পলাশ মাহমুদ।
হ্যারল্ড পিন্টারের নোবেল বক্তৃতা || শিল্প, সত্য ও রাজনীতি
১৯৫৮ সালে নিচের লেখাটা লিখেছিলাম।
বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে যেমন স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই তেমনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে নেই কোন স্বচ্ছ সীমারেখা। কোন বিষয়কে অপরিহার্যভাবে হয় সত্য, না হয় মিথ্যা হতে হবে এমন নয়। বরং একই বিষয় একইসাথে সত্য ও মিথ্যা হতে পারে।
আমি মনে করি এই কথাগুলো এখনও সমানভাবে অর্থপূর্ণ। শিল্পের মাধ্যমে বাস্তবতাকে বোঝার জন্য এখনও সমানভাবে প্রয়োগিক। লেখক হিসাবে আমি এই কথাগুলো যতো সহজে মেনে নিতে পারি কিন্তু নাগরিক হিসাবে ততোটা সহজে মানতে পারি না। নাগরিক হিসাবে আমাকে একটা প্রশ্ন করতেই হয়—সত্য কি? মিথ্যা কি?
নাট্যশিল্পে সত্য সবসময়ই অধরা থেকে যায়। তুমি কখনোই সত্যকে খুঁজে পাবে না কিন্তু তোমাকে সবসময় সত্যান্বেষী হতেই হবে। সত্য আবিষ্কারের স্পৃহা তোমাকে সবসময় একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে আবদ্ধ করে রাখবে। তুমি শুধু সন্ধান চালিয়ে যাও। অভিযানের অন্ধকার পথে তুমি হয়তো সত্যের সঙ্গে একটা হোঁচট খেতেও পারো, জোরে একটা ধাক্কা লাগতেও পারে, হয়তো একটা আবছায়া, একটা অস্পষ্ট অবয়ব দেখতেও পারো। এটা হতে পারে সত্য কিংবা সত্য সাদৃশ্য কিছু। সত্যের দেখা মিলে গেলে, সত্যকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও তুমি নিশ্চিত হতে পারবে না যে, যা পেয়েছো তাই সত্য কি না। নাট্যশিল্পের মাধ্যমে সত্যকে জানার মতো কোন কার্যকরী উপায় নেই। সত্যের বহুরূপ। এই সত্যগুলো একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, একটি আরেকটিকে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়িয়ে রাখে, একে অন্যকে প্রতিফলিত করে, একজন আরেকজনের পিছনে লেগে থাকে এমনকি কখনো কখনো একে অন্যকে দেখতে বা জানতেই পারে না। তোমার মাঝে মাঝে মনে হবে সত্যকে পাওয়ার সেই সুবর্ণ মুহূর্তে পৌঁছে গেছো কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ তোমার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে যাবে আর সত্যকে তুমি হারিয়ে ফেলবে।
আমার কাছে প্রায়ই জানতে চাওয়া হয় আমি এ পর্যন্ত কতোগুলা নাটক লিখেছি। আমি ঠিক হিসাব করে সংখ্যাটা বলতে পারি না। শুধু বলি আমার নাটকে এই এই ঘটনা আছে। নাটকের চরিত্ররা এই এই বলেছে, এটা এটা করেছে। অধিকাংশ নাটকের ভাবনা ও প্রেরণা কোন একটা বাক্য, একটা শব্দ বা একটা সামান্য ছবি থেকে উৎসারিত হয়েছে। হয়তো প্রথমে একটা শব্দ মাথায় এলো তারপর ওই শব্দ থেকে ধীরে ধীরে একটা চিত্র মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। আমি দুটো বাক্যের দুটো উদাহরণ দিবো যেটা আকস্মিকভাবে আমার মনে উদয় হয়েছিল। ঠিক পর-মুহূর্তে তার একটা ছবি আমার আমাকে তাড়া করে বেরিয়েছে।
নাটক দুটির একটি হলো ‘হোমকামিং’ এবং অন্যটি হলো ‘ওল্ড টাইমস’। হোমকামিংয়ের প্রথম লাইন ছিল ‘কাঁচিটা কোথায় রেখেছো?’ এবং ‘অন্ধকার’ ছিল ওল্ড টাইমসের প্রথম শব্দ। দুটো ক্ষেত্রেই একটি বাক্য বা একটি শব্দ ছাড়া আমার কাছে আর কোন তথ্য ছিলো না। আমার একদমই কোন ধারণা ছিলো না এরপর কি লিখবো।
প্রথম ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে কেউ একজন একটা কাঁচি খুঁজছিল। কাঁচিটা কি চুরি হয়েছে? কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে এটা ভেবেই মন অশান্ত হয়ে উঠছিল। তবে আমার মন এটা জানতো যে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সে যেমন জানে না তেমনি সন্দেহকারী নিজেও জানে না কাঁচিটা কোথায় আছে।
‘অন্ধকার’ শব্দটা দিয়ে আমার মনে একগুচ্ছ নিকষ কালো চুলের ছবিই ভেসে এসেছিল। কার চুল হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে একজন নারীর চুলের কথাই মনে আসছিল। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমি এদের সম্পূর্ণ ছবিটা না জেনে স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমার দৃশ্যকল্পনা উন্মুক্ত হয়ে যেতো। খুবই বিবর্ণ একটা অবয়ব দিয়ে শুরু হতো তারপর ধীরে ধীরে তার একটা ছায়া আলোতে আসতো।
শুরুতে আমি চরিত্রগুলোকে কোন নামবাচক বিশেষ্য দিতাম না বরং এ, বি কিংবা সি-এর মতো অক্ষর দিয়ে রাখতাম।
‘হোমকামিং’ নাটকের বেলায় আমি দেখলাম একজন লোক একটি খালি বৈঠকখানায় ঢুকলো। জীর্ণ সোফায় বসে রেসকোর্স ময়দানের পত্রিকা পড়ছিল আর এক তরুণকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। আমার মনে হলো প্রথম লোকটা মানে ‘এ’ হলো বাবা আর অল্পবয়সী ছেলেটি মানে ‘বি’ হলো তার ছেলে। কিন্তু তখনও আমি ঠিক করিনি আমার নাটকে তারা পিতা-পুত্রই হবে কিনা। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম ‘বি’ (যার নাম পরে লেনি হবে) ‘এ’-কে (যার নাম পরে ম্যাক্স হবে) বলছে, ‘বাবা, আমি যদি অন্য কোন বিষয় নিয়ে কথা বলি তুমি কি কিছু মনে করবে? আমি তোমার কাছে একটা বিষয়ে কিছু জানতে চাচ্ছি। আমরা রাতে ডিনারে যা খেলাম তার নাম কি? কি বলে ডাকো? তুমি কেন একটা কুকুর কিনছো না? তুমি তো কুকুর খাদ্য ভালো রান্না করতে পারো। এতো এতো কুকুরের জন্য রান্না করো।’ যেহেতু বি এ-কে বাবা বলে ডেকেছে তাই এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে তারা পিতা-পুত্র। এটা পরিষ্কার যে ‘এ’ একজন রাধুনি এবং তার রান্নার তালিকাকে ততোটা মূল্য দেয়া হয় না। এটা কি এটাও ইঙ্গিত দেয় যে ছেলেটির মা নেই? আমি তখনও জানতাম না। আমি প্রায়ই আমার নিজেকে বলতাম, আমাদের শুরু কখনো আমাদের শেষটা জানতে পারে না।
‘অন্ধকার’, একটা বড় খোলা জানালা, সন্ধ্যার আকাশ। একজন পুরুষ এ (যার নাম পরে ডিলি হবে) এবং একজন নারী বি চুপচাপ বসে পান করছিল। পুরুষটি জানতে চাইলো, ‘মোটা নাকি চিকন?’ তারা কি নিয়ে কথা বলছিল? তারপর আমি দেখলাম আরেকজন নারী সি (যাকে পরে অ্যানা নাম দিবো) প্রথম দুজনকে পিছনে রেখে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আবছায়া তৈরি হয়েছে। তার চুলের কালো সন্ধ্যার আধারে মিলিয়ে আছে।
শিল্প সৃষ্টির এই মুহূর্তটি খুবই অদ্ভুত। কাহিনিতে চরিত্রের অস্তিত্ব পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি সেই মুহূর্তগুলো খুব অদ্ভুত রকমের হয়। এই মুহূর্তে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাড়া করে। এমনকি সবকিছুকে অলীক মনে হতে থাকে। একটা অপ্রতিরোধ্য চেতনার ধারা মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এইখানে লেখক সত্তাটা খুবই অদ্ভুত ও অপরূপ মনে হতে থাকে। এক কথায় চরিত্ররা লেখককে সহজভাবে নেয় না। চরিত্ররা লেখকের সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। তাদের নিয়ে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন থাকা যায় না। তাদের সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। নির্দিষ্ট করে তাদের সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। ব্যাপকভাবে বললে লেখক চরিত্রদের নিয়ে অন্তহীন খেলায় লিপ্ত হয়। ইঁদুর-বিড়ালের দৌড়ে জড়িয়ে পড়ে। অন্ধের লুকোচুরি খেলার মতো। তারপর একসময় তুমি রক্ত মাংসের চরিত্রের দেখা পাবে। যারা স্বাধীন ইচ্ছায় জীবন কাটাতে চায়। নিজস্ব একটা পরিচয় গড়ে তুলতে চায়। এমন মানব সত্তা যাকে লেখক নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তন, পরিচালনা বা বিকৃত করতে পারে না।
রাজনৈতিক মঞ্চ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। যে কোন উপায়ে লেখায় উপদেশবাদী মনোভাব এড়িয়ে যেতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটা আবশ্যক। লেখকের ইচ্ছায় চরিত্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করা যাবে না। তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বেড়ে ওঠার অবকাশ দিতে হবে। লেখকের নিজের রুচি, সংস্কার ও মানসিক অবস্থা দিয়ে চরিত্রের বিকাশকে সীমিত করা যাবে না, অবরুদ্ধ করা যাবে না। সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্র সৃষ্টির জন্য লেখককে প্রস্তুত হতে হবে। লেখকের প্রভাব মুক্ত হয়ে চরিত্ররা স্বাধীন পথে চলবে এটাই কাম্য
শিল্পের ভাষা খুবই দ্ব্যর্থবোধক। অনেকটা চোরাবালির মতো। যেন দোদুল্যমান চাকতি। একটা বরফজমা হৃদের মতো যার নিচ দিয়ে লেখকের চলার পথ বয়ে গেছে।
পূর্বেই যেমনটা বলেছি, সত্য খুঁজে পাও বা না পাও, সত্যের সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। এই অনুসন্ধান ক্ষণিকের বিরতি নিতে পারে কিন্তু চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। বলা যায় না ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে তুমি সত্যের মুখোমুখি হতেও পারো।
রাজনৈতিক মঞ্চ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। যে কোন উপায়ে লেখায় উপদেশবাদী মনোভাব এড়িয়ে যেতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটা আবশ্যক। লেখকের ইচ্ছায় চরিত্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করা যাবে না। তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বেড়ে ওঠার অবকাশ দিতে হবে। লেখকের নিজের রুচি, সংস্কার ও মানসিক অবস্থা দিয়ে চরিত্রের বিকাশকে সীমিত করা যাবে না, অবরুদ্ধ করা যাবে না। সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্র সৃষ্টির জন্য লেখককে প্রস্তুত হতে হবে। লেখকের প্রভাব মুক্ত হয়ে চরিত্ররা স্বাধীন পথে চলবে এটাই কাম্য। তবে এটা সবসময় কার্যকর নয়। রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা এই প্রত্যাশিত শিল্প নীতিগুলো মেনে চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এর জন্য উপযুক্ত তবে প্রত্যাশিত শিল্প নীতির বিপরীত নীতি প্রয়োগ করে।
আমার ‘বার্থডে পার্টি’ নাটকে একটা নির্দিষ্ট অংকে স্থির হওয়ার আগে আমি নাট্যশৈলীর গভীর অরন্যের সকল সম্ভাব্য উপায়কে যাচাই করে দেখছি।
‘মাউন্টেইন ল্যাংগুয়েজ’-এ আমি এমন করে দেখার জন্য ততোটা উৎসাহ দেখাই নাই। তাই এটা কদাকার, সংক্ষিপ্ত ও তুচ্ছ নাটকের উদাহরণ হিসাবে গন্য হচ্ছে। তবুও নাটকের সৈন্যরা ‘মাউন্টেইন ল্যাংগুয়েজ’ থেকে কিছু উপভোগ্য নির্যাস নিংড়ে নিচ্ছে। অনেকেই ভুলে যায় যে যাতনা ও বিষাদেরাও নিজেদের পুনরাবৃত্তিতে নিজেরাই একঘেয়ে অনুভব করে। তাদেরকেও সজীব রাখার জন্য মাঝে মাঝে কৌতুক ও হাস্যরসের মাত্রা যোগ করতে হয়। ইরাকের আবু গারিবের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ‘মাউন্টেইন ল্যাংগুয়েজ’ মাত্র ২০ মিনিটের দীর্ঘ নাটিকা। কিন্তু তুমি একে ঘন্টার পর ঘন্টা চালাতে পারবা। শেষ হয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে চালিয়ে গেলেও মনে হবে শেষ হয়নি, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, বারবার।
অন্যদিকে ‘অ্যশেজ টু অ্যশেজ’-এর পটভূমি যেন গভীর জলের নিচে সংঘটিত হয়েছে। একজন ডুবন্ত নারী উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে হাত দুটি উঁচিয়ে রেখেছে। দৃষ্টি সীমার দূরে ভেসে যাচ্ছে, কাউকে আকড়ে ধরার জন্য, কিন্তু কোথাও কেউ নেই, না জলের উপর না জলের নিচে। শুধু ফিকে ছায়া দেখা যাচ্ছে, একটা প্রতিফলন ভেসে যাচ্ছে। জলমগ্ন ভূ-দৃশ্যের মাঝে নারীটির আকৃতি দিগন্তরেখাতে মিশে যাচ্ছে। যে সর্বনাশা নিয়তির শিকার অন্যরা হওয়ার কথা ছিল তা ওই নারীটিকে পোহাতে হচ্ছে। অন্যেরা যেভাবে মৃত্যুর কবলে পড়ছে, তাকেও সেই একই রকম মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।
রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক ভাষা শিল্পভাষার নিয়মনীতি অনুসারে ব্যবহৃত হয় না। সাক্ষ্য প্রমাণ বলে রাজনীতিবিদরা সত্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ভাষাকে ব্যবহার করে না বরং ক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য চাতুর্যপূর্ণ ভাষার আশ্রয় নেয়। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাধারণ জনগণকে অজ্ঞতায় থাকাটা জরুরী। জনগণ যতো সত্য থেকে দূরে থাকবে, এমনকি নিজের যাপিত জীবনের যাতনা থেকে অজ্ঞ থাকবে ততো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য সুবিধা। আমাদের চারপাশ মিথ্যার চাদরে আগাগোড়া ঢেকে রাখা হয়। মিথ্যার বেসাতি আমাদের জীবনের চালক হয়ে উঠে।
উপস্থিত সকলে হয়তো জানেন ইরাক যুদ্ধের ন্যায্যতার পিছনে কেমন রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল। সাদ্দাম হোসেন গণবিধ্বংসী মরণাস্ত্র মজুদ করেছেন যা ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে মারাত্নক ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই তথ্য যে সত্য সে সম্পর্কে আমাদের অকাট্য ভাষায় নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তার কিছুই সত্য ছিল না। আমাদের এটাও বলা হয়েছিল যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের হামলায় আল-কায়দার সঙ্গে জড়িত ছিল। আমাদের এর সত্যতাকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। আমাদের বলা হয়েছে ইরাক বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। আমাদের নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল, এটাই সত্য। কিন্তু আদতে তা সত্য ছিল না।
আমাদেরকে যা জানানো হয় সত্য তার থেকে ভিন্ন। এই বিষয়ে সত্যের কাজ হচ্ছে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কি আর এটা কিভাবে কার্যকর করে তার স্বরূপ উন্মোচন করা।
তাই বর্তমান নিয়ে মূল্যায়ন করার আগে বিগত কিছু দিন আগে ফিরে তাকাতে চাই। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই। আমি মনে করি সেই সময়কে সামান্য পর্যবেক্ষণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।
সবাই জানে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সমগ্র পূর্ব-ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে কি ঘটেছিল। পরিকল্পিত নৃশংসতা, বিস্তৃত ধ্বংসযজ্ঞ এবং স্বাধীন চিন্তার নিদারুণ দমন-পীড়ন ছিল প্রাত্যহিক জীবনের অংশ। সবকিছুই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও নথিভুক্ত করা আছে।
কিন্তু আমার যুক্তি হলো—সেই একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘটিত একই অপরাধ ভাসা-ভাসাভাবে লিখিত হয়েছে। পক্ষপাতমূলকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। একপাক্ষিক স্বীকার করা হয়েছে। শুধু নিপীড়িতরা একে অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে। আমি মনে করি, সময় হয়েছে এই বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বলার। বর্তমান পৃথিবীর এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সত্যকে অস্বীকার করার একটা দায় আছে। শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ থাকার পরও সারাবিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে এই অনুমান করা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কিছু করার পূর্ণক্ষমতা ভোগ করে।
কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রে সরাসরি আক্রমণ বা জবরদখল বা উপনিবেশ সৃষ্টি কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের নীতির তালিকায় ছিল না। তারা ‘সীমিত মাত্রার দ্বন্দ্ব’ নীতিকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ‘সীমিত মাত্রার দ্বন্দ্ব’ নীতি বলতে একবার বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে মহাধ্বংস নয় বরং অল্প সময়ে অল্প লোকের (বড় জোর কয়েক হাজার) মৃত্যুর সংঘটন করা। এর মানে হলো তুমি একটা দেশের হৃদপিন্ডে বিষবৃক্ষ রোপন করে দিয়ে বসে বসে দুর্গন্ধময় ফুলের সমাহার দেখতে উদগ্রীব হয়ে আছো। একদিকে সাধারণ মানুষ নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, যথেচ্ছা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করচ্ছে, অন্যদিকে তোমার প্রিয় বন্ধু, সামরিক সৈন্য কিংবা বহুজাতিক কোম্পানির মুখপাত্র আরামে ক্ষমতায় বসে ক্যামেরার সামনে হেসে হেসে বলছো, ‘গণতন্ত্র অর্জিত হয়েছে। শান্তি ফিরে এসেছে।’ এই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির আসল চিত্র।
নিকারাগুয়ার মর্মান্তিক ইতিহাস হচ্ছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতীত কিংবা বর্তমান সকল সময়ের উত্তম সাক্ষ্য হিসাবে নিকারাগুয়ার ইতিহাসই যথেষ্ট।
১৯৮০ দশকে আমি লন্ডনে আমেরিকান দূতাবাসের একটি সভাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী দলের তহবিলে যুক্তরাষ্ট্রের কগ্রেস অর্থ সরবারহ করবে কি না? এই বিষয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। আমি এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে নিকারাগুয়ার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলাম। কিন্তু প্রতিনিধি সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ফাদার জন মেটকাফ। যুক্তরাষ্ট্রের সভাসদের মুখপাত্র ছিলেন রেমন্ড জাইৎস (পরবর্তীতে নিজেই রাষ্ট্রদূত হন)। ফাদার মেটকাফ বলেছিলেন, ‘জনাব, আমি উত্তর নিকারাগুয়ার যাজক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমার যাজকবৃন্দ একটা বিদ্যালয়, একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। আমরা মোটামুটি শান্তিতে বসবাস করছি। কয়েক মাস আগে একটা বিদ্রোহী দল আমাদের অঞ্চলে কোন কারণ ছাড়াই আক্রমণ করেছে। তারা সব ধ্বংস করে দিয়েছে, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তারা হাসপাতালের নার্স ও শিক্ষকদের ধর্ষণ করেছে। ডাক্তারদের নির্বিকারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তারা যেন আদিম বর্বর হয়ে উঠেছিল। আমার আবেদন এই যে, অনুগ্রহ করে আমেরিকা সরকার যেন এমন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে তাদের সমর্থন বন্ধ করে দেয়।’
রেমন্ড জাইৎস একজন সুবিবেচক, দায়িত্ববান ও সর্বোচ্চ সজ্জ্বন মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বিশ্বের কূটনৈতিক চক্রে তিনি খুব সম্মানিত ছিলেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, কিছু সময় নীরব হয়ে রইলেন। তারপর গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, ‘ফাদার, আপনাকে একটা কথা বলি। যুদ্ধে নিরীহ মানুষ সবসময় কষ্ট ভোগ করে।’ কথাটা শেষ হতেই চারপাশটা যেন বরফ শীতল নীরবতায় অবশ হয়েছিল। আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার মধ্যে অনুশোচনার কোন রেশই দেখলাম না। নিরীহ মানুষ সবসময় কষ্ট ভোগ করে, সত্যি তো!
অবশেষে একজন বললো, “কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘নিরীহ মানুষেরা’ এক ভয়াবহ নৃশংসতার শিকার হচ্ছে। একজন নয় অসংখ্য। যদি মার্কিন কংগ্রেস এই বিদ্রোহী সন্ত্রাসী দলকে আর্থিক সহায়তা প্রদান বজায় রাখে তাহলে আরো বিপুল পরিমাণ নৃশংসতা সংঘটিত হবে। আসল ঘটনা কি এটাই না? একটি স্বার্বভোম রাষ্ট্রের নিরীহ জনগণের ওপর আপনাদের সরকারের সমর্থনের কারণে যদি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। তার জন্য আপনারা কি দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত হবেন না?”
জাইৎস নিতান্তই অবিচল ছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমি মনে করি না যে সব তথ্য ও বর্ণনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।’
দূতাবাস ছেড়ে আসার সময় একজন মার্কিন সহকারী আমাকে বললো সে আমার লেখা নাটকগুলো নিয়মিত পড়ে ও উপভোগ করে। আমি তার মন্তব্যের কোন প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিলাম।
আমি আরো মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সে সময় রাষ্ট্রপতি রেগান গর্ব করে বলেছিলেন, ‘নিকারাগুয়ার বিদ্রোহীরা আমেরিকান জাতির পিতাদের নৈতিক চেতনার সমতুল্য।’
যুক্তরাষ্ট্র প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নিকারাগুয়ার নৃশংস সমোঝা স্বৈরতন্ত্রের অবিরাম সমর্থক ছিল। ১৯৭৯ সালে স্যান্ডানিস্তা দলের নেতৃত্বে নিকারাগুয়ার গণ বিপ্লবের মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্যবাদী দলকে পরাজিত করে।
স্যান্ডানিস্তারাও নিঁখুত ছিল না। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ অজ্ঞতা ছিল এবং তাদের রাজনৈতিক দর্শন নানামুখী দ্বান্দ্বিক উপাদানে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু তারা ছিলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সভ্য। তাদের লক্ষ্য ছিল একটি সুযোগ্য ও বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা হয়েছিল। লক্ষাধিক দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। প্রায় এক লক্ষ পরিবারকে জমির মালিকানা প্রদান করা হয়েছিল। দুই হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষরতার ক্যাম্পেইন চালিয়ে নিরক্ষরতার হারকে এক-সপ্তমাংশের নিচে কমিয়ে আনা হয়েছিল। বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। শিশু মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করেছিল। পোলিও পুরোপুরি নির্মূল করা হয়েছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব অর্জনকে মার্ক্সবাদী/লেনিনবাদের পরাভব বলে বাতিল করে দিয়েছিল। মার্কিন সরকারের মতে নিকারাগুয়া একটি বিপজ্জনক উদাহরণ ও হুমকি হয়ে উঠেছিল। নিকারাগুয়া যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতার মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করে সফল হয়। যদি স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার মানদন্ড নির্ধারণ করে কার্যকরী করে তোলে। যদি সামাজিক ঐক্য ও জাতীয় আত্ম-মর্যাদা অর্জন করে ফেলে। তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও একই প্রশ্ন তুলে একই কাজ করতে চাইবে। সেই সময় এল সালভাদর মার্কিন সমর্থিত প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।
আমি শুরুতেই বলেছিলাম, আমরা ‘মিথ্যার চাদর’ দিয়ে অবরুদ্ধ থাকি। রাষ্ট্রপতি রিগান নিকারাগুয়াকে ‘একত্ববাদের অন্ধকূপ’ বলে অভিহিত করেন। গণমাধ্যম ও বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার রিগানের এই মতকে সঠিক ও সুন্দর মন্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে স্যান্ডানিস্তা সরকারের অধীনে কোন ডেথ স্কোয়াডের খোঁজ মিলেনি। অত্যাচার ও নিপীড়নের কোন নথি মিলেনি। পদ্ধতিগত ও সরকার সমর্থিত কোন সামরিক নৃশংসতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নিকারাগুয়াতে কোন ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়নি। বরং সরকারের ভিতর তিনজন পুরোহিত অঙ্গীভূত ছিল। দুজন জেসুইটস ও একজন মেরিকনল মিশনারি। একচ্ছত্রবাদের অন্ধকূপ মূলত পার্শ্ববর্তী দেশ এল সালভাদর ও গুয়েতেমালায় বিরাজ করছিল। মার্কিন সরকার ১৯৫৪ সালে গুয়েতেমালার গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। পরিসংখ্যান মতে পরবর্তী সামরিক একনায়কতন্ত্রের হাতে প্রায় দুই লক্ষের অধিক লোক নৃশংসতার শিকার হয়েছিল।
১৯৮৯ সালে সান সালভাদরের কেন্দ্রীয় আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবী স্বনামধন্য ছয় জন জেসুইটস আলকাটল রেজিমেন্টের ব্যাটেলিয়নের হাতে নির্মমভাবে মারা পড়েছিল। এই আলকাটল রেজিমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিংয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। দুঃসাহসিক আর্চ বিশপ রোমেরো সমবেত প্রার্থনা করার সময় গুপ্ত হত্যার শিকার হন। প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল। তাদের কেন হত্যা করা হয়েছিল। কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে একটা সুন্দর জীবন-যাপন করা সম্ভব এবং মর্যাদাবান জীবন অর্জন সম্ভব। তাদের এই বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ তাদের সমাজতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেছিল। তারা মারা গিয়েছিল কারণ তারা প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। অশেষ দারিদ্রতার মালভূমি, রোগ বালাইয়ের অবিরাম প্রাদুর্ভাব, অবক্ষয় আর অত্যাচার ভোগ করাকে তাদের জন্মগত অধিকার বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।
অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র স্যান্ডানিস্তা সরকারকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছিল। টানা কয়েক বছর ধরে প্রতিরোধ, নিরবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, নিপীড়ন ও ত্রিশ হাজার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিকারাগুয়ার প্রাণশক্তি পরাজয় বরণ করে। তারা আবারো পরিশ্রান্ত ও দারিদ্র পীড়িত হয়ে পড়েছিল। দেশটা আবার জুয়ার আস্তানা হয়ে উঠেছিল। বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্য সেবার দিন শেষ হয়ে এসেছিল। প্রতিহিংসা নিয়ে পূর্বের অপশাসন ফিরে এসেছিল। ‘গণতন্ত্র’ সত্যি বিজয়ী হয়েছিল!
মার্কিন এই নীতি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় আমেরিকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। সারাবিশ্বে বন্য আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নীতির কোন শেষ ছিল না। নীতিগুলো এমন ভাবে কাজ করতো যেনো মনে হতো এটা কখনো ঘটেনি।
যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়ার সকল ডানপন্থি সামরিক স্বৈরশাসনকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। এমনকি কখনো কখনো স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। আমি কয়েকটা দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, যেমন—ইন্দোনেশিয়া, গ্রিস, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, হাইতি, তুরস্ক, ফিলিপাইনস, গুয়েতেমালা, এল সালভাদর এবং অবশ্যই চিলির নাম নিতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩ সালে চিলিতে যে ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করেছিল তার ক্ষতিপূরণ কোন কিছুতেই শেষ হবে না। সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না।
এই দেশগুলোর লক্ষাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এগুলো যে ঘটেছিল তার কোন প্রমাণ আছে? এই মৃত্যুর বিভীষিকা কি মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো—হ্যাঁ, এই সকল ঘটনা বাস্তবিক অর্থে ঘটেছিল। এসব নৃশংসতা মার্কিন বিদেশ নীতিতে নিহিত। কিন্তু তুমি তার জানো না কিছু। তোমাকে জানতে দেয়া হয়নি। তোমাকে সত্যের থেকে বহু দূরে ও মিথ্যার খুব কাছাকাছি রেখে দেয়া হয়েছে।
এই ঘটনাগুলো কখনো ঘটেনি। কখনো ঘটেইনি। এমনকি যখন এগুলো ঘটছিল তখনও ঘটেনি। যেন এটা কোন ব্যাপার না। এই বিষয়টা জানতে কেউ কখনো চেষ্টা করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় ও অপরাধগুলো খুবই নিয়মতান্ত্রিক, অপরিবর্তনীয়, নিষ্ঠুর ও অনুতাপহীন। কিন্তু খুব অল্পলোকই এই বিষয়ে আওয়াজ তুলেছে। উল্টো সব ব্যাপারে আমেরিকার কাছে হাত পাততে হয়। আমেরিকা একদিকে যেমন সারা দুনিয়াতে ঠান্ডা মাথায় ভাবলেশহীনভাবে আত্মস্বার্থের জন্য সবাইকে ব্যবহার করে অন্যদিকে নিজেকে বিশ্বশান্তির শক্তি হিসাবে ছদ্মবেশ ধারন করে। আমেরিকার এই স্বভাবটা খুবই হাস্যরসাত্মক। সম্মোহনের এক সফল উদাহরণ।
একজন লেখকের জীবন খুবই নাজুক, খোলা আকাশের মতো নগ্ন বলা যায়। কিন্তু এটা নিয়ে লেখককে হাহুতাশ করলে চলবে না। লেখক নিজের ইচ্ছায় এমন জীবন বেছে নেয় আর বাকিটা জীবন এই চক্রে আটকে থাকে। এটা বলা ভুল হবে না যে, সকল মতের হাওয়া তোমার জন্য উন্মুক্ত, কিছু হাওয়া থাকবে হিমশীতল। তোমাকে নিজ দায়িত্বে বাইরের পৃথিবীতে হাঁটতে হবে। হয়তো তুমি কোন আশ্রয় পাবে না, কোন নিরাপত্তা পাবে না।
নিঃসন্দেহে আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দর্শনীয় ব্যাপার। হতে পারে সে নিষ্ঠুর, নির্বিকার, ঘৃণ্য ও পাশবিক কিন্ত সে খুব বুদ্ধিমান ও চালাকও বটে। যদি আমেরিকাকে একজন বিক্রয়কর্মী ধরে নেই তাহলে আমেরিকার সবচেয়ে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হলো আত্মপ্রেম। তাই সবকিছুতই আমেরিকা সফল হয়। আমেরিকার প্রতিটি প্রেসিডেন্ট টেলিভিশনে কি বলে শুনে দেখেন। ‘আমেরিকার জনগণ’, তাদের প্রত্যেকটা বাক্যে এই শব্দবন্ধটার রেশ থাকে। ‘আমি আমেরিকান জনগণকে বলবো এখন সময় প্রার্থনা করার যাতে আমেরিকার জনগণের অধিকারকে রক্ষা করতে পারি। আমি আমেরিকান জনগণকে অনুরোধ করবো তারা যেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উপর ভরসা রাখে যাতে তিনি আমেরিকার জনগণের জন্য যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতে সফল হন।’
আমেরিকা খুব চটকদার কৌশল অবলম্বন করতে দক্ষ। রাজনৈতিক ভাষা দিয়ে মানুষের ভাবনাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারে। ‘আমেরিকার জনগণ’ শব্দদ্বয় সত্যি করে আমেরিকার জনগণের মনে নরম বালিশের মতো মোলায়েম আশ্বাসের একটা ইন্দ্রিয়সুখ দিতে সক্ষম। তোমাকে তেমন চিন্তা করতে হবে না। তুমি শুধু সেই নরম তুলতুলে বালিশে গা এলিয়ে শুয়ে থাকলেই হবে। এই বালিশ হয়তো তোমার স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা ও বিবেক-বিবেচনার গলা চেপে ধরবে কিন্তু তোমাকে নিরিবিচ্ছিন্ন আরামে রাখবে। অবশ্য এই সুখানুভূতি আমেরিকার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করা ৪০ মিলিয়ন মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সুবিশাল গুলাগ বন্দিশিবিরে মানবেতর জীবন কাটানো ২ মিলিয়ন নারী পুরুষের জন্য কার্যকর নয়।
আমেরিকা তার ‘সীমিতমাত্রার দ্বন্দ্ব’ নীতি নিয়ে তেমনটা আর ভাবে না। মিতবাক ও সংযমী হওয়ার কোন চাপ নেয় না। এমনকি প্রতারণামূলক কৌশলের জন্য লজ্জিত নয়। আমেরিকা কোন ভয় বা কৃপার অনুভূতি ছাড়াই তার তুরুপের তাস টেবিলে রেখে খেলতে থাকে। জাতিসংঘের নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আইন বা সুচিন্তিত ভিন্নমতকে সে কোন আমলেই নেয় না। বরং এগুলোকে সে আমেরিকার স্বার্থের জন্য অন্তঃসারশূন্য ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। আমেরিকার নেতৃত্বের পিছনে উল্লাসকারী হিসেবে আছে মিনমিনে স্বভাবের একটা মেষশাবক, গোবেচারা গোছের মেরুদন্ডহীন গ্রেট ব্রিটেন।
তাহলে আমাদের নৈতিক চেতনার কি হবে? এই নৈতিক শক্তি কি সত্যি আমাদের ছিল? নৈতিক চেতনা দিয়ে আমরা আসলে কি বোঝাই? এটা দিয়ে কি আমরা বিবেককে বোঝাই যা আজকের এই অস্থির সময়ে খুব কমই কাজ করে? বিবেক শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের কাজের মানদণ্ড নয় বরং অন্যদের কাজের মধ্য আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বকেও নির্দেশ করে। বিবেক কি সত্যিই পৃথিবী থেকে নাই হয়ে গেছে? গুয়ানতানামো বে-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন। শতশত মানুষ কোনরকম মামলা ছাড়াই তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক আছে। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন আইনি প্রতিনিধি নাই কিংবা কোন আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নাই। বলা যায় অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের বন্দি করে রাখা হয়েছে। হাস্যকরভাবে এই সম্পূর্ণ অবৈধ কাঠামোটি জেনেভা কনভেশনের নীতি রক্ষার নামে চালিয়ে যাচ্ছে। এটা যে শুধু সহ্য করেই যেতে হচ্ছে তা নয়। বরং ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়’ বলে একটা কিছু আছে তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। একদিকে দিনের পর দিন তারা এই বেআইনি নারকীয় তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নিজেদের ‘মুক্ত বিশ্বের নেতা’ হিসাবে প্রচার করচ্ছে। তুমি কি কখনো গুয়ানতানামো বে এর অধিবাসীদের কথা ভেবেছো? গণমাধ্যম তাদের নিয়ে কি বলে? সংবাদ মাধ্যমে গুলো ছয় নাম্বার পাতায় ছোট একটা প্রতিবেদন নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়। তাদেরকে এমন একটা পোড়ো জমিতে পাঠানো হয়েছে যেখান থেকে তারা কখনো স্বভূমিতে ফিরবে কিনা অনিশ্চিত। বর্তমানে অনেক বাসিন্দারাই অনশন ধর্মঘটে আছে যাদের জোরপূর্বক খাওয়ানোর কর্মসূচি চলচ্ছে। অনশন দলে ব্রিটিশ অধিবাসীরাও আছে। জোরপূর্বক খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াও যথার্থভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে না। কোন চেতনানাশক বা ব্যথা প্রশমনকারী ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে না। নাকের ছিদ্র দিয়ে একটা নল ঢুকিয়ে সোজা গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এতে ক্ষুধা নিবারণের বদলে রক্তবমির উদ্রেক হচ্ছে। এটা অত্যাচারের আরেক মাত্রার সংযোজন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে কি কিছু বলেছে? কিছুই বলেনি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কি কোন বক্তব্য দিয়েছে? কিছুই বলেনি। কেন বলেনি? কারণ যুক্তরাষ্ট্র হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ‘গুয়ানতানামো বেতে আমাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করা এক প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ।’ গুয়ানতানামো সমালোচনা মানে হয় তুমি আমেরিকার সঙ্গে আছো না হয় তুমি আমেরিকার বিরুদ্ধে আছো। ব্লেয়ার তোমার চুপ থাকাই শ্রেয়।
ইরাকে সামরিক অভিযান ও আক্রমণ একটা লুটেরা কাজ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের নির্লজ্জ উদাহরণ। আন্তর্জাতিক আইনের ধারণাকে চরম অবজ্ঞা করার একটা নিকৃষ্ট ঘটনা। এই আক্রমণ মিথ্যার পর মিথ্যা দিয়ে গড়া এক সামরিক স্বেচ্ছারিতা। গণমাধ্যম সর্বোপরি বিশ্ববাসীর সঙ্গে স্থূল ও কদর্য প্রতারণা। কোন বৈধ ও যৌক্তিক কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়ে ইরাকে সাদ্দামের অপশাসন থেকে মুক্ত করা এবং বিশ্ব নিরাপত্তা রক্ষার মুখোশের আড়ালে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ও সামরিক শক্তিকে একত্রিত করার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যে এই অভিযান। আমেরিকার সামরিক শক্তির এই ছলনাময় চরিত্র লক্ষাধিক নিরীহ ইরাকিকে বিকালঙ্গ করে দিয়েছে। বহু ইরাকীকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।
আমেরিকা ইরাকি জনগণকে মৃত্যু, দুর্দশা, অধঃপতন, নির্বিচারে এলোপাতাড়ি হত্যা, ইউরেনিয়ামের বিস্তার, গুচ্ছ বোমার বর্ষণ ও অমানবিক অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। তবুও তারা প্রচার করছে, ‘মধ্যপ্রাচ্যে তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।’
গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী হওয়ার জন্য ঠিক কতো মানুষ হত্যা করতে হয়? এক লক্ষ? নাকি তারও বেশি? আমি ভাবতাম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। তাই ন্যায়বিচার প্রতিস্থাপন করার জন্য বুশ ও ব্লেয়ারকে আন্তর্জাতিক আদালতের আসামি করে বিচারের মুখোমুখি করা যর্থাথ নয় কি? বুশ খুবই চতুর আছেন তাই তিনি আন্তর্জাতিক আদালতকে সমর্থন করা থেকে বিরত ছিলেন। যদি কোন আমেরিকান সৈনিক বা মার্কিন রাজনীতিবিদকে এর সমর্থক দলে দেখতেন তাদের তিনি হুঁশিয়ারি দিতেন যে সোজা সমুদ্রবাসে পাঠাবেন। কিন্তু টনি ব্লেয়ার এই আদালতকে অনুমোদন করেছেন তাই তাকে আইনানুগ বিচারের কাঠগড়ায় ওঠাতে বাধা নেই। আমরা বরং আন্তর্জাতিক আদালতকে তার ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারি। এটা হচ্ছে—১০ ডাউনিং স্ট্রিট, লন্ডন।
এখন যে প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলবো তাতে মৃত্যুর ব্যাপারটি অপ্রাসঙ্গিক। বুশ ও ব্লেয়ার মৃত্যুকে অগোচরে রেখে এসেছেন। ইরাকি সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভের পূর্বেই আমেরিকান বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কমপক্ষে এক লক্ষ ইরাকিকে হত্যা করা হয়েছে। কালের চিত্রপটে ওই মানুষগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের অস্তিত্ব জগতের স্মৃতির মন্ডল থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে। তারা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। তারা যে মারা গেছে তারও কোন রেকর্ড নেই। আমেরিকার সেনাপ্রধান টমি ফ্রাংক তো বলেই দিয়েছেন, ‘আমরা মৃতদেহের হিসাব রাখি না।’
সামরিক অভিযানের শুরুতে ব্রিটিশ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় একটি চটকদার আলোকচিত্র ছাপা হয়েছিল যেখানে টনি ব্লেয়ারের গালে একটা ছোট্ট ইরাকি বাচ্চা চুমো দিচ্ছিল। ছবিটার শিরোনাম ছিল—‘এক কৃতজ্ঞ বালক।’ তার ঠিক কয়েক দিন পর ওই একই পত্রিকার ভেতরের পাতায় হাতবিহীন চার বছর বয়সী এক বালকের ছবিসহ একটা গল্প ছাপা হয়েছিল। এলাকায় বালকটি একমাত্র বেঁচেছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আমি আমার হাত কবে ফেরৎ পাবো?’ গল্পটাকে পরে ছেঁটে বাদ দেয়া হয়েছিল। টনি ব্লেয়ার বালকটিকে তার কোলে তুলে ছবি তুলতে দেখা যায়নি। অন্য কোন বিকালঙ্গ শিশু এমনকি রক্তাক্ত মৃতদেহের কোন ছবির সঙ্গে তাকে পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায়নি। রক্ত খুবই ক্লেদযুক্ত জিনিস। তুমি যখন টেলিভিশনের পর্দায় আন্তরিকতা নিয়ে মন ভুলানো বক্তব্য রাখো তখন তোমার শার্ট ও টাইয়ে রক্তের ময়লা দাগ দেখা যায়।
২০০০ আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু জাতির জন্য লজ্জাজনক। তাদের কফিনগুলো রাতের আঁধারে কবরস্থানে পাঠানো হয়েছিল। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান খুব সঙ্গোপনে করা হয় যেন কোন অপকর্ম চোখের আড়ালে রাখতে চাচ্ছে। বিকালাঙ্গ মানুষগুলো তাদের বিছানায় পচতে পচতে মরেছে। কেউ কেউ তো বাকিটা জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেঁচেছে। তার মানে মৃত ও জীবিত উভয়ে পচন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে। একজন মাটির উপর তো অন্যজন মাটির নীচে।
এখানে এসে আমি পাবলো নেরুদার ‘আমি কিছু বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই’ কবিতার নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনাবো।
তারপর একদিন ভোরে সবকিছু জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল,
একদিন সকালের অগ্ন্যুৎসব
ভূমিতল ছেড়ে এক লাফে উঠে এসে,
এক একটা করে মানুষ গ্রাস করছিল,
তারপর অগ্নিশিখা, বারুদের উত্তাপ,
রক্তের লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ছিল।
উড়োজাহাজ ভরা লুটেরা আর মূরগণ
অঙ্গুলি পরা লুটেরা রাজকন্যারা
আশীর্বাদ বর্ষণকারী লুটেরা খ্রিস্ট ভিক্ষুগণ
আসমান পাড়ি দিয়ে শিশুদের মারতে এসেছিল
শিশুদের রক্তের নদী শহরের পথ প্লাবিত করছিল
হায়! কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, শিশুদের রক্তের প্রতি।
শিয়াল, ওই ধূর্ত শিয়াল তোমায় ঘৃণাভরে দেখবে
প্রস্তরখণ্ডের ওই শুকনো কাঁটা তোমায় কামড়ে ধরবে,
উগড়ে ফেলবে,
সাপ, ওই বিষধর সাপের দংশনে তুমি হবে জর্জরিত।
মুখোমুখি দেখেছি দুজনে রক্তের
স্প্যানিশ দূর্গ জোয়ারের জলে
দম্ভের ঢেউ আর ছুরির ধারালো ঢেউয়ে
তোমারে ডোবাচ্ছে।
বিশ্বাসঘাতক
সেনানায়কেরা:
দেখা, আমার এই পোড়া বাড়ি,
হাড়ভাঙ্গা এই স্পেনের দিকে তাকাও:
ঘরে ঘরে জ্বলন্ত ধাতুর স্রোত বয়ে যায়
ফুলের বদলে
স্পেনের প্রতিটা কোটর থেকে
আরেকটা স্পেন ফুটে উঠছে
প্রতিটা মৃত শিশুর শরীর থেকে চোখওয়ালা রাইফেল
প্রতিটা অপরাধ থেকে একটা করে বুলেট জন্ম নিচ্ছে
বুলেটগুলো একদিন ঠিকঠিক
তোমাদের হৃদপিন্ডের মধ্যমনি খুঁজে নেবে।
তোমরা হয়তো জানতে চাইবে: তার কবিতায়
কোন স্বপ্নের কথা বলে না কেন? কিংবা নতুন পাতার কথা
স্বদেশের সেই সব আগ্নেয়গিরির জিঘাংসার কথা।
এসো, দেখে যাও পথের রক্তের দাগ
এসো, আর দেখে যাও
পথের রক্তের ছাপ
এসো, দেখে যাও রক্ত বয়ে যায়
পথে থেকে পথে!
একটা বিষয় আগে স্পষ্ট করে বলে নেই। নেরুদার কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমি স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের তুলনা একেবারই করছি না। নেরুদার কবিতাটির প্রসঙ্গটা টানলাম কারণ সমকালীন কবিতায় বেসামরিক নাগরিকদের উপর বোমা বর্ষণের এমন শক্তিশালী আবেগতাড়িত বর্ণনা আর কোথাও পড়ি নাই।
আমি আগে যেমন বলেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্র তার সব অভিপ্রায় প্রকাশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ খোলামেলা। এটাই সত্য। ‘পূর্ণ আধিপত্যের বর্ণচ্ছটা’ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঘোষিত নীতি। এটা আমার সৃষ্ট পদবাচ্য নয় তাদের নিজেদের। পূর্ণ আধিপত্যের বর্ণচ্ছটা মানে হলো আকাশ, বাতাস, মাটি ও জলে যতো সম্পদ আছে সবকিছুতে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বের ১৩২ টি দেশের মধ্যে ৭০২ টি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। অবশ্য বিশেষ সম্মাননায় সুইডেনকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আমরা জানি না যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে কিভাবে এই সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করে কিন্তু তারা সব জায়গায় বিরাজমান।
যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৮০০০ সচল ও পরিচালন সক্ষম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণ মুখের মালিক। ২০০০ ক্ষেপণাস্ত্র তাৎক্ষণিক নিক্ষেপযোগ্য যা মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে চালু করতে সক্ষম। ‘বাঙ্কার বাস্টার’ নামে পারমাণবিক শক্তির এক নতুন পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। ব্রিটেন মার্কিন সহযোগী হিসেবে তাদের পারমাণবিক মিসাইল ট্রাইডেন্টকে তেমন পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপন করতে চাইছে। তারা আসলে কাদের দিকে তাক করে রেখেছে? ওসামা বিন লাদেন? তোমার? আমার? জো ডকস? চায়না? প্যারিস? কে জানে কাকে লক্ষ্য করে? আমরা শুধু একটা বিষয় জানি—এটা এক বালখিল্য উন্মাদনা। মরণাস্ত্রের মালিকানা ও পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের হুমকি হলো বর্তমান আমেরিকার রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ীভাবে সামরিক শক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং শীঘ্রই এই নীতি শিথিল করার কোন লক্ষণ নেই।
হাজার হাজর মার্কিন নাগরিক, যদিও তা লক্ষ লক্ষ নয়, যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি নিয়ে লজ্জিত এবং সরকারের এমন কর্মকান্ডে রাগান্বিত। কিন্তু এই প্রতিবাদী দল কোন সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের যে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ও ভীতি কাজ করতো তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আমি জানি প্রেসিডেন্ট বুশের অনেক দক্ষ বক্তৃতা লেখক আছেন কিন্তু আমি নিজে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এই দায়িত্বটা নিতে চাই। আমি চাই নিচের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা তিনি টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে বলবেন।
আমার দেখায় তিনি সবসময় রাশভারী চেহারা নিয়ে থাকেন, মাথার চুল নিপাট করে আচড়ানো, গম্ভীর, বিজয়ীভাব, আন্তরিক, প্রায়ই চিত্তাকর্ষক, মাঝে মাঝে বিরক্তি মাখা হাসি, অদ্ভুত রকম আকর্ষণীয় এবং পুরুষের মতো পুরুষ।
আমরা যখন আয়নাতে নিজেদের দেখি আমরা ধরে নেই আয়নাতে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সঠিক। কিন্তু এক মিলিমিটার সরে যাও দেখবে ছবির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। আমরা মূলত সীমাহীন প্রতিবিম্বের দিকে দেখি। কিন্তু মাঝে মাঝে লেখককে এই আয়নাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেখতে হয় যে আয়নার অন্যপাশে আমাদের সত্য রূপ আমাদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।
ঈশ্বর কল্যাণময়, ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর কল্যাণময়। আমার ঈশ্বর ভালো। বিন লাদেনের ঈশ্বর মন্দ। তিনি খুব নিকৃষ্ট। সাদ্দামের ঈশ্বর খুব নিকৃষ্ট। শুধু তারই কোন ঈশ্বর ছিল না। সাদ্দাম এক বর্বর ছিল। আমরা বর্বর নই। আমরা কোন মানুষের গলা কাটি না। আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমাদের ঈশ্বরও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। আমি বর্বর নই। আমি স্বাধীনতা প্রিয় দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা। আমরা খুবই সহানুভূতিশীল সমাজে বাস করি। আমরা খুব সহানুভূতির সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মানুষ হত্যা করি। আমরা খুব সহানুভূতির সঙ্গে প্রাণনাশক ইনজেকশন দিয়ে মানুষ হত্যা করি। আমরা এক মহান জাতি। আমি কোন স্বৈরশাসক নই। সে একজন বর্বর। আমি নই। সে, শুধুমাত্র সেই বর্বর। তারা সবাই বর্বর। আমি তাদের নৈতিক অভিভাবক। আমার হাতের মুষ্ঠি দেখছো তো? এটাই তোমাদের জন্য আমার নৈতিকতার অস্ত্র। ভালো করে মাথায় রেখো, ভুলে যেও না।
একজন লেখকের জীবন খুবই নাজুক, খোলা আকাশের মতো নগ্ন বলা যায়। কিন্তু এটা নিয়ে লেখককে হাহুতাশ করলে চলবে না। লেখক নিজের ইচ্ছায় এমন জীবন বেছে নেয় আর বাকিটা জীবন এই চক্রে আটকে থাকে। এটা বলা ভুল হবে না যে, সকল মতের হাওয়া তোমার জন্য উন্মুক্ত, কিছু হাওয়া থাকবে হিমশীতল। তোমাকে নিজ দায়িত্বে বাইরের পৃথিবীতে হাঁটতে হবে। হয়তো তুমি কোন আশ্রয় পাবে না, কোন নিরাপত্তা পাবে না। যতোক্ষণ তুমি মিথ্যার আশ্রয় না নাও ততোক্ষণ তোমাকে নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিতে হবে এবং একজন রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে হবে, (আমার এই মতের প্রতিযুক্তি দিতে পারো)।
আজকের এই সন্ধ্যায় আমি কয়েক বার মৃত্যুর কথা বলেছি। তাই আমার নিজের লেখা একটা কবিতা ‘মৃত্যু’ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতি করতে চাই।
মরদেহটা ঠিক কোথায় খুঁজে পেয়েছো?
কে প্রথম দেখেছে লাশ হওয়া মানুষটাকে?
মৃত দেহটা কি মৃতই ছিল যখন পেয়েছো?
কিভাবে খুঁজে পেলে মৃত মানুষটাকে?
কে এই মৃত মানুষ?
কে তার পিতা বা কন্যা বা ভাই
অথবা চাচা বা বোন বা মা বা পুত্র
এই মৃত মানুষটার, এই পরিত্যক্ত শরীরটার?
যখন এই দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলেছে তখনও কি মৃত ছিল?
দেহটা কি পরিত্যক্তই ছিল?
কে ফেলে গেছে এই দেহটা?
শেষকৃত্যের জন্য শরীরের কি কাপড় ছিল নাকি ছিল নিখিল নগ্ন?
কি দেখে তুমি মৃতদেহকে মৃত বলে ঘোষণা করলে?
তুমি কি শবদেহ কে মৃত বলে ঘোষণা করে ফেলেছো?
মৃত মানুষটাকে তুমি কতোটুকু জানো?
তুমি জানলে কি করে মৃত মানুষটা মৃত?
তুমি কি মৃত শরীরটাকে গোসল করিয়েছিলে?
তুমি কি মৃতের দুটি চোখ বন্ধ করেছিলে?
তুমি প্রাণহীন দেহটাকে কবর দিয়েছিলে?
তুমি কি মৃতের কপালে শেষ চুম্বন দিয়েছিলে?
আমরা যখন আয়নাতে নিজেদের দেখি আমরা ধরে নেই আয়নাতে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সঠিক। কিন্তু এক মিলিমিটার সরে যাও দেখবে ছবির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। আমরা মূলত সীমাহীন প্রতিবিম্বের দিকে দেখি। কিন্তু মাঝে মাঝে লেখককে এই আয়নাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেখতে হয় যে আয়নার অন্যপাশে আমাদের সত্য রূপ আমাদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।
আমি বিশ্বাস করি শত শত নির্ভীক, অবিচল ও তুখোর বৌদ্ধিক সংকল্পে ভরা মতভেদের অস্তিত্বই আমাদের জীবনের অকপট সত্যকে আমাদের কাছে উন্মোচন করে। আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমাদের জীবনের উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়। এমন হওয়াটা বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।
যদি ওই একই রকম দৃঢ় সংকল্প আমাদের রাজনৈতিক দূরর্দশিতায় অঙ্গীভূত না করা হয় তাহলে আমরা যে মানুষের মর্যাদা হারিয়েছি তাকে পুনরুদ্ধার করার আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।
মূল কপিরাইট © Nobel Prize Foundation 2005
বাংলা কপিরাইট © Pratidhwanibd.com
উৎস লিংক: Harold Pinter–Nobel Lecture–NobelPrize.org








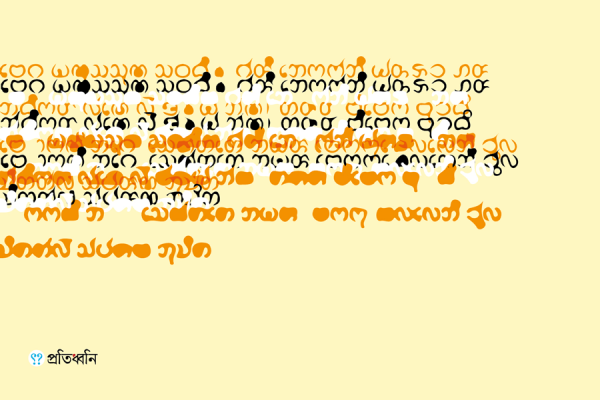
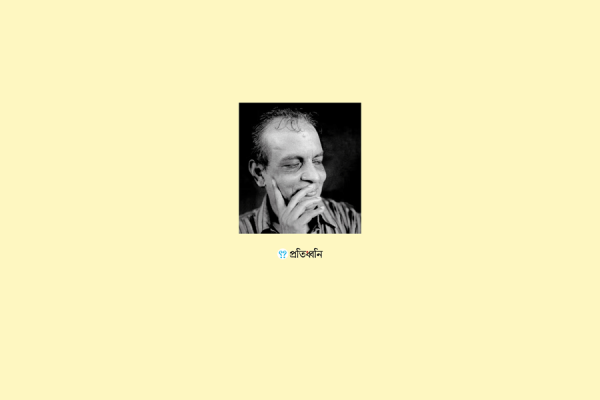
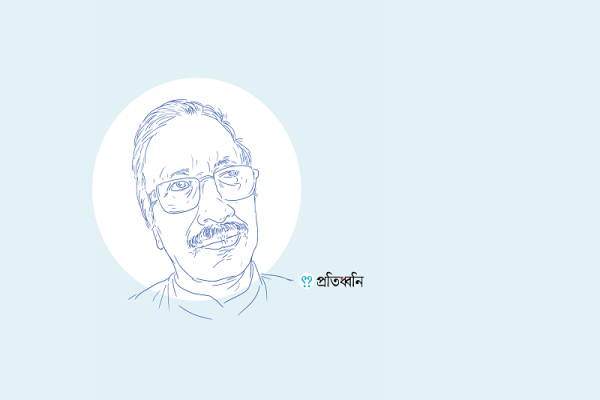
আপনার মন্তব্য প্রদান করুন