আইরিশ কবি ও নাট্যকার শেমাস হীনির নোবেল বক্তৃতা
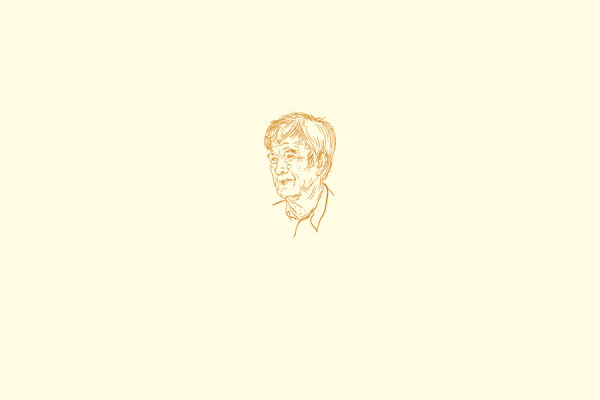
|| শেমাস হীনি ||
শেমাস হীনি ১৯৩৯ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার বংশের দিক থেকে তিনি ছিলেন গেল্টিকের পশুপালন ঐতিহ্যের বাহক এবং মায়ের বংশের দিক থেকে আলস্টারের শিল্প বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত। তিনি মনে করতেন—বাবার নিয়ত নীরব থাকার প্রবণতা আর মায়ের সমকালীন সরব থাকার অভ্যাসের জটিল সংমিশ্রণ তার লেখার প্রেক্ষাপটকে প্রভাবিত করেছে। ভাষা ও ভাবের এই পরিশোধিত সংশ্লেষণ তাকে নিজের সাথে নিজেকে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে ফেলে দিয়েছে যার মূল থেকে তার কবিতা সৃষ্ট হয়েছে। হীনি সাধারণ এক গ্রামে বেড়ে উঠেছেন। ছোটবেলায় ১৯৪৪ সালে নরম্যান্ডি আক্রমণের প্রাক-মুহূর্তে তার গ্রামের পথে আমেরিকান যোদ্ধাদের মার্চ করে হেঁটে যেতে দেখেছেন। সৈন্যরা হীনির বাড়ি থেকে এক মাইল দূরের বিমানঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই ছবিটা হীনির অচেতন মনে ‘ইতিহাস ও অজ্ঞতা’ হিসাবে স্থায়ী ছাপ ফেলে। যা তার কাব্য জীবনের প্রকৃতি ও বিকাশের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। ১৯৫৩ সালে তার পুরো পরিবার জন্মস্থানের এই খামার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে তিনি বার বার বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন। এই প্রস্থান শুধু ভৌগলিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকও বটে। জন্মভূমির স্মৃতি কখনো তিনি ভুলে যেতে পারেননি। তার অধিকাংশ কবিতার পটভূমি তাই তার জন্মভূমি।
সেন্ট. কলম্বো কলেজে শেমাস হীনি লাতিন ও আইরিশ শেখাতেন। এই ভাষার সাথে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার মিথস্ক্রিয়া কবি হিসাবে তার অগ্রগতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ১৯৬০-এর দশকে তিনি তার প্রথম দিককার কবিতা লিখেছেন, যার অধিকাংশই কবিতাই ‘নর্থ’ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজিতে লিখিত হলেও মূলত তারা অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার স্মারকলিপি। এই সময়ে লেখা তার কবিতাগুলো অনেক বেশি অভিঘাতমূলক। পরবর্তীকালে ৮০ ও ৯০ দশকে রচিত কবিতায় ইংরেজি ভাষায় ভূমধ্যসাগরীয় সাহিত্য ও ভাষার চিরায়ত উপাদান ও অনুষঙ্গ অনেক বেশি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন—‘স্টেশন আইল্যান্ড’ (১৯৮৪) কাব্যে দান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত ‘সীয়িং থিংস’ কাব্যগ্রন্থে ভার্জিলের ‘দি এ্যানিয়েড’ মহাকাব্যের পঞ্চম পুস্তক থেকে অনূদিত পদ্য কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।
১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে হীনি যখন আইরিশ সাহিত্যের ‘নর্দান স্কুল’ কবি সম্প্রদায়ের একজন পরিচিত সদস্য, তখন তার কবিতা সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যদিও শেমাস হীনি, মাইকেল লঙলি, ডেরেক মাহন, পল মুলডুন, ম্যাধ ম্যাকগুকিয়া এবং কিরণ কারসন সকলেই উত্তর আয়ারল্যান্ডের তরুন প্রজন্মের কবি ছিলেন। সকলেই সে সময়ের রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমারেখা দিয়ে চরমভাবে বিভক্ত সমাজে বেড়ে উঠেছেন। তবুও হীনির কাব্যের মেজাজ ও রচনা শৈলী তার সমসাময়িক কবিদের থেকে ভিন্ন ছিল। এই বিভক্তির কারণে পরবর্তী সিকি শতাব্দী ধরে জাতিগত হিংস্রতা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও আন্তঃসম্পর্কে অন্দরে অবিশ্বাসের ভয়ানক দাবানলের মতো ছড়িয়েছে। এই ঘটনাগুলো ১৯৭০ দশক জুড়ে হীনির কবিতায় একটা ক্লেষময় মেজাজ দিয়েছে। জগতে কবিতার দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রশ্ন হীনিকে একটা গভীর তন্ময়তার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। কবিতা একজন কবিকে যেমন তার নিজের মধ্যে সৃজনশীল স্বাধীনতা আস্বাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি নাগরিক হিসাবে কবিকে সমাজের প্রতি বাধ্য থাকার চাপ সৃষ্টি করে। এই প্রেরণা থেকে তিনি নাট্যকার ব্রায়ান ফ্রিয়েল ও অভিনেতা স্টিফেন রিয়েলের প্রতিষ্ঠিত ফিল্ড ডে থিয়েটার কোম্পানির সাথে যুক্ত হন। এই থিয়েটারে তিনি কবি শীমাস দীনে ও টম পওলিন এবং গায়ক ডেভিড হ্যাভন্ডের সাথে পরিচিত হয়ে চলমান আইরিশ রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাহিত্য ও সঙ্গীত দলের সদস্যদের শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলি ক্যাম্পাসে লেকচারার হিসাবে—১৯৭০ ও ৭১-এর দিনগুলোতে তিনি অনেক স্বাধীনতা যাপন করেছেন। আমেরিকার মুক্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হীনির মধ্যে আত্ম-দ্বন্দ্ব ও জীবনে সম্ভাবনার একটা নতুন বোধ জাগ্রত করে দিয়েছিল। যার ফলে তিনি আয়ারল্যান্ডে ফিরে এসে কুইন’স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের পদ (১৯৬৬-৭২) থেকে অব্যাহতি নিয়ে একজন স্বাধীন কবি ও লেখক হিসাবে জীবনযাপন করতে উইকল প্রদেশের একটি কুটিরকে বেছে নেন। কয়েক বছর পর হীনির পরিবার ডাবলিন শহরে স্থানান্তর হয়। ডাবলিনে তিনি ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ক্যারিসফর্ট কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের জন্য কবিতার অধ্যাপক হিসাবে নির্বাচিত হন।
শেমাস হীনি কর্মজীবন জুড়ে আয়ারল্যান্ড ও বিদেশে শিক্ষা ও শিল্পের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় তিনি উঠতি কবিদের কবিতার পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। নিয়মিত একটা শক্তিশালী কবিতার কর্মশালার আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের আর্টস কাউন্সিলে পাঁচ বছর দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। ডব্লিউ. বি. ইয়েটস আন্তর্জাতিক সামার স্কুলসহ অসংখ্য কবিতা প্রতিযোগিতার বিচারক ও সাহিত্য সম্মেলনের বক্তা হিসাবে কাজ করেছেন।
হীনি কবিতার প্রতীতিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য কাব্যমাধ্যম ছাড়াও নিয়মিত কবিতার সমালোচনা লিখতেন। তার বেশিরভাগ সুপ্রসিদ্ধ কাব্য সমালোচনা অক্সফোর্ডে কবিতার অধ্যাপক হিসাবে দেয়া বক্তৃতা সংগ্রহ ‘দ্য রেডরেস অব পোয়েট্রি’ (১৯৯৫) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। তার অন্যান্য প্রবন্ধ ‘ফাইন্ডারস কিপারস: সিলেক্টেড প্রস, ১৯৭১-২০০১’ (২০০২) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার জন্য প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মাননা ট্রুম্যান ক্যাপুটে পুরস্কার অর্জন করে। হীনি অনুবাদক হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মধ্যযুগের অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাকে আধুনিক ইংরেজিতে রূপান্তর করতে অভূতপূর্ব গীতিময়তা ব্যবহার করেছেন। ‘বেউলফ’ (২০০২) তার বিখ্যাত অনুবাদকর্ম। আইরিশ ও স্কটিশ চিরায়ত সাহিত্য ছাড়াও তিনি গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের ইংরেজি সংস্করণের জন্য সুপরিচিত।
হীনি ২০০৬ সালে ‘ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সার্কেল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ কবিতার সম্মাননা টি. এস. ইলিয়ট পুরস্কার লাভ করেন। কবিতায় গীতিময় সৌন্দর্য ও নৈতিক গভীরতার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের বিস্ময়কর ঘটনা এবং প্রাণবন্ত অতীতকে মুক্ত চিত্তে প্রকাশ করার কৃতিত্ব স্বরূপ ১৯৯৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।
|| সম্পাদকীয় নোট ||
আইরিশ কবি ও নাট্যকার শেমাস হীনির শিল্প, সত্য ও রাজনীতি শিরোনামের বক্তৃতাটি দেন ২০০৫ সালের নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশানের অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান প্রতিধ্বনি পত্রিকাকে বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশের কপিরাইট প্রদান করেছে। আমরা নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশান ও শেমাস হীনির কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। প্রতিধ্বনির জন্য এটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও সমালোচক পলাশ মাহমুদ।
নোবেল বক্তৃতা || শেমাস হীনি || কবিতার কৃতিত্বে...
আমি যখন প্রথম স্টকহোম শহরের নাম শুনি তখন ক্ষণিকের জন্য ভেবেছিলাম একদিন যাবো এই শহর ঘুরতে। কল্পনাও করিনি শেষ পর্যন্ত সুইডিশ একাডেমি ও নোবেল ফাউন্ডেশনের নিমন্ত্রণে আসা হবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে এই সফর শুধু প্রত্যাশার বাইরে নয় এটা একেবারে ধারণার অতীত। ১৯৪০ দশকে আমি যখন কো. ডেরি গ্রামে একটা ক্রমবর্ধমান পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠেছিলাম। আমরা তখন সবাই খড় দিয়ে বানানো ঐতিহ্যবাহী খামার বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকতাম। বলা যায় অনেকটা গুহাবাসীর মতো বাহির বিশ্ব থেকে দূরে কোথাও। সবাই সবার প্রতি কম-বেশি আবেগ দিয়ে যুক্ত থাকতাম, আর বৌদ্ধিক চর্চা ছিল চলমান। সবকিছু সবকিছুর সাথে খুব কাছাকাছি ছিল, আর অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত থাকতো। রাতের বেলা শোবার ঘরের বাইরে আস্তাবলে ঘোড়ার ডাকের সাথে রান্নাঘরে দুজন মানুষের আলাপের ফিসফিস শব্দ একসুরে মিশে যেতো। আমাদের চারপাশে যাই ঘটতো সবকিছুতে আমাদের সংবেদন কোন না কোনভাবে যুক্ত হয়ে পড়তো। গাছের পাতার ফাঁকে বৃষ্টির জল পড়া, খড়ের ছাদে ইঁদুরের দৌড়, ঘর থেকে মাঠ পেরিয়ে রেলের সমান্তরাল লাইনে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করতে করতে স্ট্রিম ট্রেনের চলে যাওয়া। সবকিছুর সাথে এমন জড়িয়ে ছিলাম যেন আলাদা কিছু ঘটেনি। যেন আমরা শীতনিদ্রায় ডুবে আছি। অনৈতিহাসিক, প্রাক-যৌনতার কাল যাপন করছি। অর্বাচীন ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী সিঁড়িতে দাড়িয়ে আছি। আমরা খুবই ভাবুক ও অনুভূতিপ্রবণ ছিলাম। অনেকটা কলতলার বালতির তলানিতে জমা জলের মতো। যতোবার একটা ট্রেন বিকট আওয়াজ করে চলে যেতো সাথে সাথে জমা জলের উপর পরতে চক্রাকারে মৃদু তরঙ্গ নিঃশব্দে ছড়িয়ে পরতো।
শুধুমাত্র মাটির কাঁপনই আমাদের উদ্বেলিত করতো না। আমাদের ঘিরে থাকা বাতাস ও মাথার উপর আকাশ স্পন্দিত হতো আর আমাদের নানারকম ইশারা করতো। যখন বীচবৃক্ষের ডাল-পাতা নাড়িয়ে মৃদু বাতাস বয়ে যেতো। সাথে সাথে চেস্টনাট গাছের সবচেয়ে উপরের ডালে বাধা আকাশতারও দুলে উঠতো। তারটি গাছ থেকে নেমে এসে রান্না ঘরের জানালার কোনার ছোট ছিদ্র দিয়ে ঢুকে রেডিওর সাথে যুক্ত হতো। রেডিওর সামনের দিকের জালিকা বুদবুদ ধ্বনির গুঞ্জনে মুখরিত থাকতো। একটানা চিঁ চিঁ শব্দ থেমে হঠাৎ করে বিবিসি সংবাদ পাঠকের কণ্ঠস্বর বের হয়ে আসতো। মনে হতো মানুষ নয় কোন যন্ত্র-ঈশ্বর কথা বলচ্ছে। রান্না ঘরে বড়দের কথার ভীড়কে অতিক্রম করে সেই রেডিও কণ্ঠ আমাদের শোবার ঘরে পৌঁছে যেতো। যেমন করে আমরা একজনের কথার পিছনে থেকে বলা আরেকজনের কথা শুনি, তীব্র ও তীক্ষ্ণ মোর্স কোডের সংকেতের মতো। আমাদের বাবা-মায়ের মুখে আঞ্চলিক উচ্চারণ শুনতে শুনতে রেডিওতে বলা আমাদের প্রতিবেশীদের নামগুলো একে একে ধরতে পারতাম। পরিশীলিত ইংরেজি উচ্চারণে বলা বোমা নিক্ষেপকারী ও বোমা বিস্ফোরণে আক্রান্ত শহরগুলোর নামও ধরতে পারতাম। যুদ্ধ ফ্রন্ট, সেনা শিবির, কতগুলো বিমান হারিয়ে গেছে, কত যুদ্ধবন্দী আটক আছে, কতজন মৃত্যু ও দুর্দশা ভোগ করেছে এবং কত সৈন্য রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সব বিষণ্নতা ভরা ও অদ্ভুতুড়ে ‘শত্রুপক্ষ’ ও ‘মিত্রপক্ষ’ শব্দ বন্ধ ধরতে পারতাম। সবকিছুর পরও, বিক্ষুব্ধ-বিশ্বের কোন সংবাদই আমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ সংবাদ পাঠকের গলার স্বরে অমঙ্গলের আভাস থাকলেও, আমাদের কাছাকাছি কোথাও বিপদ ঘটবে কিনা তা ধরতে না পেরে হতবুদ্ধ হয়ে থাকতাম। সেই দেশ ও কালের রাজনৈতিক অজ্ঞতা যদি নিন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে সেটা নিয়ে আমার উৎসুকতা আমার জন্য মঙ্গলই বয়ে এনেছে।
অন্য কথায়, সংগ্রামের কাল ছিল আমার জন্য প্রাক-প্রতিফলনের সময়। আমার সাহিত্যের পূর্ব-প্রস্তুতির আমল বলতে পারি। বিস্তৃতভাবে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ বলা যায়। সময় যেতে থাকে আর আমি আরো ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্যানের মতো করে চারপাশের সব শুনতে থাকি। আমি সোফার হাতলে চড়ে বসতাম আর কানটাকে রেডিওর মুখ ঘেঁষে রাখতাম আরো স্পষ্ট করে শুনবো বলে। কিন্তু আমি প্রাত্যহিক সংবাদ শোনার জন্য মোটেও আগ্রহী ছিলাম না। আমি গল্পের রোমাঞ্চের জন্য অধীর হয়ে থাকতাম যেমন: ডিক বার্টনের মতো ব্রিটিশ স্পেশাল এজেন্টের গোয়েন্দা সিরিজ কিংবা বিট্রিশ রাজ বিমান বাহিনীর উড়ন্ত টেক্কার দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন ডব্লিউ. ই. জনসের অভিযান কাহিনির রেডিও সংস্করণ শুনতে অস্থির হয়ে থাকতাম। বাড়ির বড় বাচ্চারা রান্না ঘরে ঘন ঘন যেতো। আর আমি রেডিওর খুব কাছে গিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। রেডিও ডায়ালের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি বিদেশি স্টেশনগুলোও ঘুরিয়ে দেখতাম: লিপজিগ, অসলো, স্টুগার্ড কখনো ওয়ারস এবং অবশ্যই স্টকহোমের মতো নামের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। এই করতে করতে আমি বিদেশি ভাষার নানা শব্দ শুনতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিবিসি থেকে এইরান চলে যেতাম। লন্ডনের স্বরভঙ্গি থেকে ডাবলিনের স্বরভঙ্গিতে মিশে যেতাম। যদিও আমি ইউরোপিয়ান সেই সব ভাষার কণ্ঠবর্ণ কিংবা শিসধ্বনি জীবনে প্রথম শুনেছিলাম।
আমি ততদিনে আমার চেনা দুনিয়ার বাইরের বিশালতার সমুদ্রে ভ্রমণ শুরু করেছি। যা পরে ভাষার বিস্তৃর্ণ ভূমিতে পরিভ্রমণে স্থির হয়েছে। এমন পরিভ্রমণ যেখানে প্রতিটা পদক্ষেপই নতুন আগমন। যেখানে কারো একটা কবিতা বা কারো এক জীবন গন্তব্য না হয়ে এক একটা সোপান পাথর হয়ে উঠে। এই পরিভ্রমণই আমাকে আজকের এই বিশাল মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই মঞ্চকে আমার সোপান পাথর নয় এক বিশাল মহাকাশ স্টেশন মনে হচ্ছে। তাই জীবনে এই প্রথমবার নিজেকে মহাশূন্যে হাঁটার বিলাসিতা সুযোগ দিলাম।
*
এই মহাকাশ পদচারণা সফল করার জন্য আমি পুরোটা কৃতিত্ব কবিতাকে দেবো। প্রথমত কবিতাকে কৃতিত্ব দেবো কারণ সম্প্রতি আমি আমাকে উদ্দেশ্য করে (এবং কবিতাটা যারা শুনবে তাদের উদ্দেশ্য করে) একটা কবিতার লাইন লিখেছি: ‘যদি মন সায় নাও দেয় তবুও দখিন হাওয়ায় ঘুরে এসো।’ শেষ পর্যন্ত আমি কবিতাকে কৃতিত্ব দেবো, কারণ জগতে কবিতা শৃঙ্খলা আনতে পারে, আমাদের জানার বাইরের বাস্তবতার সত্যরূপ উন্মোচন করতে পারে এবং কবি সত্তার অন্তরীণ ধর্মের প্রতি সংবেদী হয়ে উঠতে পারে। ঠিক প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে কলতলার বালতিতে জমা জল যেভাবে চক্রাকারে তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে গিয়েছিল। এক বিন্যাসিত জগৎ যেখানে আমরা অন্ততপক্ষে এমন এক স্তরে বেড়ে উঠতে পারি। এমন অনুশাসিত জগৎ যা আমাদের বুদ্ধির ক্ষুধাকে নিবারণ করে। আমাদের আবেগের আক্রোশকে শান্ত করে। কবিতা কবিতা হয়ে ওঠার জন্য আমি কবিতাকে কৃতিত্ব দেবো। আমাদের মনের কেন্দ্র ও তার পরিধির মধ্যে এমন বলবর্ধক বন্ধন তৈরি করার জন্য আমি কবিতাকে কৃতিত্ব দেবো। রেডিওর ডায়ালে ভেসে উঠা ‘স্টকহোম’ শব্দের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকা বালকটির সাথে এই স্বর্নালি মুহূর্তে স্টকহোমের মঞ্চে উপবিষ্ট দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকা এই পূর্ণবয়স্ক লোকটির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য আমি কবিতাকে কৃতিত্ব দেবো। আমি কৃতিত্ব দেবো কারণ কবিতা কৃতিত্ব পাওয়ার যোগ্য। শুধু এই মুহূর্তে নয় সবসময়ের জন্য পাওনা। কৃতিত্ব পাওনা কারণ কবিতা জীবনের প্রতি সৎ ও স্বচ্ছ থাকে, তা সে যে কোন অর্থে থাকুক না কেন।
*
আমার কবি জীবনের শুরুর দিকে কবিতার জীবনের প্রতি সৎ এই নির্যাসটি দিয়ে আমি বস্তুগত বিশ্বাসযোগ্যতাকে অধিকার করতে চেয়েছি। কবিতার দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ ক্ষমতা দেখে উল্লসিত হয়েছি। জগতকে সামনে থেকে চিত্রিত করে তার পায়ের তালে তাল মিলিয়ে দাড়িয়ে থাকার জন্য বা তার বিপরীত স্রোতে বুক পেতে ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকার জন্য কবিতাকে অন্তরীণ করতে চেয়েছি। এমনকি বালক বয়সে জন কিটসের ‘টু অটাম’ স্ত্রোত্র কবিতাটি যেভাবে ভাষা ও মানব সংবেদনের মাঝে সেতু নির্মাণ করেছে তার জন্য কবিতাটি খুবই পছন্দ করেছিলাম। কিশোর বেলায় আমি জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতায় বিস্ময়োক্তির তীব্রতাকে এড়াতে পারিনি। বিস্ময়বোধকগুলো এক একটা পরমানন্দ ও বিষাদের সমীকরণ মনে হতো। হপকিন্স পড়ার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম না যে এই সমীকরণ আমি জানি। আমি রর্বাট ফ্রস্টকে তার কাব্যের নৈপুণ্যশীলতা ও ভাষার কৌশলী বিনয় বোধের জন্য কৃতিত্ব দেবো। চসারকে ও একই কারণে প্রশংসা না করে পারছি না। পরের দিকে আমি এক ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় কবিতার নিপুণতার দেখা পেয়েছি। এবার নৈতিকতা সিক্ত বিনয় যার প্রতি আমি তীব্রভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আজীবন থাকবো বলে মনে হচ্ছে। উইলফ্রেড ওয়েনের যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা যেখানে নিউ টেস্টামেন্টের চেতনা দুর্দশায় জর্জরিত আর নতুন শতাব্দীর বর্বরতার অভিঘাতকে শুষে নিচ্ছে। আরো পরে এসে এলিজাবেথ বিশপের বিশুদ্ধ পরিণতি, রর্বাট লওয়েলের অকাট্য দৃঢ়তা, প্যাট্রিক ক্যাভ্নহর মুখোমুখি সংঘর্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি কবিতার ক্ষমতা ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাস এনেছিলাম। কবিতার মধ্য দিয়ে আমি বলতে পারি জগতে কি ঘটে চলেছে, ‘গ্রহানুগ্রের প্রতি করুণা সিক্ত হই’ আর ‘কবিতা নিয়ে সংশয়ে থাকি না।’
শিল্পের প্রতি আমার এমন মেজাজী স্বভাব খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। উত্তর আয়ারল্যান্ডে জন্ম নিয়ে এর আলো-বাতাসে বেড়ে উঠার কারণে এ মাটির সবকিছুর প্রতি একটা গভীর অনুরাগ কাজ করে। যদিও আমি গত পঁচিশ বছর ধরে এই আয়ারল্যান্ডের বাইরে আছি, তবুও এখনো এই অনুভূতি কাজ করে।
পৃথিবীর আর কোন দেশ তার বাস্তবতা ও সর্তক অবস্থান নিয়ে এতো আত্ম-অহমিকা করে না। পৃথিবীর আর কোন দেশ তার প্রত্যাশার আধিক্য বা বাগ্মিতা বিকাশের নিন্দা জ্ঞাপনে নিজেকে এত যোগ্য মনে করে না। তাই কিছু ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আত্তীকরণ করতে করতে বেড়ে উঠতে হয়, কিছু ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। ওয়ালেস স্টিভেনস ও রাইনার মারিয়া রিলকের মতো বৈচিত্র্যময় কবিদের কবিতার ঐশ্বর্য ও ব্যাপকতা থেকে নিজেকে অনেক বছর ধরে কখনো দূরে দূরে থেকেছি আবার কখনো আত্ম-সংবরণ করেছি। এমিলি ডিকিনসন্সের স্ফটিক-স্বচ্ছ অন্তর্মুখিতাকে তার প্রাপ্য কৃতিত্ব দেইনি। ওইসব হঠাৎ আলোর বিচ্ছুরণ আর সকল ভাবানুসঙ্গের অন্ধিসন্ধিগুলোকে যথাযথভাবে স্বীকার করিনি। ইলিয়টের অপার্থিব, অপরূপ ভাব বিলাসকে মনের আড়ালে রেখেছি। যে কোন নাগরিকের থেকে একজন কবিকে অধিক কৃতিত্ব না দেয়ার এই কার্পণ্য অধিক শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংকটে গণমানুষের প্রত্যাশা চরিতার্থ করার জন্য কবিকে কবি হয়ে উঠার জন্য প্ররোচিত করেছে। কবির কাছে এই গণপ্রত্যাশা কবিতার জন্য নয় বরং পারস্পরিক অসম্মতিতে বিভক্ত দলের মধ্যে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করার জন্য। এহেন পরিস্থিতিতে স্যামুয়েল জনসন যে উচ্চ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ‘সত্যের স্থিতিশীলতার’ কথা বলেছেন তাতে নিজের মনকে স্থির করতে তাগিদ বোধ করি। যদিও সত্য নিজেই তার অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণে অস্থিতিশীল প্রকৃতির। কোন তাত্ত্বিক সহায়তা ছাড়াই আমাদের চেতনা প্রবাহ বুঝতে পারে যে সত্য অনুসন্ধান নিজেই একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আলাপ। শোবার ঘরে বসে যে শিশু আইরিশ পারিবারিক প্রবচনের ও একই সাথে রেডিওতে ব্রিটিশ দাপ্তরিক প্রবচন শুনে অভ্যস্ত হচ্ছিল। পাশাপাশি স্বদেশের সীমারেখা ছাড়িয়ে পরদেশী ভাষার আস্বাদন নিচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার ফলে সেই শিশুটি প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে তার পূর্ণ বয়স্কবেলার জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম ধারণা পেয়ে যাচ্ছিল। এমন এক আগামীর নৈতিক, নান্দনিক, রাজনৈতিক, ছান্দিক, সংশয়ী, সাংস্কৃতিক, স্থানিক, প্রতিকী, উত্তর-উপনিবেশিক, এবং অন্যান্য সকল জটিলতা একসাথে মূল্যায়ন করার বাসনা ও ক্ষমতা অর্জন করতে চাচ্ছিল যা এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি আরেকটি ছোট বাড়িতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। এইবার ডাবলিনের দক্ষিণে কো. উইকলোর এক আত্মীয়ের বাড়ি। এখানে আগের বাড়ি আরো একটু কম আকর্ষণীয় রেডিও শুনছিলাম। সাথে জানালার পাশে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে পড়া বৃষ্টির শব্দ। খবরে সংবাদ পাঠকের শব্দের সাথে কাছাকাছি কোথাও বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ভেসে আসছিল। শুধুমাত্র বেলফেস্টের আইআরএ নয়। উত্তর আয়ারল্যান্ডের অনুগত আধা সামরিক বাহিনী ডাবলিনে একই মাত্রায় নৃশংস হামলা চালাচ্ছিল। ১৯৩০ দশকে ওসিপ ম্যান্ডেলস্টামের বিষাদময় করুণ পরিণতির কাহিনী পড়ে আমার নিজের দুরাবস্থার কথা ভেবে খুব অসহায় বোধ করছিলাম। আমার স্কুলের এক নিরীহ বন্ধুকে রাজনৈতিক হত্যার সন্দেহে কোন বিচার ছাড়াই বন্দি শিবিরে আটক করা হয়েছিল। এই ঘটনা শুনে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ থেকে দূরে ছিলাম কিন্তু তীব্র দ্রোহের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি মন থেকে যা চাচ্ছিলাম তা জীবনে স্থিতিশীলতা নয় বরং বাস্তবতার অদ্ভুত ও নির্মম আপেক্ষিকতার চোরাবালি থেকে পালাতে চাচ্ছিলাম। কোন রকম কৈফিয়ত বা পাপ মোচন নয় বরং জীবনে মুক্তির স্বাদ আনতে কবিতায় ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার কবিতা ‘এক্সপোজার’-এর মাধ্যমে কবিতার কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম।
যদিও আমি আসতে পারতাম উল্কাপিন্ডের ঘাড়ে চরে!
তবুও, আমি হেঁটে আসলাম ক্লেদাক্ত পাতায় পাতায়,
তুষের দানায় দানায়, হেমন্তের ফুরানো ফসলের পথে।
এক বীর পুরুষের ছবি মানসপটে ভাসছিল
কোন এক পঙ্কিল ভূমিতলে,
হাত ভরা গুলতি পাথর
বেপরোয়া হয়ে ছুটতে উন্মুখ।
শেষ পর্যন্ত আমার এই হাল হলো বেহাল?
মনে পড়ে বারবার কাছের বন্ধুটির
অনিন্দ্য, জ্যোর্তিময় সদালাপ
আর আমার নিন্দুকের কর্ণাস্থির শব্দাবেশ।
আমি নিরালায় বসে শুধু ভাবছি আর ভাবছি
কেন আমার এই জীবন ভরা বিষাদ।
কিসের জন্য? কোন সে দেশ? কোন সে মানুষ?
পিঠ পিছনে কোন ষড়যন্ত্র?
ভূর্জ বৃক্ষের ডাল বেয়ে নামচ্ছে বৃষ্টির ধারা,
মিহি স্বরে গেয়ে যাচ্ছে
আমার পতন, আমার ক্ষয়ের কথা
জলের প্রতি ফোঁটায়।
হীরক সে তো পরম পাথর।
আমি তো নই যুদ্ধবন্দী, নই তো কোন গুপ্তচর
আমি নিজের ভেতর নিজেই দেশান্তরী; এক জটাধারী
আত্মমগ্ন বনাচারী।
বধ্যভূমি থেকে পলাতক পাখি।
সঙ্গোপনে রঙ মাখছি
পত্র বাকল রসে, বিবশ হচ্ছি
হাওয়ার কলতানে।
কে সে? দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে
ম্রিয়মাণ তাপে, আমি হারাচ্ছি
জীবনে একবার আসা সেই সুবর্ণ সুযোগ,
ধূমকেতুর স্পন্দন আমি এখনো টের পাই।
[‘নর্থ’ থেকে]
আমার প্রজন্মের ছাত্রদের কাছে একটা কবিতা খুব বিখ্যাত ছিল। প্রতীকী আন্দোলনের সবটুকু নির্যাস আত্মস্থ করে একটা ক্যাপসুলের মতো প্রকাশ করা যেতে এমন একটা কবিতা। মার্কিন কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ যেমন লিখেছেন, ‘কবিতাকে সমান হয়ে উঠতে হবে/সত্য, ন্যায়ের সমান।’ কবিতা সত্য বলবে কিন্তু তির্যক সত্য—এই দ্বান্দ্বিকতা পূর্ণ বাক্যটি একই সাথে অকাট্য এবং খণ্ডনযোগ্য। মাঝে মাঝে কবিতায় যখন কোন গভীর তাড়না ঢুকে যায়, তখন আমরা কবিতাকে সঠিক হয়ে উঠার প্রত্যাশার মধ্যে আবদ্ধ রাখি না। বরং অপরিহার্যভাবে বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠার চাপ সৃষ্টি করি। বিশ্ব সংসারে চমৎকার কোন প্রভাব বিস্তারে আটকে রাখি না। বরং বিশ্বকে নতুন কোন সুরে সাজাবে এই প্রত্যাশায় উদগ্রীব থাকি। কবিতা সেই ছেলেটির চঞ্চল বৃদ্ধাঙ্গুলির মতো সকর্মক হয়ে উঠুক, যে কিনা অনবরত অস্থিরতায় নাড়াচাড়া করতে করতে টেলিভিশন পর্দার ছবিতে স্পষ্টতা ফিরে আনতে পারে। অথবা ঐ ইলেকট্রিক শকের মতো যে কিনা অস্থির হৃদয়কে তার স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরিয়ে দেয়। লেনিনগ্রাদের কারাগারের লাইনে দাঁড়িয়ে ওই নারীটি যা চেয়েছিল আমরাও তাই চাই। স্ট্যালিন আমলের নৃশংসতা ও নির্মমতা সহ্য করে, তীব্র শীতে নীল হয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে কবি আন্না আখমাতোভাকে জিজ্ঞেস করেচ্ছিল, ‘ও কি এই সব কিছু তার লেখায় তুলে আনতে পারবে? তার কাব্যশিল্প কি এই নির্মমতার সমান হতে পারে?’ আমি যখন আপন ঘর থেকে দূরে সুরক্ষিত কো. উইকলোর বনে বসে আমার উদ্ধৃত কবিতাটা লিখছিলাম। আমিও ঠিক একই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমি কি আমার কবিতায় এই চলমান বিক্ষুব্ধ সময় কে হুবহু শব্দ দিয়ে ধরতে পারবো? কয়েক মুহূর্ত আগে কবিতার যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি তার মর্যাদা কি রাখতে পারবো? ‘বাইরের জগতের বাস্তবতার প্রতি সৎ থাকতে পারবো... কবির ভেতরের জগতের প্রতি সংবেদনশীল থাকতে পারবো।’
*
১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাহ্যিক বাস্তবতা ও আভ্যন্তরীণ প্রগতির জন্য যে ঘটনা ঘটছিল তা ছিল মূলত আদর্শিক পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন খুব নাশকতার মধ্য দিয়ে ঘটে যাচ্ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জীবন ও পরিস্থিতির পরিবর্তন আগের মতোই ছিল। ষাটের দশকে পথে প্রান্তরে সংগঠিত দুর্বার প্রতিবাদের ফলে অনেক আগেই সংস্কারটা হতে পারতো। কিন্তু সেটা না হয়ে মুরগির তায়ে বাচ্চা ফুটানোর মতো বিপদের ডালপালা দ্রুত গজাতে লাগলো। আইরিশ রিপাবলিক আর্মির বোমাবাজি ও নির্বিচার হত্যার পৈচাশিক প্রকৃতিকে যখন ব্যক্তির ভেতরে নিহিত খ্রিষ্ট নৈতিকতা দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছিলো। তখন ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার চিহ্ন ডেরির রক্তাক্ত রবিবারে ঘটনার ফলে আইরিশ চেতনা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সংখ্যালঘু নাগরিক সম্প্রদায় সরকারি ও বেসরকারী সকল নীতির প্রতি একরকম বৈষম্য ও অবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠেছে। ওই আইরিশ নাগরিক এই বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিকে কাব্যিক সত্যের চোখ দিয়ে দেখেছিল। সে মনে করেছে উত্তর আয়ারল্যান্ড যদি সত্যি বিকশিত হতে চায় তাহলে চলতি পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু ওই নাগরিক বিপরীত সত্যটা ও দেখেছে। আইরিশ রিপাবলিক আর্মি এই পরিবর্তন আনার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছে তা খুবই বিপজ্জনক পথ। আর এই ঝুকিপূর্ণ উপায়ে নির্ভর করে কি নতুন সম্ভাব্য পরিবর্তন আসবে? ১৯৭৪ সালে সানিংডেইল সম্মেলনের পর অলস্টারের একনিষ্ঠ কর্মীদের শক্তিশালী রণকৌশলের কাছে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে নেয়ার আগ পর্যন্ত যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকই এই পরিস্থিতিকে যথার্থ ভাবে বুঝতে পারতো। প্রত্যাশার আলোর সাথে হতাশার অন্ধকারের ভারসাম্যকে ধরতে পারতো। ডব্লিউ. বি. ইয়েটস অর্ধ শতাব্দী আগে যা করতে চেয়েছিল তাই করতো যেমন, ‘চিন্তার মাঝে একই সাথে বাস্তবতা ও ন্যায়বিচারকে ধরতে পারা।’ ১৯৭৪ সালের পর থেকে ১৯৯৪ সালের যুদ্ধবিরতির আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিশ বছরে এমন আশাব্যাঞ্জক কিছু ঘটনাটা প্রায় অসম্ভব ছিল। আয়ারল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের সহিংসতা তেমন উপকারী তো ছিলই না বরং দক্ষিণাঞ্চলের রক্তপাতের প্রতিহিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিশোধ ছিল। বাস্তবতার নিষ্ঠুরতা ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এক শতাব্দীর সিকিভাগ সময় জুড়ে মানুষ তাদের জীবন অপচয় করেছে, তাদের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করেছে। রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতি একটা অনড় মনোভাব ধারণ করেছে। জীবনের সম্ভাবনাকে সংকীর্ণ করে রেখেছে। রাজনৈতিক সংহতি, দুঃসহ মনোবেদনা এবং তীব্র আবেগের আত্মরক্ষার ফলশ্রুতিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
*
উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমগ্র ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক মুহূর্তটি ছিল ১৯৭৬ সালের এক জানুয়ারির সন্ধ্যা। যখন একটা মিনিবাস ভর্তি যাত্রী কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন একদল মুখোশধারী সশস্ত্র লোক পথ আটকে বন্দুকের মুখে সব যাত্রীকে রাস্তায় সারিবদ্ধ দাড় করিয়েছিল। একজন মুখোশধারী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, ‘তোমাদের মধ্যে যারা ক্যাথলিক তারা এক পাশে সরে দাঁড়াও।’ পরে দেখা গেলো এই যাত্রীদলের একজন ছাড়া সবাই প্রটেস্টান্ট। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে মুখোশধারী আক্রমণকারী ছিল একজন আধা সামরিক প্রটেস্টান্ট যে কিনা বদলার বদলে বদলা নিতে আইআরএ’র আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন ক্যাথলিককে সাম্প্রদায়িক হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। ক্যাথলিক লোকটার জন্য এই পরিস্থিতি ছিল এক ত্রাসের অভিজ্ঞতা, কিন্তু সে একধাপ এগিয়ে আসলো। ঠিক তারপরই ঘটলো আসল ঘটনা। এমন হিম শীতল সন্ধ্যার অন্ধকারে আরেকটি সিদ্ধান্তের কারণে ঘটনার অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। পাশে দাঁড়ানো প্রটেস্টান্ট লোকটি ক্যাথলিক লোকটির হাত চেপে ধরে ইশারা করলো যার মানে ছিল: না, তুমি নড়বে না, আমরা একই পথের যাত্রী। আমরা তোমার সাথে প্রতারণা করবো না। কারো জানার দরকার নাই তুমি কোন ধর্ম বিশ্বাসী বা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সব কিছুই অনর্থক। কিন্তু যেই ক্যাথলিক লোকটি যাত্রীদের সারি থেকে এক পা এগিয়ে এসেছিল সে কানের কাছে কোন বন্দুকের নল তাক করা পেলো না। উল্টো আক্রমনকারী তাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনের দিকে সরিয়ে দিলো। আর বাকি প্রটেস্টান্টদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগলো। আসলে সন্ত্রাসীরা প্রটেস্টান্ট ছিল না। ছিল আপতকালীন আইআরএ’র বাধ্যগত সদস্য।
*
ইতিহাস কসাইখানার মতো নির্দেশক—এই চিন্তাটা দমিয়ে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। ট্যাসিটাসের কথাই ঠিক, নির্মম ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রয়োগের পর যে নিরানন্দময় নির্জনতা অবশিষ্ট থাকে তাই শান্তি। আমি এখনো আমার সেই বন্ধুর কথা ভাবলে মর্মাহত হই যে কিনা সত্তরের দশকে রাজনৈতিক হত্যার সন্দেহবশত কারাগারে বন্দি ছিল। আমি এটা ভেবে মর্মাহত হই যে, যদি সে অপরাধী হতো তবুও সুন্দর একটা আগামী গড়ার কাজে সে অংশগ্রহণ করতে পারতো। দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারতো। নতুন কোন কার্যকরী সম্ভাবনার উপায় খুঁজে বের করতো। আর এই সময়ের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ হতো সহিংসতার পথ, এটাই হতো একমাত্র সঠিক পথ। এই মুহূর্তটা অনেকটা আন্তঃনাক্ষত্রিক শীতলতার মতো। ভেতর ও বাইরে বিদ্যমান সকল ভীতিকর বিষয়ে একটা সর্তকতার মতো যে পরিস্থিতিতে মানুষ নিজের অবস্থান দেখতে পারে আর জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু এটা শুধুই একটা মুহূর্ত। আমরা যে আগামীর স্বপ্ন দেখি তার গন্ডি সীমিত হয়ে আসে। যখন একদিকে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ক্যাথলিক লোকটা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, অন্যদিকে কোন বন্দুক নয়, প্রটেস্ট্যান্ট এক ভরসার হাত ক্যাথলিকের সন্ত্রস্ত হাতকে চেপে ধরে। এই মুহূর্তটা একদিকে পরম সময় অন্যদিকে পতিত সময়। এটা চলমান সঙ্গীতের একাংশ। লেখক ও পাঠক হিসাবে, পাপী ও নাগরিক হিসেবে, আমাদের বাস্তববাদ ও নন্দনতত্ত্ব যে কোন ইতিবাচক কিছুকে কৃতিত্ব দেয়ার সময় সর্তক করে দেয়। সবসময় গোলাগুলি আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে। ভয়াবহ নৃশংসতার একটা মূল্য দিতে হয় এবং এই নৃশংসতার প্রয়াস আমাদের বাধ্য করে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। তাই তো আমরা পল সেলানের কবিতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়ি। স্যামুয়েল ব্যাকিটের নিরাশার স্বর শুনে আবিষ্ট হয়ে থাকি। কারণ এইগুলো হলো শিল্পের সেইসব স্বাক্ষ্য যা আমাদের নির্মম বাস্তবতাকে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। কবিতাগুলো হলোকাস্টে দুঃস্বপ্নে টিকে যাওয়া সেলানের নিষ্ঠুর নিয়তির অনুসিদ্ধান্ত স্বরূপ। নাটকগুলো ফরাসি প্রতিরোধ ব্যবস্থার সদস্য হিসাবে বেকিটের অবিচল বীরত্বপূর্ণতার স্বাক্ষ্য। ঠিক একই ভাবে এই রকম পরিস্থিতিতে যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনা দেয় তাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞানের দুরবস্থা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নির্বোধ বা অজ্ঞান ব্যক্তি কেবল জানে না যে সভ্যতার নথিপত্র সব রক্ত আর অশ্রুজলে লেখা। দীর্ঘদিন আগের হলেও এই রক্ত ও অশ্রুজল অবাস্তব মনে হবে না। যখন আলস্টার, ইসরাইল, বসনিয়া, রুয়ান্ডা এবং পৃথিবীর অন্যসব পীড়িত দেশের এই করাল বাস্তবতার সাথে শিল্পের এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা সহাবস্থান করে তখন মানব প্রকৃতির এই গঠনমূলক সম্ভাবনাকে কৃতিত্ব না জানানো একমাত্র প্রবৃত্তি নয় বরং শিল্পকর্মের যে কোন ইতিবাচকতা ও কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। ঠিক এই কারণেই বছরের পর বছর ধরে আমি আমার লেখার টেবিলে নতজানু হয়ে ছিলাম যেভাবে একজন সন্ন্যাসী তার প্রার্থনা পিড়িতে নতজানু হয়ে থাকে। তার এই কর্তব্যনিষ্ঠ ধ্যান নিজের সম্পর্কে একটি সম্যক উপলব্ধির কেন্দ্রে নিয়ে যায় যা তাকে পৃথিবীর প্রতি তার দায় বহন করার প্রচেষ্টায় যুক্ত করে। সে যখন জানতে পারে তার মধ্যে নায়কোচিত কোন গুণ নেই কিংবা পাপমোচনে অক্ষম তবুও সে সেই একই প্রচেষ্টা ও ভঙ্গির নিয়ম বাধ্যতার সাথে পালন করে যায়। একটু উষ্ণতার জন্য সবসময় স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রাখে। প্রতিশ্রুতি ভুলে শুভ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আংশিকভাবে পরম সত্যের সাথে যুক্ত হতে চায়। এই কল্পিত পরম সত্তার সাথে আত্মসংযোগকে হিসেবে নিতে হবে। তাই অবশেষে এই যাতনাময় পরিস্থিতির কাছে নত না হয়ে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। তাই ঠিক কয়েক বছর আগে এই বিস্ময় এবং এই ভয়াবহতার বাস্তবতাকে আমার ভেতরে জায়গা দিলাম। এবং আরো একবার আয়ারল্যান্ড পটভূমি থেকে নতুন অভিমুখের গল্পকে তুলে আনলাম।
এইবারের গল্পটা আরেকজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে যে কিনা বীরোচিতভাবে সহনশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিল। এটা বলা হয়ে থাকে যে এক সময় সেন্ট কেভিন খ্রিষ্ট ক্রসের আকৃতিতে তার দুহাত দিয়ে গ্লেনডালায় হামাগুড়ি দিয়েছিল। গ্লেনডালা কো উইকলোর নিকটবর্তী একটি মঠ স্থান। এই জায়গাটা সমগ্র দেশের সবচেয়ে বেশি জলাধার ও বনবেষ্টিত নিভৃত আবাসস্থান। যাই হোক কেভিন যখন হাঁটু মুড়ে প্রার্থনারত ছিল তখন একটা কালো তিতির তার মাটিতে ছড়িয়ে রাখা হাত দুটি পাখির বাসা ভেবে তাতে বসে পড়লো। কয়েকটা ডিম পেড়ে তাতে তা দিতে লাগলো। তারপর তার নিজের মতো বাসা বানানোর জন্য খড়কুটো যোগাড় করতে লাগলো যেন হাত দুটো গাছের কোন ডাল। সহানুভূতির তাড়না এবং জগতের ছোট বড় সকল প্রাণের প্রতি মমতার বিশ্বাস থেকে কেমন অবিচল হয়ে রইলো। ঘন্টা, দিন, রাত ও সপ্তাহ চলে গেলো তবুও সে ততক্ষণ তার হাত দুটো সরালো না যতক্ষণ ডিমগুলোর তা দেয়া শেষ না হয়, যতক্ষণ ছানাগুলো থেকে পাখা না গজায়। সাধারণ কান্ডজ্ঞানের বিরুদ্ধে হলেও এই গল্পটা জীবনের সত্যটা প্রকাশ করে। যেন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার প্রতিচ্ছেদের একটা আদর্শ চিত্রের এক ঝলক নমুনা ও অভিজ্ঞান। যেন মানব বিকাশের এক কাব্যিক বিন্যাসের পরিস্ফুটন।
*
সেন্ট কেভিনের গল্পটা আয়ারল্যান্ডের হৃদয় থেকে উঠে আসা গল্প। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এই গল্পটা সমান ভাবে ভারতের, আফ্রিকার, আর্কটিকের কিংবা আমেরিকার দেশগুলো থেকেও তৈরি হতে পারে। এই বচন দিয়ে আমি গল্পটাকে কোন আঞ্চলিক লোকগাথার নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছি না। কিংবা বহুসংস্কৃতির অংশ হিসাবে গল্পটির সংস্কৃতির অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এর মূল্যকে বিতর্কিত করতে চাচ্ছি না। বিপরীতক্রমে এই গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্থানিকতা অতিক্রম করার ক্ষমতাকে এর আঞ্চলিক পটভূমি নির্ভর হতে হয়। আজকের এই সময়ে আমি সহজেই একে বির্নিমিত বিষয় হিসাবে কল্পনা করতে পারি যা অনেকটা উপনিবেশবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। কেভিনকে আমরা একজন অমায়িক সাম্রাজ্যবাদী বলতে পারি (অথবা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানপর্বের মঠ সন্ন্যাসী)। ওই সন্ন্যাস যে কিনা আদিবাসীদের সহজাত জীবনচক্রে হস্তক্ষেপ করে একে আত্মস্থ করেছিল। বাস্তুসংস্থার অকৃত্রিম প্রবাহে হস্তক্ষেপ করেছিল। আমাকে মেনে নিতে হবে যে এই পুরো গল্পটিতে একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ নিহিত আছে। যেন এই গল্পে আইরিশ ঐতিহ্যের আসল সৌন্দর্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সংরক্ষিত করা হয়েছে। কেভিনের গল্পটি গ্রীলদাস ক্যামব্রেনিসিসের লেখায় উঠে এসেছে।
গ্রীলদাস হলো একজন নরম্যান। যে দ্বাদশ শতাব্দীতে আয়ারল্যান্ড আক্রমণ করেছিল। পাচঁশত বছর পর আইরিশ ভাষা বিশ্লেষক জিওফ্রে কিটিং যাকে ‘আইরিশ ইতিহাসের মিথ্যা ভাষ্যকারের ষাঁড়দের অন্যতম’ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তারপরও আমি আমার নিজেকে কোনভাবেই বোঝাতে পারি না যে আমাদের আইরিশ ইতিহাসের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী যেকোন নিপীড়ন ও বর্বরতাকে খ্রিষ্ট-সভ্যতার প্রারম্ভিক অমায়িকতার সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে কেন স্বাভাবিক করা হয়েছে। সাহিত্য নোবেল ঘোষণার আগের দিন সকালবেলায় এই পুরো প্রত্যয় আমার চোখে অন্য একটি বর্বর ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছিল, যা আমি কয়েক সপ্তাহ আগে র্স্পাটার জাদুঘরে দেখেছিলাম। এই শিল্প একটা ধর্মবিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে যা সেন্ট কেভিনের সমর্থিত বিশ্বাস থেকে একেবারে ভিন্ন। কেভিনের শিল্পে যদিও একটা পরিশ্রান্ত পাখি, একটা মোহাবিষ্ট পশু আর আত্ম-আহ্লাদিত মানুষের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু র্স্পাটা শিল্পে ছিল অরফিউস এবং পরমানন্দের ভাবাবেশ। কোন পূজা প্রার্থনার বদলে সঙ্গীত থেকে উৎসারিত হয়েছিল। শিল্পকর্মটি ছিল একটি খোদিত প্রতিমা। আমি তৎক্ষণাৎ এর একটি রেখাচিত্র একেঁ ফেলেছিলাম। এমনকি প্রদর্শনীর নিচে কার্ডে এই শিল্প সম্পর্কে লিখিত সব বিবরণ পর্যন্ত আমার নোটবুকে টুকে ফেলেছিলাম। এই চিত্রটির প্রাচীনতা ও টেকসইতা আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে ঠিক তেমনি কার্ডে বর্ণিত বিবরণও আমাকে সমানভাবে মোহিত করেছে। কারণ বিবরণে এমন একটা নাম ও প্রত্যয় ছিল যাকে নিয়ে আমি বিগত তিন দশক ধরে ভেবে আসছিলাম। পরিচিতি কার্ডে ‘ব্রত সভাসদ’ নামের বিবরণে লেখা ছিল, ‘সম্ভবত আঞ্চলিক কবি ওরফেউস দ্বারা স্থাপিত। হেলেনিস্টিক যুগের স্থানীয় শিল্পকর্ম।’
*
আমি আরো একবার বলতে চাই শিল্পের স্থানিকতা নিয়ে আমি ততটা ভাবপ্রবণ হচ্ছি না কিংবা একে অতিভক্তির স্তরে নামিয়ে নিচ্ছি না। আমি বরং যে ছবি ও গল্পের কথা এখানে আহ্বান করছি তা শিল্পের মূল্যমানের বাহক হিসেবে কাজ করে। এই শতাব্দীর মানবসম্প্রদায় অস্ত্রশক্তির জোরে নাৎসিবাদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এই সব গল্প ও ছবির বেষ্টনে ও আরোপিত আদর্শিক সামঞ্জস্যতার অধীনে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধের অনড় অবস্থানের ফলে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ও প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকি আমরা যদি কোন জাতির সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও অখণ্ডতাকে আদর্শিক মানদণ্ড ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় উন্নীত করতে ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। এমনকি আমাদের কাছে যদি এই ভয়ানক প্রমাণও থাকে যেখানে জাতিতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় অহংবোধ খুব অল্প সময়ে ফ্যাসিবাদের কাতারে নেমে আসতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের সর্তক অবস্থান সহজাত আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য যে আস্থা ও মমতা তাকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে। বিপরীত দিকে বিদ্যমান ক্ষমতা ও কল্যাণকামিতা স্থানিক পরিভ্রমণ আমাদের এমন এক বিশ্বের সম্ভাব্যতাকে কৃতিত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করে যেখানে সকল ঐতিহ্যের অস্তিত্বকে সম্মান জানাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যেখানে রাজনৈতিক পরিসরে এক স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় থাকে। গণহত্যা, গুপ্তহত্যা ও গণ উচ্ছেদের বিধ্বংসী ঘটনা এবং পৌনঃপুনিকতা প্যালেস্টাইন ও ইসরাইল, আফ্রিকা ও আফ্রিকানার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন মোড় ও ভিত্তি প্রদান করেছে। যেভাবে ইউরোপের সীমানা প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়েছে আর লোহার পর্দা টেনে দিয়েছে। এই সব কিছু আয়ারল্যান্ডের জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের বিচার ব্যবস্থা চলমান বিভক্তিই মূলত এই জটিলতার মূল কারণ। ব্রিটিশ ও আইরিশদের ঐতিহ্য, সমানভাবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রতি অনুরাগ এই সীমাহীন বিভাজনের কান্ডারী। কিন্তু এই দেশের অধিবাসীরা এই আশা করতে পারে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সরকার দল জড়িত তারা দেশভাগকে এমনভাবে সম্পাদন করতে পারে যেটা অনেকটা টেনিস কোর্টের জালের মতো। সীমান্তরেখা দিয়ে সহজে প্রবেশ-প্রস্থান করতে পারে, বিরোধ ও প্রতিরোধ করতে পারে, একটা আশাব্যঞ্জক আগামীর পূর্বানুমান করতে পারে। ‘শত্রুতা’ ও ‘মিত্রতা’ শব্দের বেষ্টনী থেকে যে প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয়েছে তা আরও কম দ্বৈত অর্থে প্রকাশিত হবে, আরো কম সংযুক্ত থাকবে।
*
ডব্লিউ. বি. ইয়েটস আজ থেকে সত্তর বছর আগে যখন এই নোবেল মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ড তখন গৃহযুদ্ধের তীব্র বেদনার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, যা আয়ারল্যান্ডকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতার পদমূলে এসে দাঁড় করিয়েছিল। সংগ্রামটা খুব ক্ষণকালের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। ১৯২৩ সালের মে মাস জুড়ে। তার ঠিক সাত মাস আগে ইয়েটস স্টকহোমের পথে যাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধটা ছোট কিন্তু এটি ছিল চরমভাবে রক্তাক্ত, হিংস্র ও প্রগাঢ়। পরবর্তী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আয়ারল্যান্ড ২৬টি কাউন্টির রাজনৈতিক পরিভাষা প্রকৃতি ঠিক করে দিয়েছিল। এই দ্বীপে প্রথম যে অংশটা আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয় তা পরবর্তীকালে আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র রূপান্তরিত হয়।
ইয়েটস তার নোবেল বক্তৃতাতে আয়ারল্যান্ড এই গৃহযুদ্ধ বা এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গে কোন কথা উচ্চারণ করেননি। আয়ারল্যান্ড রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিকতার ভাঙা ও গড়ার এই নিবিড় সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক জীবনের নির্মাণ ও নির্মাতাদের বিষয়ে ইয়েটস ছাড়া নোবেলের ওইদিনের মঞ্চে আর কেউ ভালো বুঝতে পারতো না। কিন্তু উনি এই সব জরুরী বিষয় রেখে আইরিশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের সৃজনশীল উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প করেছেন। তার প্রতিভার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তার বন্ধু জন মিলিংটন সিঞ্জ ও লেডি অগাস্তা গেগ্রি প্রতিভার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি সুইডেনে এসে এই কথাটাই বলে গেছেন যে তার দেশ ও কালের গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরে আইরিশ কবি ও নাট্যকারদের শিল্প ও সাহিত্য কর্ম গেরিলা-যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার মতোই সমান মূল্য বহন করে। তার দাম্ভিকতা পূর্ণ নোবেল বক্তৃতার উৎকৃষ্ট গদ্য কয়েক দশক পরে তার রচিত ‘পৌর চিত্রশালার পুনঃপরিদর্শন’ পদ্যে আবশ্যিক ভাবে একই বোধের প্রকাশ করে। কবিতাটিতে তিনি সেই ঐতিহাসিক সময়ের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের প্রতিকৃতি ও বীরোচিত কাহিনী চিত্রের মাঝে নিজেকে উপস্থাপন করেন এবং আকস্মিকভাবে বুঝতে পারেন যে যুগান্তকারী কিছু একটা ঘটে গেছে। ‘এটা আমি বলতে রাজি নই,/ আমার ছেলেবেলার মৃত আয়ারল্যান্ড, কিন্তু এমন এক আয়ারল্যান্ড/ কবি তার কবিতায় রচেছে, বীভৎস ও প্রফুল্ল,’ তারপর তিনি তার সাহিত্য সমগ্রের সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা দুটি পদ্যচরণ দিয়ে শেষ করেন।
ভেবে দেখো জীবনের মহিমা কোথায় শুরু কোথায় শেষ।
আর বলো আমার গৌরব আমার এমন কিছু বন্ধু ছিল।
এই কবিতা চরণ দুটি যতোটা ব্যাপক আর রোমাঞ্চকর ততটাই কাব্য আঙ্গিকের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ: এমন কবিতাই শুদ্ধ কবিতা যে নিজেকে জাহির করার চেয়ে আপন আলোয় বিকশিত হয়। তারা কবির বিশ্বজয়ের রাজপথ হয়ে উঠে। আজকে আমি যে বিজয় লাভ করেছি সেই সম্মানের মুকুট আমার কবিতার জন্য, আমার জন্য নয়। সত্যি বলতে আজকে আমি আমার হয়ে আমার সম্মানে আমার কবিতা থেকে আরো কিছু চরণ উদ্ধৃত করতে চাই। ‘তোমরা যারা আজ আমাকে বিচার করবে, নেড়ো না বিচারের কাঠি শুধু/ এই গ্রন্থ থেকে ওই গ্রন্থে।’ আমিও তোমাদের সেই একই কাজ করতে বলবো। যে কাজ ইয়েটস তার শ্রোতাদের করতে বলেছিলেন। আইরিশ কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের বিগত চল্লিশ বছরের অবদানকে স্মরণ করতে বলবো যাদের মধ্যে আমি ও গর্ব করে কিছু বন্ধুকে স্মরণ করতে চাই। এজরা পাউন্ড যেমন বলেছিলেন, ‘এমন কারো মতামত গ্রহণ করো না যারা উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেনি।’ এই উপদেশ বার্তাটি আমি অনুসরণ করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। ত্রিশ বছরের বেশি হবে আমি যখন বেলফাস্টে আমার লেখালেখি শুরু করেছি। তখন শুধুমাত্র আমার নিজের দেশের প্রসিদ্ধ লেখকদের বাইরেও বিদেশি লেখকদের মতও আমার সাহিত্যিক অভিযানে প্রেরণা দিয়েছে। আমি আজকে যে আয়ারল্যান্ডে বাস করছি এখানকার সমকালীন লেখকদের লেখাও আমার কল্পনাকে বিস্তৃত করেছে। যাই হোক এটা কোনভাবেই বলা যাবে না ইয়েটস সবদিক থেকে বিকাশিত হতে পেরেছেন। আমার শতাব্দীর কবিতাকে যদি কৃতিত্ব দিতে হয় তাহলে অবশ্যই তার বিখ্যাত দুটি ধারাবাহিক কবিতাকে গণনায় আনতে হবে। একটি হলো ‘উনিশ শত উনিশ’ আরেকটি হলো ‘গৃহযুদ্ধ কালের ধ্যান মগ্নতা’। দ্বিতীয় কবিতার তার সেই বিখ্যাত গীতিকাব্য যেখানে তার ঘরের জানালার দেয়ালের ফাটলে একটা পাখি ঘর বেধেঁছিল। সেই পুরনো দেয়ালের ফোকরে একটা কাঠ শালিক বেড়ে উঠেছে। কবি তখন একটা নরম্যান টাওয়ারে বসবাস করছেন। এই টাওয়ারটি যেমন দেশের সামরিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, তেমনি সেই বিক্ষুব্ধ সময়েরও অংশও ছিল। ইয়েটসের চিন্তাগুলো সভ্যতার প্রতি বিদ্রুপ হিসাবে চলতে থাকলো। ওইসব নৃশংস ও ক্ষমতাশালী দিগ্বিজয়ীদের গাঁথা যারা শেষ জীবনে শিল্পী ও স্থপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলো। একটা মা পাখি তার ছানাকে খাবার খাওয়াচ্ছে এই চিত্রটাকে মধুমক্ষীর সাথে যুক্ত করে দিলেন। কাব্যের ধারায় এই রকম চিত্ররূপ গভীরভাবে বিভূষিত। সবসময় একটা কর্মঠ, সুরেলা ও প্রতিপালক তুল্য জনরাষ্ট্রের দিকে ইশারা করে।
মৌমাছিরা গড়েছে ঘর নড়বড়ে
দেয়ালের এক ফোকরে, আর তারপর
মা পাখিটা এলো পতঙ্গ আর ফড়িং ধরে।
আমার দেয়াল খসে পড়চ্ছে; মধুমক্ষীর দলে,
এসো, কাঠ শালিকের শূন্য ঘরে এসো।
আমরা আছি ঘরবন্দি, চাবিটা ঘুরে চলছে
আমাদের অজানা পথে, কোথাও
একজন হয়েছে নিহত, বা একটা ঘর পুড়েছে।
কিছুই যাচ্ছে না জানা, কোথায় কেন কি হচ্ছে:
এসো, কাঠ শালিকের শূন্য ঘরে এসো।
কাঠ ও পাথরে রুদ্ধ পথ;
ঘরে ঘরে বিগ্রহ এক পক্ষ কাল;
গত রাতে তারা গড়াতে গড়াতে পার হলো পথ।
সেই মৃত তরুণ সেনার বুকে লেখা রক্তের শপথ
এসো, কাঠ শালিকের শূন্য ঘরে এসো।
আমাদের হৃদয় ভরে আছে অলীক সুখে,
মেনে নিতে নিতে আমাদের আত্মা নিষ্করুণ;
আমরা পূর্ণ বিরাগ রসে।
আমাদের প্রেম শূন্যতলে। ও মৌমাছি দলে,
এসো, কাঠ শালিকের শূন্য ঘরে এসো।
আমি গত পঁচিশ বছর যাবত আইরিশদের মুখে মুখে এই কবিতাটা বারবার শুনেছি। কখনো আংশিক কখনো পুরোটা। জেনে অবাক হবেন না, জীবনের প্রতি দরদ ভরা এই কবিতাটা সেন্ট কেভিনের জীবনের মতো নিবেদিত। হোমারের কবিতায় জীবনে ঘটে যাওয়া চালচিত্রের প্রতি ইস্পাত কঠিন যেমন। এটা সবার জানা ছিল রাস্তায় আবারও গণহত্যার ঘটনা ঘটবে। মিনিবাসগুলো রাস্তায় সারিবদ্ধ করে রাখা হবে আর চলে যাবার সময় ঠিক ঠিক সবাইকে গুলি করে মারা হবে। এই নির্মমতা নিয়ে যেমন বাঁচতে হয় তেমনি ওই যে ক্যাথলিক ভাইটা যে প্রটেস্টান্ট ভাইকে বাঁচাতে তার হাতটা চেপে ধরেছিল আমাদের ওই সহানুভূতিপ্রবণ বাস্তবতাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। মানুষ মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে এই দিকটাকেও সম্মান জানাতে হবে। চরম সংকটকালে আমাদের চেতনা যে পরস্পরবিরোধী অনুভূতির মধ্য দিয়ে যায় তাকে মানুষের এই দরদ ভরা সহানুভূতিই রক্ষা করে। একদিকে সত্য বলার আকাঙ্ক্ষা যা খুবই কঠিন ও প্রতিশোধ পরায়ন, অন্যদিকে যা কিছু মধুর, যা কিছু শুভ তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা না করার প্রবল তাগিদ থাকবেই। এটা প্রমাণিত যে কবিতা একই সাথে সমমাত্রিক ও সত্য হতে পারে। এমন সম্পূর্ণ সঠিক কবিতা আনা আখমাতোভার লেখায় পাওয়া যাবে। প্রায় দুইশত বছর আগে যে ঐতিহাসিক সংকট মুহূর্তে ও ব্যক্তিগত হতাশা থেকে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ তার কবিতা লিখে গেছেন তাতে পাওয়া যাবে এমন শুদ্ধ কবিতার দীপ্তি।
*
যখন গ্রিক চারণকবি ডেমোডকাস ট্রয় নগরীর পতন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে গান গাইছিলেন, ওডিসিয়াস কাঁদছিল ও হোমার বলেছিল এই কান্না হলো স্বামীর মৃত্যু শোকে রণক্ষেত্রে বুক ভেঙ্গে অঝোরে কাঁদতে থাকা নারীর চোখের জলের মতো। তার মহাকাব্যের উপমাগুলো ঠিক এমনই:
যখন রণাঙ্গনে যোদ্ধার শ্বাস শেষ হয় আসচ্ছে, মরে যাচ্ছে,
নারীটি তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়ে, আর্তনাদ করে উঠলো;
বর্শার তীক্ষ্ণ দাঁত তার কাঁধে ও পিঠে এফোড়-ওফোড় করে দিলো,
দাসত্বে আর বিষাদের স্রোতে ভেসে গেলো।
গাল গড়িয়ে পড়ল সকাতর অশ্রুজল:
ওডিসিয়াসের কান্নার চেয়ে করুণ কিছু নাই,
আভরণে ঢাকা ছিল যা আজ তা সেনাদলে ঘেরা।
এমনকি আজ এই বেলায়, তিন হাজার বছর পরে যখন টেলিভিশন পর্দায় এই সময়ের নানা ধরনের বর্বরতা চোখের সামনে সরাসরি সম্প্রচার হতে দেখি। আমরা সবকিছু সম্পর্কে খুব ভালো করে অবগত কিন্তু এসব বর্বরতার ক্রমবর্ধমান দায়মুক্তি ও গোচর হচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিশিবির ও গুলাগের চেনা ছবিগুলো অতি সাধারণ হয়ে যাচ্ছে। হোমারের চিত্ররূপগুলো এখনও আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়। নারীটির পিঠে ও ঘাড়ে বর্শার ধারালো ও নির্মম ক্ষত কাল ও ভাষাকে অতিক্রম করে আজও সতেজ আছে। এই চিত্ররূপ এতোটাই স্বচ্ছ যে মানব ইতিহাসের সকল অসহিষ্ণুতার সকল প্রশ্নের সকল উত্তর ঠিকঠাক পাওয়া যায়।
আরেক রকম উপমা ও দেখতে পাওয়া যায়, যা শুধু গীতিকাব্যের সাথে মানানসই। এটা আমাদের ‘কানের পর্দার’ উপর প্রযোজ্য মানে আমাদের শ্রবণেন্দ্রীয় কবিতার উদ্ধৃতাংশকে মূর্তমান করে তোলে। এটা এমন এক উপমা যাকে ম্যান্ডেলস্টাম ‘স্পষ্ট বচনের দৃঢ়তা’ বলেছেন। এই স্পষ্ট কথার দৃঢ় সংকল্প ও স্বতন্ত্রতা একটা কবিতাকে পুরোপুরি হৃদয়াঙ্গম করার জামিনদার। ভাষার এই বিভাজন ও সংমিশ্রণ থেকে যে সংবেদী শক্তি নিঃসৃত হয় তাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায়। কবিতার ছন্দময়তা, স্বরভঙ্গি, মিত্রাক্ষর ও স্তবক থেকে যে উচ্ছ্বাস তৈরি হয় তা থেকে কবিতার উদ্বেগ আর কবির সত্যের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে আঁচ করা যায়।
সত্যি বলতে গীতি কবিতায় সত্যবচন খুব স্পষ্ট করে চেনা যায়। এই কবিতার মাধ্যমে সত্য নিজেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এটা সঙ্গীতের তানের অশান্ত সাধনার মতো। যে তান এমিলি ডিকিনন্সন ও পল সেলানের কবিতায় পাওয়া যায়। জন কিটসের কবিতার সুরের ঐকতান সুললিত হয়ে কানে বাজে। এটা এমন কাব্য আঙ্গিক যা দিয়ে সকল জ্ঞাত স্বরের অগোচরে সম্পূর্ণ প্ররোচিত স্বর শোনার জন্য কবির কানকে অনবরত জোর জবরদস্তি করতে থাকে।
অন্যভাবে বললে বলবো আমি তো এখনো পর্যন্ত সোফার নরম হাতল থেকে মেঝেতই নেমে আসিনি। আমি আগের চেয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে খবর শুনি। বিশ্বের ইতিহাস আর তার পিছনে জগতের দুর্দশার কথা জানতে আরো বেশি উদ্গ্রীব থাকি। কিন্তু যে বক্তার কথা শোনার জন্য আমি উদ্গ্রীব হই তা ঠিক চলমান ঘটনার গল্প নয়। এটা আরো আত্মবাচক। কারণ একজন কবি হিসেবে আমি যেন এক গতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমি সংগীতের তালে তালে বাজতে থাকা ধ্বনির শৃংখলার স্থিতি অবস্থায় এক টুকু বিশ্রাম নিতে উন্মুখ হয়ে আছি। যেন কবিতার মৃদু তরঙ্গ নিজেকে সংশোধন করে এর অপরিমেয় কামনাকে যাচাই করে দেখতে চায়। কবিতার সূচনা বিন্দু থেকে একবার সন্নিবেশিত হয় তো আরেক বার নিষ্কোষিত হয়।
আমি কবিতার এই গীতিময়তার দিকে প্রবলভাবে ধাবিত হই। ‘কাঠ শালিকের শূন্য ঘরে এসো’, ইয়েটসের গীত-ধ্রুবকের পৌনঃপুনিকতায় একটা বিনয়ের সুর শুনতে পাই। ‘ঘর’ ও ‘নির্মাণ’-এর মতো শব্দগুলো কবিতার আবর্তন কেন্দ্রবিন্দু। ‘শূন্য’ শব্দ দিয়ে বিভাজনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়।
‘অলীক সুখে’ ‘বিরাগ রসে’ ও ‘মৌমাছি দলে’ এই ত্রিমাত্রার অন্তমিলের সমাবস্থাতে আমি ত্রিধারা শক্তিকে ধরতে পারি। পুরো কবিতার পুরোদস্তুর আঁটসাঁট শৃঙ্খলা ভাষাকে ভিন্ন মাত্রার আকৃতি দিয়েছে। কাব্যের আঙ্গিক একই সাথে জাহাজ ও নোঙ্গরের মতো। এটা একই সাথে গতিময় ও স্থিতিশীল। আমাদের শরীর ও মনের যা কিছু অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক তার সবকিছুকে যুগপৎ ও সমলয়ে পরিতৃপ্ত করতে পারে। একটি বিশুদ্ধ কবিতার জীবন ও জগতের উপর সব সময় কোন না কোন ব্যঞ্জনা ও উপযোগ আছে ইয়েটসের কবিতায় তার সবই সমভাবে উপস্থিত। তার মানে জগতের নির্মম ও অসংবেদী প্রকৃতির প্রস্তরখন্ডে কবিতা মানুষের সংবেদনশীল প্রকৃতির কোমল স্পর্শ বুলিয়ে যায়। অন্য কথায় কবিতার কাঠামো স্বয়ং কবিতার শক্তি প্রকাশের জন্য যথেষ্ট। আমাদের চেতনার অসীমতায় যে ভ্রান্তি ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে তার মাঝেই আমাদের ক্ষীণ শুভবোধের স্ফুলিঙ্গকে জ্বালিয়ে রাখতে কবিতাকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। কবিতার শক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরাই আমাদের মূল্যবোধের শিকারী ও সংগ্রহকারী। কবিতার ঐশ্বর্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের নিঃসঙ্গতা আর জীবন যন্ত্রণা কতটা বাস্তব; আমাদের খাঁটি মানব জীবনে কতটা ঐকান্তিক।
উৎস লিংক: Seamus Heaney–Nobel Lecture–NobelPrize.org
Copyright © The Nobel Foundation 1995
Bengali Copyriht © pratidhwanibd.com








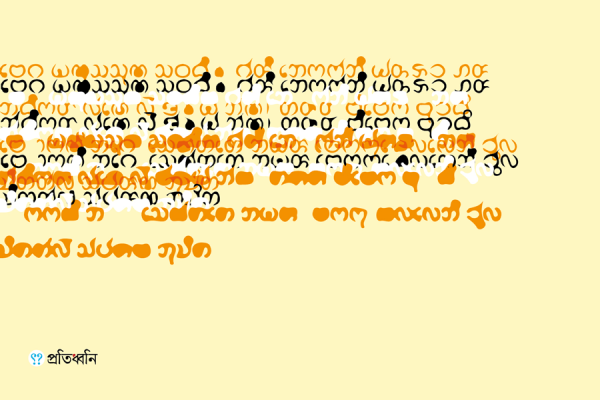


আপনার মন্তব্য প্রদান করুন